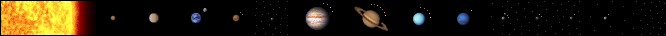এরিস
 এরিস (মাঝে) এবং ডিসনোমিয়া (বামে); ছবিটি হাবল স্পেস টেলিস্কোপ দ্বারা তোলা হয়েছে | |||||||||
| আবিষ্কার | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| আবিষ্কারক | |||||||||
| আবিষ্কারের তারিখ | ৫ই জানুয়ারি, ২০০৫[২] | ||||||||
| বিবরণ | |||||||||
| উচ্চারণ | /ˈɪərɪs/,[৩][৪] /ˈɛrɪs/[৫][৪] | ||||||||
| নামকরণের উৎস | Ἔρις Eris | ||||||||
| বিকল্প নামসমূহ | 2003 UB313[৬] Xena (nickname) | ||||||||
| ক্ষুদ্র গ্রহসমূহের শ্রেণী | |||||||||
| বিশেষণ | Eridian /ɛˈrɪdiən/[৯][১০] | ||||||||
| কক্ষপথের বৈশিষ্ট্য[৬] | |||||||||
| যুগ ৩১শে মে, ২০২০ (JD 2459000.5) | |||||||||
| অপসূর | ৯৭.৪৫৭ AU (১৪.৫৭৯ টেমি) | ||||||||
| অনুসূর | ৩৮.২৭১ AU (৫.৭২৫ টেমি) | ||||||||
| অর্ধ-মুখ্য অক্ষ | ৬৭.৮৬৪ AU (১০.১৫২ টেমি) | ||||||||
| উৎকেন্দ্রিকতা | ০.৪৩৬০৭ | ||||||||
| কক্ষীয় পর্যায়কাল | ৫৫৯.০৭ ্বছর (২০৪,১৯৯ d) | ||||||||
| গড় কক্ষীয় দ্রুতি | ৩.৪৩৪ কিমি/সেকেন্ড | ||||||||
| গড় ব্যত্যয় | ২০৫.৯৮৯° | ||||||||
| নতি | ৪৪.০৪০° | ||||||||
| উদ্বিন্দুর দ্রাঘিমা | ৩৫.৯৫১° | ||||||||
| নিকটবিন্দুর সময় | ≈ ৭ই ডিসেম্বর, ২২৫৭[১১] ±২ সপ্তাহ | ||||||||
| অনুসূরের উপপত্তি | ১৫১.৬৩৯° | ||||||||
| উপগ্রহসমূহ | Dysnomia | ||||||||
| ভৌত বৈশিষ্ট্যসমূহ | |||||||||
| গড় ব্যাসার্ধ | ১১৬৩±৬ কিমি[১২][১৩] | ||||||||
| পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল | (১.৭০±০.০২)×১০৭ km2[ক] | ||||||||
| আয়তন | (৬.৫৯±০.১০)×১০৯ km3[ক] | ||||||||
| ভর | |||||||||
| গড় ঘনত্ব | ২.৪৩±০.০৫ গ্রাম/সেমি3[১৪] | ||||||||
| বিষুবীয় পৃষ্ঠের অভিকর্ষ | ০.৮২±০.০২ মি/সে2 ০.০৮৪±০.০০২ গ্রাম[গ] | ||||||||
| বিষুবীয় মুক্তি বেগ | টেমপ্লেট:V2 ± ০.০১ কিমি/সে[গ] | ||||||||
| নাক্ষত্রিক ঘূর্ণনকাল | ১৫.৭৮৬ d (synchronous)[১৫] | ||||||||
| অক্ষীয় ঢাল | ≈ ৭৮.৩° কক্ষপথের দিকে (অনুমান)[ঘ][১৬] ≈ ৬১.৬° to ecliptic (অনুমান)[ঘ][ঙ] | ||||||||
| জ্যামিতিক অ্যালবেডো | ০.৯৬+০.০৯ −০.০৪ [সিক] geometric[১২] ০.৯৯+০.০১ −০.০৯ Bond[১৭] | ||||||||
| |||||||||
| বর্ণালীর ধরন | বি−ভি=০.৭৮, ভি−আর=০.৪৫[১৮] | ||||||||
| আপাত মান | ১৮.৭[১৯] | ||||||||
| পরম মান (H) | –১.২১[৬] | ||||||||
| কৌণিক ব্যাস | ৩৪.৪±১.৪ মিলি-আর্কসেকেন্ড[২০] | ||||||||
এরিস (অপ্রধান গ্রহ উপাধি ১৩৬১৯৯ এরিস) হল সৌরজগত-এর সবচেয়ে বিশাল এবং পরিচিত দ্বিতীয় বৃহত্তম বামন গ্রহ।[২২] এটি বিক্ষিপ্ত ডিস্ক-এ একটি ট্রান্স-নেপচুনিয়ান অবজেক্ট (টি এন ও) এবং এটির উচ্চ-অকেন্দ্রিক কক্ষপথ রয়েছে। ২০০৫ সালের জানুয়ারী মাসে মাইক ব্রাউন-এর নেতৃত্বে একটি পালোমার অবজারভেটরি-ভিত্তিক দল দ্বারা এরিস আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং পরের বছরে যাচাই করা হয়েছিল। ২০০৬ সালের সেপ্টেম্বরে, গ্রেকো-রোমান বিবাদ ও বিবাদের দেবী-র নামে এটির নামকরণ করা হয়েছিল। এরিস হল নবম-সর্বোচ্চ বৃহদায়তন পরিচিত বস্তু যা সূর্য-কে প্রদক্ষিণ করছে এবং সৌরজগতের (উপগ্রহদের নিয়ে) সামগ্রিকভাবে ষোড়শ-সর্বোচ্চ বিশাল। এটি সবচেয়ে বড় বস্তু যা একটি মহাকাশযান দ্বারা পরিদর্শন করা হয়নি। এরিসের ব্যাস ২,৩২৬ ± ১২ কিলোমিটার ২,৩২৬ ± ১২ কিলোমিটার (১,৪৪৫ ± ৭ মা)[১২] ; এর ভর পৃথিবীর ০.২৮% এবং প্লুটোর তুলনায় ২৭% বেশি,[২৩][২৪] [২৫] যদিও প্লুটো আয়তনে কিছুটা বড়,উভয়েরই ভূপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল রাশিয়া বা অ্যান্টার্কটিকার ক্ষেত্রফলের সাথে তুলনীয়।
এরিসের পরিচিত একটি বড় উপগ্রহ আছে, ডিসনোমিয়া। ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে, সূর্য থেকে এরিসের দূরত্ব ছিল ৯৬.৩ এ ইউ (১৪.৪১ বিলিয়ন কিমি; ৮.৯৫ বিলিয়ন মাইল),[১৯] নেপচুন বা প্লুটোর থেকে তিনগুণ বেশি। দীর্ঘ-কালের ধূমকেতু বাদে, ২০১৮ সালে ২০১৮ ভিজি১৮ আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত এরিস এবং ডিসনোমিয়া সৌরজগতের সবচেয়ে দূরবর্তী পরিচিত প্রাকৃতিক বস্তু ছিল।[১৯]
যেহেতু এরিস প্লুটোর চেয়ে বড় বলে মনে হয়েছিল, নাসা প্রাথমিকভাবে এটিকে সৌরজগতের দশম গ্রহ হিসাবে বর্ণনা করেছিল। এটি, ভবিষ্যতে একই আকারের অন্যান্য বস্তুর আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনার সাথে, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়ন (আই এ ইউ) কে প্রথমবারের মতো গ্রহ শব্দটি সংজ্ঞায়িত করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। ২৪শে আগস্ট, ২০০৬-এ আই এ ইউ অনুমোদিত সংজ্ঞা অনুসারে, এরিস, প্লুটো এবং সেরেস হল "বামন গ্রহ",[২৬] সৌরজগতের পরিচিত গ্রহের সংখ্যা কমিয়ে আট করা হয়েছে, যা ১৯৩০ সালে প্লুটোর আবিষ্কারের আগে ছিল। ২০১০ সালে এরিসের দ্বারা নাক্ষত্রিক জাদুবিদ্যা দেখায় যে এটি প্লুটোর থেকে খুব সামান্য ছোট,[২৭][২৮] যা জুলাই ২০১৫ সালে ২,৩৭৭ ± ৪ কিলোমিটার (১,৪৭৭ ± ২ মা) গড় ব্যাস হিসাবে নিউ হরাইজনস দ্বারা পরিমাপ করা হয়েছিল।[২৯][৩০]
আবিষ্কার[সম্পাদনা]
২১শে অক্টোবর ২০০৩-এ তোলা ছবি থেকে[৩১] ৫ই জানুয়ারী,২০০৫-এ মাইক ব্রাউন, চ্যাড ট্রুজিলো এবং ডেভিড রাবিনোভিটজ-এর দল[২] এরিসকে আবিষ্কার করেন। আবিষ্কারটি ২৯শে জুলাই, ২০০৫-এ ঘোষণা করা হয়েছিল, মেকমেকের একই দিনে এবং হাউমিয়ার[৩২] দু'দিন পরে,ঘটনাগুলির কারণে যা পরবর্তীতে হাউমিয়া সম্পর্কে বিতর্কের দিকে নিয়ে যায়। অনুসন্ধান দলটি বেশ কয়েক বছর ধরে বৃহৎ বাইরের সৌরজগতের জন্য পদ্ধতিগতভাবে স্ক্যান করছিল এবং ৫০০০০ কোয়াওর, ৯০৪৮২ অর্কাস, এবং ৯০৩৭৭ সেডনা সহ আরও কয়েকটি বড় টিএনও আবিষ্কারের সাথে জড়িত ছিল।[৩৩]
ক্যালিফোর্নিয়ার পালোমার অবজারভেটরিতে ১.২ মিটার স্যামুয়েল ওসচিন শ্মিট টেলিস্কোপ ব্যবহার করে ২১শে অক্টোবর, ২০০৩-এ রুটিন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল, কিন্তু খুব ধীর গতির কারণে এরিসের চিত্রটি সেই সময়ে আবিষ্কৃত হয়নি: দলের স্বয়ংক্রিয় ইমেজ-অনুসন্ধান সফ্টওয়্যার ফিরে আসা ফলস পজিটিভ সংখ্যা কমাতে প্রতি ঘন্টায় ১.৫ আর্কসেকেন্ডের কম গতিতে চলমান সমস্ত বস্তুকে বাদ দেয়।[৩১] ২০০৩ সালে যখন সেডনা আবিষ্কৃত হয়েছিল, তখন এটি ১.৭৫ আর্কসেক/ঘণ্টা গতিতে চলছিল, এবং সেই আলোকে দলটি তাদের পুরানো ডেটাকে কৌণিক গতির একটি নিম্ন সীমা দিয়ে পুনঃবিশ্লেষণ করেছিল, চোখের দ্বারা পূর্বে বাদ দেওয়া চিত্রগুলির মাধ্যমে সাজিয়ে৷ ২০০৫ সালের জানুয়ারিতে, পুনঃ-বিশ্লেষণে পটভূমির তারার তুলনায় এরিসের ধীর গতির প্রকাশ ঘটে।[৩১]
এরিসের কক্ষপথের প্রাথমিক নির্ণয় করার জন্য বারংবার পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল, যার ফলে বস্তুর দূরত্ব অনুমান করা যায়।[৩১] দলটি পরবর্তী পর্যবেক্ষণ এবং গণনা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত উজ্জ্বল বস্তু এরিস এবং মেকমেক- এর আবিষ্কারের ঘোষণা বিলম্বিত করার পরিকল্পনা করেছিল, কিন্তু তারা ২৯শে জুলাই উভয়েরই ঘোষণা করেছিল যখন ২৭শে জুলাই স্পেনের একটি ভিন্ন দল তাদের ট্র্যাকিং করা আরেকটি বড় টি এন ও-হাউমেয়া-এর আবিষ্কারটি বিতর্কিতভাবে ঘোষণা করে।[২]
এরিসের পুনরুদ্ধারের চিত্রগুলি ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪ থেকে চিহ্নিত করা হয়েছে।[৬]
২০০৫ সালের অক্টোবরে প্রকাশিত আরও পর্যবেক্ষণ থেকে জানা যায় যে এরিসের একটি উপগ্রহ রয়েছে, পরে তার নাম দেওয়া হয় ডিসনোমিয়া। ডিসনোমিয়ার কক্ষপথের উপর পর্যবেক্ষণ বিজ্ঞানীদের এরিসের ভর নির্ধারণ করতে সাহায্য করে, যা ২০০৭ সালের জুনে গণনা করা হয়েছিল (১.৬৬±০.০২)×১০২২ কেজি,[২৩] প্লুটোর থেকে ২৭%±২% বেশি।
নাম[সম্পাদনা]
এরিসের নামকরণ করা হয়েছে গ্রিক দেবী এরিসের (গ্রীক Ἔρις) নামানুসারে, যা বিবাদ ও মতবিরোধের রূপকার।[৩৪] নামটি ক্যালটেক টিম দ্বারা ৬ই সেপ্টেম্বর, ২০০৬-এ প্রস্তাব করা হয়েছিল, এবং এটি ১৩ই সেপ্টেম্বর, ২০০৬-এ নামকরণ করা হয়েছিল,[৩৫] একটি অস্বাভাবিক দীর্ঘ সময়ের পরে যেখানে বস্তুটি অস্থায়ী নাম ২০০৩ ইউ বি৩১৩ দ্বারা পরিচিত ছিল, যা আই এ ইউ দ্বারা ছোট গ্রহের জন্য তাদের নামকরণ প্রোটোকলের অধীনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুমোদিত হয়েছিল ।
এরিস নামের দুটি উচ্চারণ রয়েছে, একটি "দীর্ঘ" বা একটি "ছোট" ই সহ,[৩] যুগ বা era শব্দের দুটি উচ্চারণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।[৪] গ্রিক দেবীর ধ্রুপদী ইংরেজি উচ্চারণ হল ˈɪərɪs/, একটি দীর্ঘ ই। যাইহোক, ব্রাউন এবং তার শিক্ষার্থীরা[৩৬] /ˈɛrɪs/ সহ ডিসিলেবিক ল্যাক্সিং এবং একটি ছোট ই সহ /ˈɛrɪs/ ব্যবহার করেন।[৫]
নামটির গ্রীক এবং ল্যাটিন তির্যক কান্ড হল এরিড-,[৩৭] যেমনটি ইতালীয় এরিড এবং রাশিয়ান Эрида ইরিডা-তে দেখা যায়, তাই ইংরেজিতে বিশেষণটি হল এরিডিয়ান /ɛˈrɪdiən/.[৯][১০]
জেনা[সম্পাদনা]
আই এ ইউ-র নিয়মানুসারে, বস্তুটিকে গ্রহ বা ছোট গ্রহ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হবে কিনা তা নিয়ে অনিশ্চয়তার কারণে, (কারণ বিভিন্ন নামকরণ পদ্ধতি এই শ্রেণীর বস্তুর জন্য প্রযোজ্য),[৩৮] ২৪শে আগস্ট, ২০০৬-এর আগে পর্যন্ত এর নামকরণ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়নি।[৩৯] কিছু সময়ের জন্য বস্তুটি জনসাধারণের কাছে জেনা নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। "জেনা" ছিল একটি অনানুষ্ঠানিক নাম যা আবিষ্কারকারী দল অভ্যন্তরীণভাবে ব্যবহার করেছিল, যা টেলিভিশন সিরিজ জেনা:ওয়ারিয়র প্রিন্সেসের শিরোনাম চরিত্র দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। আবিষ্কার দলটি প্লুটোর চেয়ে বড় যে প্রথম বস্তু আবিষ্কার হবে তার জন্য ডাকনাম "জেনা" সংরক্ষণ করেছিল বলে জানা গেছে। ব্রাউনের মতে,
আমরা এটি বেছে নিয়েছি যেহেতু এটি একটি X (গ্রহ "X") দিয়ে শুরু হয়েছে, এটি পৌরাণিক শোনাচ্ছে... এবং আমরা সেখানে আরও দেবীদের (যেমন সেডনা) আনার জন্য কাজ করছি। এছাড়াও, সেই সময়ে, টিভি শোটি তখনও প্রচারিত ছিল, যা বোঝায় যে আমরা কত সময় ধরে অনুসন্ধান করছি![৪০]
ব্রাউন একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন যে নামকরণ প্রক্রিয়া স্থবির ছিল:
একজন প্রতিবেদক [কেন চ্যাং][৪১] আমাকে দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস থেকে ডেকেছিলেন যিনি আমার কলেজের একজন বন্ধু ছিলেন, [এবং] ... আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তুমি কোন নামটি প্রস্তাব করেছ?" এবং আমি বললাম, "না, আমি বলব না।" তিনি বললেন, "আচ্ছা, যখন তোমরা নিজেদের মধ্যে কথা বল তখন তোমরা একে কি নামে ডাকো?" ...যতদূর আমার মনে আছে এটিই একমাত্র সময় ছিল যখন আমি সংবাদপত্রে কাউকে এটি বলেছিলাম, এবং তারপর এটি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, যা আমি কেবলমাত্র খারাপ অনুভব করেছি; আমি নামটি পছন্দ করি।[৪২]
আনুষ্ঠানিক নাম নির্বাচন[সম্পাদনা]

বিজ্ঞান বিষয়ক লেখক গভার্ট শিলিং এর মতে, ব্রাউন প্রথমে বস্তুটিকে "লীলা" বলতে চেয়েছিলেন, হিন্দু পুরাণে একটি ধারণার পরে যেটি ব্রহ্ম দ্বারা খেলা একটি খেলার ফলাফল হিসাবে বিশ্বকে বর্ণনা করেছিল।[৩৩] নামটি "লিলাহ" এ র মতো উচ্চারণ করা যেতে পারে, ব্রাউনের নবজাতক কন্যার নাম। আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হওয়ার আগে ব্রাউন তার নাম প্রকাশ না করার বিষয়ে সচেতন ছিলেন। তিনি এক বছর আগে সেডনার সাথে এটি করেছিলেন এবং প্রচণ্ড সমালোচনার শিকার হয়েছিলেন। যাইহোক, নিয়ম লঙ্ঘন ব্যতীত সেডনা নামের প্রতি কোন আপত্তি উত্থাপিত হয়নি এবং সেডনার জন্য কোন নাম প্রস্তাব করা হয়নি।[৪৩]
তিনি তার ব্যক্তিগত ওয়েব পেজের ঠিকানাটিকে /~mbrown/planetlila হিসাবে আবিষ্কারের ঘোষণা করে দিয়েছিলেন এবং হাউমিয়া আবিষ্কারের বিতর্কের পরে বিশৃঙ্খলার মধ্যে এটি পরিবর্তন করতে ভুলে গিয়েছিলেন। তার সহকর্মী জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের অযথা রাগ করার পরিবর্তে, তিনি কেবল বলেছিলেন যে ওয়েবপেজটির নামকরণ করা হয়েছিল তার মেয়ের জন্য এবং "লীলা" নামটি বাদ দেওয়া হয়েছিল।[৩৩]
ব্রাউন আরও অনুমান করেছিলেন যে দেবতা প্লুটোর স্ত্রী পার্সেফোন, বস্তুটির জন্য একটি ভাল নাম হবে।[২] কল্পবিজ্ঞান কাহিনীতে[৪৪] নামটি গ্রহের জন্য বেশ কয়েকবার ব্যবহার করা হয়েছে এবং তা জনসাধারণের কাছে জনপ্রিয় ছিল (নিউ সায়েন্টিস্ট ম্যাগাজিন দ্বারা পরিচালিত একটি পোল সহজেই জিতে নেয়)।[৪৫] ("জেনা", শুধুমাত্র একটি ডাকনাম হওয়া সত্ত্বেও, চতুর্থ বার ভাবা হয়) একবার বস্তুটিকে একটি বামন (এবং এইভাবে অপ্রধান) গ্রহ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করার পরে এই পছন্দটি সম্ভব ছিল না, কারণ ইতিমধ্যেই একই নামের একটি গৌণ গ্রহ ছিল, ৩৯৯ পার্সেফোন।[২]
আবিষ্কার দলটি ৬ই সেপ্টেম্বর, ২০০৬ তারিখে এরিস নামটি প্রস্তাব করেছিল। ১৩ই সেপ্টেম্বর, ২০০৬-এ, এটি আইএউ কর্তৃক সরকারী নাম হিসাবে গৃহীত হয়েছিল।[৪৬][৪৭] ব্রাউন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যেহেতু বস্তুটিকে এত দিন ধরে একটি গ্রহ হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল, তাই এটির অন্যান্য গ্রহের মতো গ্রিক বা রোমান পুরাণ থেকে একটি নাম প্রাপ্য।[৪২] গ্রহাণুগুলি গ্র্যাকো-রোমান নামের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা গ্রহণ করেছিল। এরিস, যাকে ব্রাউন তার প্রিয় দেবী হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন, ভাগ্যক্রমে অন্তর্ভুক্তি করতে পেয়েছিলেন। ২০০৬ সালে ব্রাউন বলেন, "এরিস লোকেদের মধ্যে কলহ ও বিভেদ সৃষ্টি করেছিল।"[৪৮]
জ্যোতির্বিদ্যায় গ্রহের প্রতীকগুলি আর বেশি ব্যবহৃত হয় না, তবে নাসা এরিসের জন্য হ্যান্ড অফ এরিস,⟨![]() ⟩ (U+2BF0), ব্যবহার করেছে।[৪৯] এটি ডিসকর্ডিয়ানিজমের ধর্মের একটি প্রতীক, যা দেবী এরিসের উপাসনা করে।[৫০] বেশিরভাগ জ্যোতিষীরা এই চিহ্নটি ব্যবহার করেন, আবার কেউ কেউ মঙ্গল গ্রহের মতো একটি প্রতীক ব্যবহার করেন কিন্তু তীরটি নীচের দিকে নির্দেশ করে:⟨
⟩ (U+2BF0), ব্যবহার করেছে।[৪৯] এটি ডিসকর্ডিয়ানিজমের ধর্মের একটি প্রতীক, যা দেবী এরিসের উপাসনা করে।[৫০] বেশিরভাগ জ্যোতিষীরা এই চিহ্নটি ব্যবহার করেন, আবার কেউ কেউ মঙ্গল গ্রহের মতো একটি প্রতীক ব্যবহার করেন কিন্তু তীরটি নীচের দিকে নির্দেশ করে:⟨![]() ⟩ (U+2BF1).[৫০] উভয় প্রতীকই ইউনিকোডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[৫১]
⟩ (U+2BF1).[৫০] উভয় প্রতীকই ইউনিকোডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[৫১]
শ্রেণিবিভাগ[সম্পাদনা]

এরিস একটি ট্রান্স-নেপচুনিয়ান বামন গ্রহ (প্লুটয়েড)।[৫২] এর কক্ষপথের বৈশিষ্ট্যগুলি আরও সুনির্দিষ্টভাবে এটিকে একটি বিক্ষিপ্ত-ডিস্ক অবজেক্ট (এসডিও), বা একটি টিএনও হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করে যা সৌরজগতের গঠনের সময় নেপচুনের সাথে মহাকর্ষীয় মিথস্ক্রিয়া অনুসরণ করে কুইপার বেল্ট থেকে আরও দূরবর্তী এবং অস্বাভাবিক কক্ষপথে "বিক্ষিপ্ত" হয়েছে। যদিও পরিচিত এসডিওগুলির মধ্যে এর উচ্চ কক্ষপথের প্রবণতা অস্বাভাবিক, তাত্ত্বিক মডেলগুলি প্রস্তাব করে যে কুইপার বেল্টের অভ্যন্তরীণ প্রান্তের কাছাকাছি বস্তুগুলি বাইরের বেল্টের বস্তুর তুলনায় উচ্চ প্রবণতা সহ কক্ষপথে ছড়িয়ে পড়েছিল।[৫৩]
যেহেতু এরিসকে প্রাথমিকভাবে প্লুটোর চেয়ে বড় বলে মনে করা হয়েছিল, এর আবিষ্কারের মিডিয়া রিপোর্টে এটিকে নাসা "দশম গ্রহ" হিসাবে বর্ণনা করেছিল।[৫৪] এর স্থিতি নিয়ে অনিশ্চয়তার প্রতিক্রিয়ায়, এবং প্লুটোকে একটি গ্রহ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা উচিত কিনা তা নিয়ে চলমান বিতর্কের কারণে, আইএইউ একটি জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের একটি দলকে গ্রহ শব্দটির একটি যথেষ্ট সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা তৈরি করার জন্য ভার অর্পণ করে। ২৪শে আগস্ট, ২০০৬ এ গৃহীত সৌরজগতের একটি গ্রহের সংজ্ঞা হিসাবে এটি ঘোষণা করা হয়েছিল। এই সময়ে, এরিস এবং প্লুটো উভয়কেই বামন গ্রহ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছিল, যা গ্রহের নতুন সংজ্ঞা থেকে আলাদা একটি বিভাগ।[৫৫] ব্রাউন এই শ্রেণিবিভাগে তার অনুমোদনের কথা বলেছে।[৫৬] আইএইউ পরবর্তীতে এরিসকে তার মাইনর প্ল্যানেট ক্যাটালগে যুক্ত করে, এটি (১৩৬১৯৯) এরিস-কে মনোনীত করে।[৩৯]
কক্ষপথ[সম্পাদনা]
এরিসের একটি কক্ষপথের আবর্তকাল ৫৫৯ বছর।[১৯] সূর্য (অ্যাফিলিয়ন) থেকে এর সর্বোচ্চ সম্ভাব্য দূরত্ব হল ৯৭.৫ এ ইউ, এবং এর নিকটতম (পেরিহেলিয়ন) হল ৩৮ এ ইউ।[১৯] যেহেতু পেরিহেলিয়নের সময়টি একটি নিরবচ্ছিন্ন দ্বি-শরীরের সমাধান ব্যবহার করে নির্বাচিত যুগে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, সেই যুগটি পেরিহিলিয়নের তারিখ থেকে যত বেশি হবে, ফলাফল তত কম সঠিক হবে। পেরিহিলিয়নের সময় সঠিকভাবে অনুমান করার জন্য সংখ্যাসূচক একীকরণ প্রয়োজন। জেপিএল হরাইজনস দ্বারা সংখ্যাসূচক একীকরণ দেখায় যে, এরিস ১৬৯৯ সালের দিকে পেরিহিলিয়নে এসেছিল,[১১] ১৯৭৭ সালের দিকে অ্যাফিলিয়নে এসেছিল,[১১] এবং ডিসেম্বর ২২৫৭ সালের দিকে পেরিহিলিয়নে ফিরে আসবে।[১১] আটটি গ্রহের বিপরীতে, যার কক্ষপথ সমস্ত পৃথিবীর মতো একই সমতলে অবস্থিত, এরিসের কক্ষপথটি অত্যন্ত বেশি কাত হয়ে আছে: এটি প্রায় ৪৪ ডিগ্রী কোণে গ্রহনধারে হেলে পড়েছে।[৬] যখন আবিষ্কৃত হয়, দীর্ঘ সময়ের ধূমকেতু এবং স্পেস প্রোব ছাড়া এরিস এবং এর উপগ্রহ সৌরজগতের সবচেয়ে দূরবর্তী পরিচিত বস্তু ছিল।[২][৫৭] এটি ২০১৮ সালে ২০১৮ ভিজি১৮ আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত সবচেয়ে দূরবর্তী পরিচিত বস্তু ছিল।[৫৮]
২০০৮ সালের হিসাবে, প্রায় চল্লিশটি পরিচিত টিএনও ছিল, বিশেষ করে ২০০৬ এসকিউ৩৭২, ২০০০ ওও৬৭ এবং সেডনা, যেগুলি বর্তমানে এরিসের তুলনায় সূর্যের কাছাকাছি, যদিও তাদের আধা-প্রধান অক্ষ এরিসের (৬৭.৮ এ ইউ) থেকে বড়।[৭]
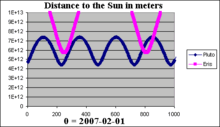
এরিসের কক্ষপথ অত্যন্ত উদ্ভট, এবং এরিসকে সূর্যের ৩৭.৯ এ ইউ -এর মধ্যে নিয়ে আসে, যা বিক্ষিপ্ত বস্তুর জন্য একটি সাধারণ পেরিহিলিয়ন।[৫৯] এটি প্লুটোর কক্ষপথের মধ্যে, কিন্তু এখনও নেপচুনের (~৩৭ এ ইউ ) সাথে সরাসরি মিথস্ক্রিয়া থেকে নিরাপদ।[৬০] অন্যদিকে, প্লুটো, অন্যান্য প্লুটিনোর মতো, একটি কম ঝোঁক এবং কম উদ্ভট কক্ষপথ অনুসরণ করে এবং কক্ষপথের অনুরণন দ্বারা সুরক্ষিত, নেপচুনের কক্ষপথ অতিক্রম করতে পারে।[৬১] প্রায় ৮০০ বছরে, এরিস কিছু সময়ের জন্য প্লুটোর চেয়ে সূর্যের কাছাকাছি থাকবে (বাম দিকের গ্রাফটি দেখুন)।
২০০৭ সালের হিসাবে, এরিসের আপাত মাত্রা ছিল ১৮.৭, যা কিছু অপেশাদার টেলিস্কোপের জন্য এটিকে সনাক্ত করার মতো যথেষ্ট উজ্জ্বল করে তোলে।[৬২] একটি সিসিডি সহ ২০০-মিলিমিটার (৭.৯ ইঞ্চি) টেলিস্কোপ অনুকূল পরিস্থিতিতে এরিসকে সনাক্ত করতে পারে।[চ] বৃহৎ বাইরের সৌরজগতের বস্তুগুলির জন্য অনুসন্ধানগুলি গ্রহন সমতলে মনোনিবেশ করে, যেখানে বেশিরভাগ বস্তু পাওয়া যায়।[৬৩]
এর কক্ষপথের উচ্চ প্রবণতার কারণে, এরিস ঐতিহ্যগত রাশিচক্রের কয়েকটি নক্ষত্রমণ্ডলের মধ্য দিয়ে যায়; এটি এখন সেটাস নক্ষত্রে রয়েছে।১৮৭৬ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত এটি ভাস্কর্যতে এবং ১৮৪০ থেকে ১৮৭৫ পর্যন্ত ফিনিক্সে ছিল। ২০৩৬ সালে এটি মীন রাশিতে প্রবেশ করবে এবং ২০৬৫ পর্যন্ত সেখানে থাকবে, যখন এটি মেষ রাশিতে প্রবেশ করবে।[১১] তারপরে এটি উত্তর আকাশে চলে যাবে, ২১২৮ সালে পার্সিয়াসে প্রবেশ করবে এবং ২১৭৩ সালে ক্যামেলোপার্ডালিসে (যেখানে এটি তার সবচেয়ে উত্তরের পতনে পৌঁছাবে)।
ঘূর্ণন[সম্পাদনা]
এরিস খুব কম উজ্জ্বলতার তারতম্য প্রদর্শন করে কারণ এটি তার অভিন্ন পৃষ্ঠের কারণে ঘোরে, যার ফলে এর ঘূর্ণনের সময়কাল পরিমাপ করা কঠিন হয়।[৬৪][১৫] এরিসের উজ্জ্বলতার সুনির্দিষ্ট দীর্ঘমেয়াদী পর্যবেক্ষণ ইঙ্গিত দেয় যে এটি জোয়ারের সাথে তার উপগ্রহ ডিসনোমিয়ায় আটকে আছে, এর একটি ঘূর্ণনের সময়কাল উপগ্রহটির কক্ষপথের সময়কালের ১৫.৭৮ দিনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।[১৫] ডিসনোমিয়াও জোয়ারের সাথে এরিসের সঙ্গে লক করা হয়েছে, যা প্লুটো এবং ক্যারনের পরে এরিস-ডাইসনোমিয়া ঘূর্ণনের দ্বিতীয় পরিচিত ডাবল-সিঙ্ক্রোনাস সিস্টেম। এরিসের ঘূর্ণন সময়ের পূর্ববর্তী পরিমাপগুলি এরিসের ঘূর্ণনের অপর্যাপ্ত দীর্ঘমেয়াদী কভারেজের কারণে কয়েক ঘন্টা থেকে কয়েক দিনের মধ্যে অত্যন্ত অনিশ্চিত মান প্রাপ্ত হয়েছিল।[৬৪][৬৫][৬৬] এরিসের অক্ষীয় কাত পরিমাপ করা হয়নি,[১৪] তবে এটি যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমান করা যেতে পারে যে এটি ডিসনোমিয়ার অরবিটাল প্রবণতার মতো, যা গ্রহের ক্ষেত্রে প্রায় ৭৮ ডিগ্রি হবে।[১৬] যদি তাই হয়, তবে ২০১৮ সালে এরিসের উত্তর গোলার্ধের বেশিরভাগ অংশ সূর্যালোক দ্বারা আলোকিত হবে, গোলার্ধের ৩০% ধ্রুবক আলোকসজ্জার সম্মুখীন হবে।[১৬]
আকার, ভর এবং ঘনত্ব[সম্পাদনা]
| বছর | ব্যাসার্ধ | উৎস |
|---|---|---|
| ২০০৫ | ১,১৯৯ কিমি[৬৭] | হাবল |
| ২০০৭ | ১,৩০০ কিমি[৬৮] | স্পিটজার |
| ২০১১ | ১,১৬৩ কিমি[১২] | অকুলেশন |
কারিগরি সমস্যার কারণে গ্রাফ এই মূহুর্তে অস্থায়ীভাবে অনুপলব্ধ রয়েছে। |
নভেম্বর ২০১০ সালে, এরিস পৃথিবী থেকে এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে দূরবর্তী নাক্ষত্রিক জাদুবিদ্যার বিষয় ছিল।[১৩] এই ঘটনা থেকে লব্ধ প্রাথমিক তথ্য পূর্ববর্তী আকারের অনুমান সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে।[১৩] দলটি অক্টোবর ২০১১-তে অকুলেশন সহ ২৩২৬±১২ কিমি আনুমানিক ব্যাস সহ তাদের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করে।[১২]
এটি থেকে জানা যায়, এরিস ক্ষেত্রফল এবং ব্যাসের (যা ২৩৭২±৪ কিমি জুড়ে রয়েছে) হিসেবে প্লুটোর থেকে একটু ছোট, যদিও এরিস আরও বিশাল। এটি ০.৯৬ এর জ্যামিতিক অ্যালবেডোও নির্দেশ করে। এটা অনুমান করা হয় যে, তাপমাত্রার ওঠানামার কারণে ভূপৃষ্ঠের বরফগুলি পুনরায় পূরণ হয়, তাই উচ্চ অ্যালবেডো হয় কারণ এরিসের অদ্ভুত কক্ষপথ এটিকে সূর্যের কাছাকাছি এবং দূরে নিয়ে যায়।[২০]
এরিসের ভর অনেক বেশি নির্ভুলতার সাথে গণনা করা যেতে পারে। ডিসনোমিয়ার সময়কালের (১৫.৭৭৪ দিন) জন্য স্বীকৃত মানের উপর ভিত্তি করে[২৩][৬৯]——এরিস প্লুটোর চেয়ে ২৭% বেশি বিশাল। ২০১১ওকে অকুলেশনের ফলাফল ব্যবহার করে পাওয়া যায়, এরিসের ঘনত্ব ২.৫২±০.০৭ গ্রাম/সেমি3,[ছ] প্লুটোর তুলনায় যথেষ্ট ঘন, এবং এইভাবে এটি অবশ্যই মূলত পাথুরে পদার্থ দিয়ে গঠিত।[১২]
তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ উত্তাপের মডেলগুলি পরামর্শ দেয় যে এরিসের ম্যান্টল-কোর সীমানায় তরল জলের অভ্যন্তরীণ মহাসাগর থাকতে পারে।[৭০]
জুলাই ২০১৫ সালে, সূর্যকে প্রত্যক্ষভাবে প্রদক্ষিণ করা পরিচিত নবম বৃহত্তম বস্তু হিসেবে এরিসকে বিবেচনা করার পর, নিউ হরাইজনস মিশনের ক্লোজ-আপ ইমেজ থেকে আরো সঠিকভাবে নির্ধারণ করা হয় যে , পূর্বে চিন্তা করা হত যে, প্লুটোর আয়তন এরিসের তুলনায় সামান্য ছোট।[৭১] এরিস এখন পরিচিত দশম-বৃহত্তর বস্তু যা আয়তনের ভিত্তিতে সূর্যকে সরাসরি প্রদক্ষিণ করে , কিন্তু ভরের দিক থেকে নবম বৃহত্তম।
পৃষ্ঠ এবং বায়ুমণ্ডল[সম্পাদনা]

আবিষ্কার দলটি ২৫শে জানুয়ারী, ২০০৫-এ হাওয়াইয়ের ৮ মিটার জেমিনি নর্থ টেলিস্কোপে তৈরি বর্ণালী পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এরিসের প্রাথমিক সনাক্তকরণ করে। বস্তু থেকে ইনফ্রারেড আলো মিথেন বরফের উপস্থিতি প্রকাশ করে, যা ইঙ্গিত করে যে পৃষ্ঠটি প্লুটোর পৃষ্ঠের অনুরূপ হতে পারে, যেটি সেই সময়ে একমাত্র টিএনও ছিল যার ভূপৃষ্ঠে মিথেন ছিল এবং নেপচুনের উপগ্রহ ট্রাইটনের পৃষ্ঠেও মিথেন রয়েছে।[৭২]
এরিসের দূরবর্তী এককেন্দ্রিক কক্ষপথের কারণে, এর পৃষ্ঠের তাপমাত্রা প্রায় ৩০ এবং ৫৬ K (−২৪৩.২ এবং −২১৭.২ °সে; −৪০৫.৭ এবং −৩৫৮.৯ °ফা) এর মধ্যে পরিবর্তিত হতে পারে।[২]
প্লুটো এবং ট্রাইটন কিছুটা লালচে হলেও, এরিসকে প্রায় সাদা দেখায়।[২] মনে করা হয় যে, প্লুটোর লালচে রঙের পৃষ্ঠে থোলিন জমার কারণে এবং যেখানে এগুলি জমে থাকে তা পৃষ্ঠকে অন্ধকার করে, নিম্ন অ্যালবেডো উচ্চ তাপমাত্রা এবং মিথেন জমার বাষ্পীভবনের দিকে পরিচালিত করে। বিপরীতে, এরিস সূর্য থেকে যথেষ্ট দূরে যে মিথেন তার পৃষ্ঠে ঘনীভূত হতে পারে এমনকি যেখানে অ্যালবেডো কম থাকে। মিথেনের ঘনীভবন পৃষ্ঠের উপর অভিন্নভাবে কোনো অ্যালবেডো বৈপরীত্য হ্রাস করে এবং লাল থোলিনের কোনো জমাকে আবৃত করে।[৩১]
যদিও এরিস প্লুটোর চেয়ে সূর্যের থেকে তিনগুণ বেশি দূরে থাকতে পারে, তবে এটি এতটা কাছাকাছি আসে যে পৃষ্ঠের কিছু বরফ উষ্ণ হতে পারে। যেহেতু মিথেন অত্যন্ত উদ্বায়ী, এর উপস্থিতি বোঝায় যে, এরিস সর্বদা সৌরজগতের দূরবর্তী অঞ্চলে অবস্থান করে, যেখানে এটি মিথেন বরফ স্থায়ী হওয়ার জন্য যথেষ্ট ঠান্ডা, অথবা মহাকাশীয় দেহে গ্যাস যা বায়ুমণ্ডল থেকে চলে যায়, তা পুনরায় পূরণ করার জন্য মিথেনের অভ্যন্তরীণ উত্স রয়েছে । এটি অন্য একটি আবিষ্কৃত টিএনও, হাউমিয়ার পর্যবেক্ষণের সাথে বিপরীত, যা জলের বরফের উপস্থিতি প্রকাশ করে কিন্তু মিথেন নয়।[৭৩]
উপগ্রহ[সম্পাদনা]

২০০৫ সালে, হাওয়াইয়ের কেক টেলিস্কোপ অভিযোজিত অপটিক্স দলটি নতুন চালু করা লেজার গাইড তারকা অভিযোজিত অপটিক্স সিস্টেম ব্যবহার করে চারটি উজ্জ্বল টি এন ও (প্লুটো, মেকমেক, হাউমেয়া এবং এরিস) পর্যবেক্ষণ করে।[৭৪] ১০ই সেপ্টেম্বরে তোলা চিত্রগুলি থেকে এরিসের কক্ষপথে একটি উপগ্রহ প্রকাশ পায়। ইতিমধ্যে এরিসের জন্য ব্যবহৃত "জেনা" ডাকনামের সাথে মিল রেখে, ব্রাউনের দল টেলিভিশন যোদ্ধা রাজকুমারীর সাইডকিকের নামানুসারে উপগ্রহটিকে "গ্যাব্রিয়েল" ডাকনাম দেয়। যখন এরিস আইএইউ থেকে তার সরকারী নাম পায়, তখন উপগ্রহটির নাম হয় ডিসনোমিয়া, অনাচারের গ্রীক দেবীর নামানুসারে, যিনি এরিসের কন্যা ছিলেন। ব্রাউন বলেছেন যে তিনি তার স্ত্রীর নাম ডায়ান-এর সাথে মিল থাকার জন্য এটি বেছে নেন। নামটি এরিসের পুরানো অনানুষ্ঠানিক নাম জেনা-এর একটি তির্যক উল্লেখও ধরে রেখেছে, যা টেলিভিশনে লুসি ললেস দ্বারা চিত্রিত হয়েছিল।[৭৫]
| নাম | ব্যাস (কিমি) | আধা-প্রধান অক্ষ
(কিমি) |
ভর
(১০২২ কেজি) |
আবিষ্কারের তারিখ |
|---|---|---|---|---|
| এরিস | ২৩২৬±১২[১২] | >১.৬[খ] | ৫ই জানুয়ারি, ২০০৫ | |
| ডিসনোমিয়া | ৭০০±১১৫[৭৬] | ৩৭২৭৩±৬৪[১৪] | <০.০৫[১৫] | ১০ই সেপ্টেম্বর, ২০০৫[৭৪] |
অন্বেষণ[সম্পাদনা]
২০১৫ সালে সফল প্লুটো ফ্লাইবাইয়ের পরে এটির বর্ধিত অভিযানের অংশ হিসাবে এরিসকে ২০২০ সালের মে মাসে নিউ হরাইজনস মহাকাশযান দ্বারা দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল।[১৭] যদিও এরিস পৃথিবীর (৯৬ এ ইউ) চেয়ে নিউ হরাইজনস (১১২ এ ইউ) থেকে অনেক দূরে ছিল, তবে কুইপার বেল্টের ভিতরে মহাকাশযানের অনন্য সুবিধার স্থানটি উচ্চ পর্যায়ের কোণে এরিসের পর্যবেক্ষণের অনুমতি দেয় যা অন্যথায় পৃথিবী থেকে পাওয়া যায় না, যা হালকা বিক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্য এবং Eris এর পৃষ্ঠের ফেজ বক্ররেখা আচরণ নির্ধারণ করতে সাহায্য করে।[১৭]
২০১০-এর দশকে, কুইপার বেল্ট অন্বেষণ করার ফলো-অন মিশনের জন্য একাধিক গবেষণা হয়েছিল, যার মধ্যে এরিসকে একটি প্রার্থী হিসাবে মূল্যায়ন করা হয়েছিল।[৭৭] এটি গণনা করা হয়েছিল যে, ৩রা এপ্রিল, ২০৩২ বা ৭ই এপ্রিল, ২০৪৪-এর উৎক্ষেপণের তারিখের উপর ভিত্তি করে বৃহস্পতির মাধ্যাকর্ষণ-সহায়তা ব্যবহার করে এরিসের ফ্লাইবাই মিশনে ২৪.৬৬ বছর সময় লাগবে। মহাকাশযানটি আসার সময় এরিস সূর্য থেকে ৯২.০৩ বা ৯০.১৯ এ ইউ হবে।[৭৮]
আরও দেখুন[সম্পাদনা]
- চারিদিক পরিষ্কার করা
- গ্রহের পূর্বতন শ্রেণিবিভাগ
- সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরে সৌরজগতের বস্তুর তালিকা
- ট্রান্স-নেপচুনিয়ান বস্তুর তালিকা
- মেসোপ্ল্যানেট
ব্যাখ্যামূলক নোট[সম্পাদনা]
- ↑ ক খ Calculated from the mean radius
- ↑ ক খ The mass of Eris by itself is the difference between the mass of the system (১.৬৪৬৬×১০২২ কিg)[১৪] and mass of Dysnomia by itself (<৫×১০২০ কিg):[১৫] ১.৬৪৬৬×১০২২ কিg – ০.০৫×১০২২ কিg = ১.৫৯৬৬×১০২২ কিg ≈ ১.৬×১০২২ কিg.
- ↑ ক খ Calculated based on the known parameters
- ↑ ক খ Assumed axial tilt if Eris rotates in the same plane as Dysnomia's orbit, which is tilted 78.29° with respect to Eris's orbit.[১৪]
- ↑ Holler et al. (2021) determined an ecliptic latitude of β = 28.41° for the north pole of Dysnomia's orbit, which is assumed to be similarly oriented as Eris's rotational north pole.[১৪][১৬] β is the angular offset from the ecliptic plane, whereas inclination i with respect to the ecliptic is the angular offset from the ecliptic north pole at β = +90° ; i with respect to the ecliptic would be the complement of β. Therefore, given β = 28.41° , i = 90° – (28.41°) = 61.59° from the ecliptic.
- ↑ For an example of an amateur image of Eris, see Fred Bruenjes' Astronomy ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত নভেম্বর ২, ২০০৫ তারিখে
- ↑ Calculated by dividing the listed mass by the listed volume
তথ্যসূত্র[সম্পাদনা]
- ↑ "Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets"। IAU: Minor Planet Center। মে ১, ২০০৭। মে ৪, ২০১৬ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ মে ৫, ২০০৭।
- ↑ ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ Brown, Mike (২০০৬)। "The discovery of 2003 UB313 Eris, the largest known dwarf planet"। California Institute of Technology, Department of Geological Sciences। জুলাই ১৯, ২০১১ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ মে ৩, ২০০৭।
- ↑ ক খ Noah Webster (1884) A Practical Dictionary of the English Language
- ↑ ক খ গ টেমপ্লেট:Dict.com
- ↑ ক খ "Eris"। Lexico UK English Dictionary। Oxford University Press। জুলাই ৩১, ২০২০ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা।
টেমপ্লেট:MW - ↑ ক খ গ ঘ ঙ "JPL Small-Body Database Browser: 136199 Eris (2003 UB313)" (December 14, 2019, solution date)। এপ্রিল ১২, ২০১৬ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ফেব্রুয়ারি ২০, ২০২০।
- ↑ ক খ "List Of Centaurs and Scattered-Disk Objects"। Minor Planet Center। জুলাই ২৫, ২০১১ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ সেপ্টেম্বর ১০, ২০০৮।
- ↑ Buie, Marc (নভেম্বর ৬, ২০০৭)। "Orbit Fit and Astrometric record for 136199"। Deep Ecliptic Survey। জুলাই ৩০, ২০১২ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ডিসেম্বর ৮, ২০০৭।
- ↑ ক খ "David Morrison (2008) Ask an Astrobiologist"। এপ্রিল ২৫, ২০০৯ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা।
- ↑ ক খ Ian Douglas (2013) Semper Human
- ↑ ক খ গ ঘ ঙ "Horizons Batch for Eris at perihelion around 7 December 2257 ±2 weeks"। JPL Horizons (Perihelion occurs when rdot flips from negative to positive. The JPL SBDB generically (incorrectly) lists an unperturbed two-body perihelion date in 2260.)। Jet Propulsion Laboratory। ২০২২-০৯-০৪ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ সেপ্টেম্বর ১৩, ২০২১।
- ↑ ক খ গ ঘ ঙ চ ছ Sicardy, B.; Ortiz, J. L.; Assafin, M.; Jehin, E.; Maury, A.; Lellouch, E.; Gil-Hutton, R.; Braga-Ribas, F.; Colas, F.; Widemann (২০১১)। "Size, density, albedo and atmosphere limit of dwarf planet Eris from a stellar occultation" (পিডিএফ)। European Planetary Science Congress Abstracts। 6: 137। বিবকোড:2011epsc.conf..137S। অক্টোবর ১৮, ২০১১ তারিখে মূল (পিডিএফ) থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ সেপ্টেম্বর ১৪, ২০১১।
- ↑ ক খ গ Beatty, Kelly (নভেম্বর ২০১০)। "Former 'tenth planet' may be smaller than Pluto"। NewScientist.com। Sky and Telescope। ফেব্রুয়ারি ২৩, ২০১২ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ অক্টোবর ১৭, ২০১১।
- ↑ ক খ গ ঘ ঙ চ ছ Holler, Bryan J.; Grundy, William M.; Buie, Marc W.; Noll, Keith S. (ফেব্রুয়ারি ২০২১)। "The Eris/Dysnomia system I: The orbit of Dysnomia" (পিডিএফ)। Icarus। 355: 114130। arXiv:2009.13733
 । এসটুসিআইডি 221995416। ডিওআই:10.1016/j.icarus.2020.114130। বিবকোড:2021Icar..35514130H। 114130।
। এসটুসিআইডি 221995416। ডিওআই:10.1016/j.icarus.2020.114130। বিবকোড:2021Icar..35514130H। 114130।
- ↑ ক খ গ ঘ ঙ Szakáts, R.; Kiss, Cs.; Ortiz, J. L.; Morales, N.; Pál, A.; Müller, T. G.; ও অন্যান্য (২০২৩)। "Tidally locked rotation of the dwarf planet (136199) Eris discovered from long-term ground based and space photometry"। Astronomy & Astrophysics। L3: 669। arXiv:2211.07987
 । এসটুসিআইডি 253522934 Check
। এসটুসিআইডি 253522934 Check |s2cid=value (সাহায্য)। ডিওআই:10.1051/0004-6361/202245234। বিবকোড:2023A&A...669L...3S। - ↑ ক খ গ ঘ Holler, Bryan J.; Grundy, William; Buie, Marc W.; Noll, Keith (অক্টোবর ২০১৮)। Breaking the degeneracy of Eris' pole orientation। 50th DPS Meeting। American Astronomical Society। বিবকোড:2018DPS....5050903H। 509.03।
- ↑ ক খ গ Verbiscer, Anne J.; Helfenstein, Paul; Porter, Simon B.; Benecchi, Susan D.; Kavelaars, J. J.; Lauer, Tod R.; ও অন্যান্য (এপ্রিল ২০২২)। "The Diverse Shapes of Dwarf Planet and Large KBO Phase Curves Observed from New Horizons"। The Planetary Science Journal। 3 (4): 31। ডিওআই:10.3847/PSJ/ac63a6
 । বিবকোড:2022PSJ.....3...95V। 95।
। বিবকোড:2022PSJ.....3...95V। 95।
- ↑
Snodgrass, C.; Carry, B.; Dumas, C.; Hainaut, O. (ফেব্রুয়ারি ২০১০)। "Characterisation of candidate members of (136108) Haumea's family"। Astronomy and Astrophysics। 511: A72। arXiv:0912.3171
 । এসটুসিআইডি 62880843। ডিওআই:10.1051/0004-6361/200913031। বিবকোড:2010A&A...511A..72S।
। এসটুসিআইডি 62880843। ডিওআই:10.1051/0004-6361/200913031। বিবকোড:2010A&A...511A..72S।
- ↑ ক খ গ ঘ ঙ "AstDys (136199) Eris Ephemerides"। Department of Mathematics, University of Pisa, Italy। সংগ্রহের তারিখ ফেব্রুয়ারি ২৮, ২০১৬।
- ↑ ক খ M. E. Brown; E.L. Schaller; H.G. Roe; D. L. Rabinowitz; C. A. Trujillo (২০০৬)। "Direct measurement of the size of 2003 UB313 from the Hubble Space Telescope" (পিডিএফ)। The Astrophysical Journal। 643 (2): L61–L63। arXiv:astro-ph/0604245
 । এসটুসিআইডি 16487075। ডিওআই:10.1086/504843। বিবকোড:2006ApJ...643L..61B। সাইট সিয়ারX 10.1.1.256.601
। এসটুসিআইডি 16487075। ডিওআই:10.1086/504843। বিবকোড:2006ApJ...643L..61B। সাইট সিয়ারX 10.1.1.256.601  । সেপ্টেম্বর ১০, ২০০৮ তারিখে মূল (পিডিএফ) থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ এপ্রিল ১১, ২০০৬।
। সেপ্টেম্বর ১০, ২০০৮ তারিখে মূল (পিডিএফ) থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ এপ্রিল ১১, ২০০৬।
- ↑ "Eris Facts"। Space Facts।
- ↑ "Dwarf Planets"। Canadian Space Agency। মার্চ ১২, ২০২০। সংগ্রহের তারিখ জানুয়ারি ১, ২০২৩।
- ↑ ক খ গ Brown, Michael E.; Schaller, Emily L. (জুন ১৫, ২০০৭)। "The Mass of Dwarf Planet Eris" (পিডিএফ)। Science। 316 (5831): 1585। এসটুসিআইডি 21468196। ডিওআই:10.1126/science.1139415। পিএমআইডি 17569855। বিবকোড:2007Sci...316.1585B। মার্চ ৪, ২০১৬ তারিখে মূল (পিডিএফ) থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ সেপ্টেম্বর ২৭, ২০১৫।
- ↑ "Dwarf Planet Outweighs Pluto"। space.com। ২০০৭। জুন ১৭, ২০০৭ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ জুন ১৪, ২০০৭।
- ↑ "How Big Is Pluto? New Horizons Settles Decades-Long Debate"। www.nasa.gov। ২০১৫। জুলাই ১, ২০১৭ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ জুলাই ১৪, ২০১৫।
- ↑ "The IAU draft definition of "planet" and "plutons"" (সংবাদ বিজ্ঞপ্তি)। IAU। আগস্ট ১৬, ২০০৬। আগস্ট ২০, ২০০৬ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ আগস্ট ১৬, ২০০৬।
- ↑ Brown, Mike (২০১০)। "The shadowy hand of Eris"। Mike Brown's Planets। নভেম্বর ১১, ২০১০ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ নভেম্বর ৭, ২০১০।
- ↑ Brown, Mike (নভেম্বর ২২, ২০১০)। "How big is Pluto, anyway?"। Mike Brown's Planets। জুলাই ২১, ২০১১ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ নভেম্বর ২৩, ২০১০। (Franck Marchis on 2010-11-08)
- ↑ "How Big Is Pluto? New Horizons Settles Decades-Long Debate"। NASA। ২০১৫। জুলাই ১৩, ২০১৫ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ জুলাই ১৩, ২০১৫।
- ↑ Stern, S. A.; Grundy, W.; ও অন্যান্য (সেপ্টেম্বর ২০১৮)। "The Pluto System After New Horizons"। Annual Review of Astronomy and Astrophysics। 56: 357–392। arXiv:1712.05669
 । এসটুসিআইডি 119072504। ডিওআই:10.1146/annurev-astro-081817-051935। বিবকোড:2018ARA&A..56..357S। সংগ্রহের তারিখ এপ্রিল ৫, ২০২২।
। এসটুসিআইডি 119072504। ডিওআই:10.1146/annurev-astro-081817-051935। বিবকোড:2018ARA&A..56..357S। সংগ্রহের তারিখ এপ্রিল ৫, ২০২২।
- ↑ ক খ গ ঘ ঙ
M. E. Brown; C. A. Trujillo; D. L. Rabinowitz (২০০৫)। "Discovery of a Planetary-sized Object in the Scattered Kuiper Belt"। The Astrophysical Journal। 635 (1): L97–L100। arXiv:astro-ph/0508633
 । এসটুসিআইডি 1761936। ডিওআই:10.1086/499336। বিবকোড:2005ApJ...635L..97B।
। এসটুসিআইডি 1761936। ডিওআই:10.1086/499336। বিবকোড:2005ApJ...635L..97B।
- ↑ Thomas H. Maugh II; John Johnson Jr. (অক্টোবর ১৬, ২০০৫)। "His Stellar Discovery Is Eclipsed"। Los Angeles Times। অক্টোবর ১২, ২০১২ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ জুলাই ১৪, ২০০৮।
- ↑ ক খ গ Schilling, Govert (২০০৮)। The Hunt For Planet X। Springer। পৃষ্ঠা 214। আইএসবিএন 978-0-387-77804-4।
- ↑ Blue, Jennifer (সেপ্টেম্বর ১৪, ২০০৬)। "2003 UB 313 named Eris"। USGS Astrogeology Research Program। অক্টোবর ১৮, ২০০৬ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ জানুয়ারি ৩, ২০০৭।
- ↑ Brown, Mike। "New Planet"। web.gps.caltech.edu। মে ১৭, ২০১২ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ জানুয়ারি ৫, ২০১০।
- ↑ "Julia Sweeney and Michael E. Brown"। Hammer Conversations: KCET podcast। ২০০৭। অক্টোবর ৬, ২০০৮ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ অক্টোবর ১, ২০০৮।
- ↑ টেমপ্লেট:L&S
- ↑ "International Astronomical Association homepage"। সেপ্টেম্বর ৩০, ২০০৭ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ জানুয়ারি ৫, ২০০৭।
- ↑ ক খ Green, Daniel W. E. (সেপ্টেম্বর ১৩, ২০০৬)। "(134340) Pluto, (136199) Eris, and (136199) Eris I (Dysnomia)" (পিডিএফ)। IAU Circular। 8747: 1। বিবকোড:2006IAUC.8747....1G। ফেব্রুয়ারি ৫, ২০০৭ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ জানুয়ারি ১২, ২০১২।
- ↑ "Xena and Gabrielle" (পিডিএফ)। Status। জানুয়ারি ২০০৬। মার্চ ১৪, ২০১২ তারিখে মূল (পিডিএফ) থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ মে ৩, ২০০৭।
- ↑ Mike Brown (২০১২)। How I Killed Pluto and Why it Had it Coming। Spiegel & Grau। পৃষ্ঠা 159।
- ↑ ক খ Brown, Mike (২০০৭)। "Lowell Lectures in Astronomy"। WGBH। জুলাই ১৬, ২০০৮ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ জুলাই ১৩, ২০০৮।
- ↑ "M.P.C. 52733" (পিডিএফ)। Minor Planet Circulars। Minor Planet Center। ২০০৪। পৃষ্ঠা 1। জুলাই ২৫, ২০১১ তারিখে মূল (পিডিএফ) থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ আগস্ট ৩০, ২০১০।
- ↑ "Planet X Marks the Spot" (পিডিএফ)। TechRepublic। ২০০৬। সেপ্টেম্বর ১০, ২০০৮ তারিখে মূল (পিডিএফ) থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ জুলাই ১৩, ২০০৮।
- ↑ O'Neill, Sean (২০০৫)। "Your top 10 names for the tenth planet"। NewScientist। মে ১, ২০০৮ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ জুন ২৮, ২০০৮।
- ↑ "The Discovery of Eris, the Largest Known Dwarf Planet"। California Institute of Technology, Department of Geological Sciences। জুলাই ১৯, ২০১১ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ জানুয়ারি ৫, ২০০৭।
- ↑ "IAU0605: IAU Names Dwarf Planet Eris"। International Astronomical Union News। সেপ্টেম্বর ১৪, ২০০৬। জানুয়ারি ৪, ২০০৭ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ জানুয়ারি ৫, ২০০৭।
- ↑ Sullivan, Andy (২০০৬)। "Xena renamed Eris in planet shuffle"। Reuters। সংগ্রহের তারিখ জানুয়ারি ২৯, ২০২০।
- ↑ JPL/NASA (এপ্রিল ২২, ২০১৫)। "What is a Dwarf Planet?"। Jet Propulsion Laboratory। সংগ্রহের তারিখ ২০২১-০৯-২৪।
- ↑ ক খ Faulks, David (জুন ১২, ২০১৬)। "Eris and Sedna Symbols" (পিডিএফ)। unicode.org। মে ৮, ২০১৭ তারিখে মূল (পিডিএফ) থেকে আর্কাইভ করা।
- ↑ "Miscellaneous Symbols and Arrows" (পিডিএফ)। unicode.org। Unicode। ১৯৯১–২০২১। সংগ্রহের তারিখ ৬ আগস্ট ২০২২।
- ↑ "Pluto Now Called a Plutoid"। Space.com। জুন ১১, ২০০৮। জুন ১২, ২০০৮ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ জুন ১১, ২০০৮।
- ↑ Gomes R. S.; Gallardo T.; Fernández J. A.; Brunini A. (২০০৫)। "On the origin of the High-Perihelion Scattered Disk: the role of the Kozai mechanism and mean motion resonances"। Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy। 91 (1–2): 109–129। এসটুসিআইডি 18066500। ডিওআই:10.1007/s10569-004-4623-y। বিবকোড:2005CeMDA..91..109G।
- ↑ "NASA-Funded Scientists Discover Tenth Planet"। Jet Propulsion Laboratory। ২০০৫। মে ১৪, ২০০৭ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ মে ৩, ২০০৭।
- ↑ "IAU 2006 General Assembly: Resolutions 5 and 6" (পিডিএফ)। IAU। আগস্ট ২৪, ২০০৬। সেপ্টেম্বর ২৮, ২০০৬ তারিখে মূল (পিডিএফ) থেকে আর্কাইভ করা।
- ↑ Robert Roy Britt (২০০৬)। "Pluto Demoted: No Longer a Planet in Highly Controversial Definition"। space.com। ডিসেম্বর ২৭, ২০১০ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ মে ৩, ২০০৭।
- ↑ Peat, Chris। "Spacecraft escaping the Solar System"। Heavens-Above। মে ১১, ২০১৮ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ জানুয়ারি ২৫, ২০০৮।
- ↑ "Discovered: The Most-Distant Solar System Object Ever Observed"। Carnegie Science। ডিসেম্বর ১৭, ২০১৮। ডিসেম্বর ১৭, ২০১৮ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ডিসেম্বর ১৮, ২০১৮।
The second-most-distant observed Solar System object is Eris, at about 96 AU.
- ↑ Trujillo, Chadwick A.; Jewitt, David C.; Luu, Jane X. (ফেব্রুয়ারি ১, ২০০০)। "Population of the Scattered Kuiper Belt" (পিডিএফ)। The Astrophysical Journal। 529 (2): L103–L106। arXiv:astro-ph/9912428
 । এসটুসিআইডি 8240136। ডিওআই:10.1086/312467। পিএমআইডি 10622765। বিবকোড:2000ApJ...529L.103T। সাইট সিয়ারX 10.1.1.338.2682
। এসটুসিআইডি 8240136। ডিওআই:10.1086/312467। পিএমআইডি 10622765। বিবকোড:2000ApJ...529L.103T। সাইট সিয়ারX 10.1.1.338.2682  । আগস্ট ১২, ২০০৭ তারিখে মূল (পিডিএফ) থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ জুলাই ২, ২০০৮।
। আগস্ট ১২, ২০০৭ তারিখে মূল (পিডিএফ) থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ জুলাই ২, ২০০৮।
- ↑ Patryk Sofia Lykawka, Tadashi Mukai (জুলাই ২০০৭)। "Dynamical classification of trans-neptunian objects: Probing their origin, evolution, and interrelation"। Icarus। 189 (1): 213–232। ডিওআই:10.1016/j.icarus.2007.01.001। বিবকোড:2007Icar..189..213L।
- ↑ David Jewitt। "The Plutinos"। UCLA। সংগ্রহের তারিখ জানুয়ারি ২৯, ২০২০।
- ↑ H.-W.Lin; Y.-L.Wu; W.-H.Ip (২০০৭)। "Observations of dwarf planet (136199) Eris and other large TNOs on Lulin Observatory"। Advances in Space Research। 40 (2): 238–243। ডিওআই:10.1016/j.asr.2007.06.009। বিবকোড:2007AdSpR..40..238L।
- ↑ "Bye-Bye Planet Pluto"। Horizon। জুন ২২, ২০০৬। BBC।
- ↑ ক খ Duffard, R.; Ortiz, J. L.; Santos-Sanz, P.; Mora, A.; Gutiérrez, P. J.; Morales, N.; Guirado, D. (মার্চ ২০০৮)। "A study of photometric variations on the dwarf planet (136199) Eris" (পিডিএফ)। Astronomy & Astrophysics। 479 (3): 877–881। এসটুসিআইডি 54930853। ডিওআই:10.1051/0004-6361:20078619
 । বিবকোড:2008A&A...479..877D।
। বিবকোড:2008A&A...479..877D।
- ↑ Roe, Henry G.; Pike, Rosemary E.; Brown, Michael E. (ডিসেম্বর ২০০৮)। "Tentative detection of the rotation of Eris"। Icarus। 198 (2): 459–464। arXiv:0808.4130
 । এসটুসিআইডি 16069419। ডিওআই:10.1016/j.icarus.2008.08.001। বিবকোড:2008Icar..198..459R।
। এসটুসিআইডি 16069419। ডিওআই:10.1016/j.icarus.2008.08.001। বিবকোড:2008Icar..198..459R।
- ↑ Holler, B. J.; Benecchi, S. D.; Mommert, M.; Bauer, J. (অক্টোবর ২০২০)। The Not-Quite-Synchronous Rotation Periods of Eris and Dysnomia। 52nd DPS Meeting। 52। American Astronomical Society। বিবকোড:2020DPS....5230706H। 307.06।
- ↑ "Hubble Finds 'Tenth Planet' Slightly Larger Than Pluto"। NASA। এপ্রিল ১১, ২০০৬। আগস্ট ২৯, ২০০৮ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ আগস্ট ২৯, ২০০৮।
- ↑
John Stansberry; Will Grundy; Mike Brown; John Spencer; David Trilling; Dale Cruikshank; Jean-Luc Margot (২০০৭)। Physical Properties of Kuiper Belt and Centaur Objects: Constraints from Spitzer Space Telescope। arXiv:astro-ph/0702538
 । বিবকোড:2008ssbn.book..161S।
। বিবকোড:2008ssbn.book..161S।
- ↑ Brown, Mike (২০০৭)। "Dysnomia, the moon of Eris"। Caltech। জুলাই ১৭, ২০১২ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ জুন ১৪, ২০০৭।
- ↑ Hussmann, Hauke; Sohl, Frank; Spohn, Tilman (নভেম্বর ২০০৬)। "Subsurface oceans and deep interiors of medium-sized outer planet satellites and large trans-neptunian objects" (পিডিএফ)। Icarus। 185 (1): 258–273। ডিওআই:10.1016/j.icarus.2006.06.005। বিবকোড:2006Icar..185..258H। আগস্ট ৩১, ২০১৫ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ডিসেম্বর ২, ২০১৭।
- ↑ "New Horizons Probe Finds Out Pluto's Bigger (and Icier) Than We Thought"। NBC News। জুলাই ১৩, ২০১৫। জুলাই ১৩, ২০১৫ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ জুলাই ১৩, ২০১৫।
- ↑ "Gemini Observatory Shows That "10th Planet" Has a Pluto-Like Surface"। Gemini Observatory। ২০০৫। মার্চ ১১, ২০০৭ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ মে ৩, ২০০৭।
- ↑ J. Licandro; W. M. Grundy; N. Pinilla-Alonso; P. Leisy (২০০৬)। "Visible spectroscopy of 2003 UB313: evidence for N2 ice on the surface of the largest TNO" (পিডিএফ)। Astronomy and Astrophysics। 458 (1): L5–L8। arXiv:astro-ph/0608044
 । এসটুসিআইডি 31587702। ডিওআই:10.1051/0004-6361:20066028। বিবকোড:2006A&A...458L...5L। নভেম্বর ২১, ২০০৮ তারিখে মূল (পিডিএফ) থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ নভেম্বর ১৪, ২০০৬।
। এসটুসিআইডি 31587702। ডিওআই:10.1051/0004-6361:20066028। বিবকোড:2006A&A...458L...5L। নভেম্বর ২১, ২০০৮ তারিখে মূল (পিডিএফ) থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ নভেম্বর ১৪, ২০০৬।
- ↑ ক খ Brown, M. E.; Van Dam, M. A.; Bouchez, A. H.; Le Mignant, D.; Campbell, R. D.; Chin, J. C. Y.; Conrad, A.; Hartman, S. K.; Johansson, E. M.; Lafon, R. E.; Rabinowitz, D. L. Rabinowitz; Stomski, P. J. Jr.; Summers, D. M.; Trujillo, C. A.; Wizinowich, P. L. (২০০৬)। "Satellites of the Largest Kuiper Belt Objects" (পিডিএফ)। The Astrophysical Journal। 639 (1): L43–L46। arXiv:astro-ph/0510029
 । এসটুসিআইডি 2578831। ডিওআই:10.1086/501524। বিবকোড:2006ApJ...639L..43B। নভেম্বর ৩, ২০১৩ তারিখে মূল (পিডিএফ) থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ অক্টোবর ১৯, ২০১১।
। এসটুসিআইডি 2578831। ডিওআই:10.1086/501524। বিবকোড:2006ApJ...639L..43B। নভেম্বর ৩, ২০১৩ তারিখে মূল (পিডিএফ) থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ অক্টোবর ১৯, ২০১১।
- ↑ Tytell, David (২০০৬)। "All Hail Eris and Dysnomia"। Sky and Telescope। ডিসেম্বর ২৭, ২০১৪ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ জানুয়ারি ৫, ২০১০।
- ↑ Brown, Michael E.; Butler, Bryan J. (সেপ্টেম্বর ১৮, ২০১৮)। "Medium-sized Satellites of Large Kuiper Belt Objects"। The Astronomical Journal। 156 (4): 164। arXiv:1801.07221
 । আইএসএসএন 1538-3881। এসটুসিআইডি 119343798। ডিওআই:10.3847/1538-3881/aad9f2। বিবকোড:2018AJ....156..164B।
। আইএসএসএন 1538-3881। এসটুসিআইডি 119343798। ডিওআই:10.3847/1538-3881/aad9f2। বিবকোড:2018AJ....156..164B।
- ↑ "SwRI team makes breakthroughs studying Pluto orbiter mission"। Astrobiology Magazine (ইংরেজি ভাষায়)। অক্টোবর ২৫, ২০১৮। Archived from the original on ২০১৮-১০-২৮। সংগ্রহের তারিখ অক্টোবর ২৭, ২০১৮।
- ↑ McGranaghan, R.; Sagan, B.; Dove, G.; Tullos, A.; Lyne, J. E.; Emery, J. P. (২০১১)। "A Survey of Mission Opportunities to Trans-Neptunian Objects"। Journal of the British Interplanetary Society। 64: 296–303। বিবকোড:2011JBIS...64..296M।
বহি:সংযোগ[সম্পাদনা]
- CS1 errors: S2CID
- Minor planet object articles (numbered)
- সৌরজগৎ
- Eris (dwarf planet)
- Astronomical objects discovered in 2005
- Binary trans-Neptunian objects
- Discoveries by Chad Trujillo
- Discoveries by David L. Rabinowitz
- Discoveries by Michael E. Brown
- Dwarf planets
- Named minor planets
- Objects observed by stellar occultation
- Pluto's planethood
- Scattered disc and detached objects
- Eris (mythology)
- বামন গ্রহ
- নামকরণ করা গ্রহাণু