জৈন ধর্ম: সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য
আফতাবুজ্জামান (আলোচনা | অবদান) →শীর্ষ: বাংলা উইকিতে অপ্রয়োজনীয়, বরং আমাদের এখানে বাংলা উচ্চারণ দেওয়া উচিত |
অসম্পাদনা সারাংশ নেই ট্যাগ: দ্ব্যর্থতা নিরসন পাতায় সংযোগ |
||
| ১ নং লাইন: | ১ নং লাইন: | ||
{{Redirect|জৈন}} |
|||
{{infobox Jainism}} |
|||
[[File:Ahimsa Jainism Gradient.jpg|thumb|upright=0.5|জৈনধর্মে হাত [[জৈনধর্মে অহিংসা|অহিংসার]], চক্র [[ধর্মচক্র|ধর্মচক্রের]] এবং হাতের নিবৃত্ত করার ভঙ্গিটি সংসার অর্থাৎ মৃত্যুর পরে আত্মার অন্য দেহে গমনের প্রতীক।]] |
|||
'''জৈনধর্ম''' (প্রথাগত নাম '''জিন সাশন''' বা '''জৈন [[ধর্ম (জৈনধর্ম)|ধর্ম]]''') {{sfn|Sangave|2006|p=15}} হল একটি [[ভারতীয় ধর্ম]]। এই ধর্ম সকল জীবিত প্রাণীর প্রতি অহিংসার শিক্ষা দেয়। জৈন ধর্মাবলম্বীরা মনে করেন অহিংসা ও আত্ম-সংযম হল মোক্ষ এবং জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তিলাভের পন্থা। |
|||
{{জৈনধর্ম}} |
|||
'''জৈনধর্ম''' ({{IPAc-en|ˈ|dʒ|eɪ|n|ɪ|z|əm}}),<ref>{{citation|title="Jainism" (ODE)|url=http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/Jainism|website=অক্সফোর্ড ডিকশনারিজ}}</ref> হল একটি প্রাচীন [[ভারতীয় ধর্ম]]। ধর্মটির আধ্যাত্মিক ধ্যানধারণা ও ইতিহাসের সূত্রপাত ঘটেছিল এই ধর্মের আদি প্রবর্তক হিসেবে কথিত চব্বিশ জন [[তীর্থঙ্কর|তীর্থংকরের]] এক পরম্পরার মাধ্যমে।<ref>{{citation|title=তীর্থংকর|url=https://www.jainismknowledge.com/2020/05/jain-dharm-me-tirthankar-kya-hota-hai.html|website=জৈনিজম নলেজ}}</ref> প্রথম তীর্থংকরের নাম [[ঋষভনাথ]]। বর্তমানে তিনি "আদিনাথ ভগবান" নামেও পরিচিত। জৈনরা বিশ্বাস করেন, ঋষভনাথ জন্মগ্রহণ করেছিলেন বহু লক্ষ বছর আগে। ত্রয়োবিংশ তীর্থংকর [[পার্শ্বনাথ]] খ্রিস্টপূর্ব ৯০০ অব্দ এবং চতুর্বিংশ তীর্থংকর [[মহাবীর]] খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ অব্দ নাগাদ জন্মগ্রহণ করেন। জৈন ধর্মবিশ্বাসে এই ধর্ম হল এক চিরন্তন [[ধর্ম (জৈনধর্ম)|ধর্ম]] এবং তীর্থংকরগণ [[জৈন সৃষ্টিতত্ত্ব|মহাবিশ্বের]] প্রতিটি চক্রে মানবসমাজকে পথ প্রদর্শন করার জন্য আবির্ভূত হয়ে থাকেন। |
|||
জৈনদের প্রধান ধর্মীয় নীতিগুলি হল [[জৈনধর্মে অহিংসা|অহিংসা]], [[অনেকান্তবাদ]] (বহুত্ববাদ), [[অপরিগ্রহ]] (অনাসক্তি) ও [[সন্ন্যাস]] (ইন্দ্রিয় সংযম)। ধর্মপ্রাণ জৈনেরা পাঁচটি প্রধান প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন: অহিংসা, [[সত্য]], [[অস্তেয়]] (চুরি না করা), [[ব্রহ্মচর্য]] (যৌন-সংযম) ও অপরিগ্রহ। জৈন সংস্কৃতির উপর এই নীতিগুলির প্রভাব ব্যাপক। যেমন, এই নীতির ফলেই জৈনরা প্রধানত নিরামিশাষী। এই ধর্মের আদর্শবাক্য হল ''[[পরস্পরোপগ্রহো জীবনাম]]'' (আত্মার কার্য পরস্পরকে সহায়তা করা) এবং ''[[ণমোকার মন্ত্র]]'' হল জৈনদের সর্বাপেক্ষা অধিক পরিচিত ও মৌলিক প্রার্থনামন্ত্র। |
|||
"জৈন" শব্দটি এসেছে [[সংস্কৃত]] "জিন" (অর্থাৎ, জয়ী) শব্দটি থেকে। যে মানুষ আসক্তি, আকাঙ্ক্ষা, ক্রোধ, অহংকার, লোভ ইত্যাদি আন্তরিক আবেগগুলিকে জয় করেছেন এবং সেই জয়ের মাধ্যমে পবিত্র অনন্ত জ্ঞান ([[কেবল জ্ঞান]]) লাভ করেছেন, তাঁকেই "জিন" বলা হয়। "জিন"দের আচরিত ও প্রচারিত পথের অনুগামীদের বলে "জৈন"।{{sfn|Sangave|2006|p=15}}{{sfn|Jain|1998|p=11}}{{sfn|Sangave|2001|p=164}} |
|||
জৈনধর্ম বিশ্বের প্রাচীনতম ধর্মগুলির অন্যতম। এই ধর্ম দু’টি প্রধান প্রাচীন সম্প্রদায়ে বিভক্ত: [[দিগম্বর]] ও [[শ্বেতাম্বর]]। কৃচ্ছসাধনের নিয়ম, স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক এবং কোন ধর্মগ্রন্থগুলি প্রামাণ্য সেই নিয়ে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু মতভেদ রয়েছে। তবে দুই সম্প্রদায়েই ভিক্ষু সাধু ও সাধ্বীদের (সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী) ভার শ্রাবক ও শ্রাবিকারাই (গৃহী পুরুষ ও নারী) বহন করেন। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ জৈনধর্মের অনুগামী। এঁদের অধিকাংশই [[ভারতে জৈনধর্ম|ভারতে]] বসবাস করেন। ভারতের বাইরে [[কানাডায় জৈনধর্ম|কানাডা]], [[ইউরোপে জৈনধর্ম|ইউরোপ]] ও [[মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জৈনধর্ম|মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে]] বহুসংখ্যক জৈন বাস করেন। [[জাপানে জৈনধর্ম|জাপানেও]] জৈনদের জনসংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেদেশে পাঁচ হাজারেরও বেশি জাপানি পরিবার জৈনধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে। জৈনদের প্রধান উৎসবগুলির অন্যতম হল [[পর্যুষণ]], দশলক্ষণ, অষ্টনিকা, [[মহাবীর জন্ম কল্যাণক]] ও [[দীপাবলি (জৈনধর্ম)|দীপাবলি]]। |
|||
জৈনধর্ম [[শ্রমণ]] প্রথা থেকে উদ্গত ধর্মমত। এটি বিশ্বের প্রাচীনতম ধর্মমতগুলির অন্যতম।<ref name="flugelP">{{Citation|last=Flügel|first=Peter|title=Encyclopedia of Global Studies|year=2012|editor=Anheier, Helmut K and Juergensmeyer, Mark|chapter=Jainism|volume=3|location=Thousand Oakes|publisher=Sage|page=975}}</ref> জৈনরা তাঁদের ইতিহাসে চব্বিশজন [[তীর্থঙ্কর|তীর্থঙ্করের]] কথা উল্লেখ করেন। এঁদের শিক্ষাই জৈনধর্মের মূল ভিত্তি। প্রথম তীর্থঙ্করের নাম [[ঋষভ (জৈন তীর্থঙ্কর)|ঋষভ]] এবং সর্বশেষ তীর্থঙ্করের নাম [[মহাবীর]]।।<ref>Larson, Gerald James (1995) ''India’s Agony over religion '' SUNY Press {{আইএসবিএন|0-7914-2412-X}} . “There is some evidence that Jain traditions may be even older than the Buddhist traditions, possibly going back to the time of the Indus valley civilization, and that Vardhamana rather than being a “founder” per se was, rather, simply a primary spokesman for much older tradition. Page 27”</ref><ref>Varni, Jinendra; Ed. Prof. Sagarmal Jain, Translated Justice T.K. Tukol and Dr. K.K. Dixit (1993). ''{{IAST|Samaṇ Suttaṁ}}.'' New Delhi: Bhagwan Mahavir memorial Samiti. “The Historians have so far fully recognized the truth that Tirthankara Mahavira was not the founder of the religion. He was preceded by many tirthankaras. He merely reiterated and rejuvenated that religion. It is correct that history has not been able to trace the origin of the Jaina religion; but historical evidence now available and the result of dispassionate researches in literature have established that Jainism is undoubtably an ancient religion.” Pp. xii – xiii of introduction by Justice T.K.Tutkol and Dr. K.K. Dixit.</ref><ref>Edward Craig (1998) ''Routledge Encyclopedia of Philosophy'', Taylor & Francis {{আইএসবিএন|0-415-07310-3}} “One significant difference between Mahavira and Buddha is that Mahavira was not a founder of a new movement, but rather a reformer of the teachings of his predecessor, Parsva.” p. 33</ref><ref>Joel Diederik Beversluis (2000) In: ''Sourcebook of the World's Religions: An Interfaith Guide to Religion and Spirituality'', New World Library : Novato, CA {{আইএসবিএন|1-57731-121-3}} Originating on the Indian sub-continent, Jainism is one of the oldest religion of its homeland and indeed the world, having pre-historic origins before 3000 BC and the propagation of Indo-Aryan culture…. p. 81</ref><ref>Jainism by Mrs. N.R. Guseva p.44</ref> |
|||
==ধর্মবিশ্বাস ও দর্শন== |
|||
ভারতে জৈন ধর্মবলম্বীদের সংখ্যা প্রায় ১০,২০০,০০০।<ref>[http://www.censusindia.gov.in/Census_Data_2001/India_at_glance/religion.aspx Indian Census]</ref> এছাড়া [[উত্তর আমেরিকা]], [[পশ্চিম ইউরোপ]], [[দূরপ্রাচ্য]], [[অস্ট্রেলিয়া]] ও বিশ্বের অন্যত্রও অভিবাসী জৈনদের দেখা মেলে।<ref>Estimates for the population of Jains differ from just over four million to twelve million due to difficulties of Jain identity, with Jains in some areas counted as a Hindu sect. Many Jains do not return Jainism as their religion on census forms for various reasons such as certain Jain castes considering themselves both Hindu and Jain. Following a major advertising campaign urging Jains to register as such, the 1981 Census of India returned 3.19 million Jains. This was estimated at the time to be at least half the true number. There are an estimated 25,000 Jains in Europe (mostly in England), 21,000 in Africa, 20,000 plus in North America and 5,000 in the rest of Asia.</ref> ভারতের অপরাপর ধর্মমত, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জৈনদের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে বৃত্তিদানের একটি প্রাচীন প্রথা জৈনদের মধ্যে আজও বিদ্যমান; এবং ভারতে এই সম্প্রদায়ের সাক্ষরতার হার অত্যন্ত উচ্চ।<ref>[http://pib.nic.in/release/rel_print_page1.asp?relid=3724 Press Information Bureau, Government of India]</ref><ref>[http://www.censusindia.net Census of India 2001]</ref> শুধু তাই নয়, জৈন গ্রন্থাগারগুলি দেশের প্রাচীনতম গ্রন্থাগারও বটে।<ref>The Jain Knowledge Warehouses: Traditional Libraries in India, John E. Cort, Journal of the American Oriental Society, Vol. 115, No. 1 (January - March, 1995), pp. 77–87</ref> |
|||
{{Main|জৈন দর্শন}} |
|||
জৈনধর্ম হল একটি [[ঈশ্বর-নিরপেক্ষতাবাদ|ঈশ্বর-নিরপেক্ষতাবাদী]] ধর্ম। এই ধর্মের পূর্বাভাস অনুযায়ী, মহাবিশ্ব [[বস্তু দ্বৈতবাদ|বস্তু দ্বৈতবাদের]] নীতিকে লঙ্ঘন না করেই বিবর্তিত হচ্ছে{{sfn|ইয়ানডেল|১৯৯৯|p=২৪৩}} এবং [[মনঃশারীরিক সমান্তরালতা|সমান্তরালতা]] ও [[মিথষ্ক্রিয়াবাদ (মনের দর্শন)|মিথষ্ক্রিয়তাবাদের]] মূলসূত্রের মধ্যবর্তী ভূমিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্বাহিত হচ্ছে।{{sfn|সিনহা|১৯৪৪|p=২০}} |
|||
===দ্রব্য (বস্তু) === |
|||
==মতবাদ== |
|||
{{Main|দ্রব্য (জৈনধর্ম)}} |
|||
{{Jainism}} |
|||
[[সংস্কৃত ভাষা|সংস্কৃত ভাষায়]] "দ্রব্য" শব্দটির অর্থ সারবস্তু বা সত্ত্বা।{{sfn|গ্রিমস|১৯৯৬|pp=১১৮–১১৯}} [[জৈন দর্শন]] অনুযায়ী, মহাবিশ্ব ছয়টি চিরন্তন দ্রব্য দ্বারা গঠিত: চেতন সত্ত্বা বা আত্মা ("[[জীব (জৈনধর্ম)|জীব]]"), অচেতন বস্তু বা পদার্থ ("[[পুদ্গল]]"), গতির মূলসূত্র ("[[ধর্ম (জৈনধর্ম)|ধর্ম]]"), বিরামের মূলসূত্র ("[[অধর্ম]]"), মহাশূন্য ("[[আকাশ (জৈনধর্ম)|আকাশ]]") ও সময় ("[[কাল (সময়)|কাল]]")।{{sfn|নেমিচন্দ্র|বলবীর|২০১০|p=ভূমিকার প্রথম পৃষ্ঠা}}{{sfn|গ্রিমস|১৯৯৬|pp=১১৮–১১৯}} শেষোক্ত পাঁচটি দ্রব্যকে একত্রে "অজীব" (জড় পদার্থ) নামে অভিহিত করা হয়।{{sfn|গ্রিমস|১৯৯৬|pp=১১৮–১১৯}} জৈন দার্শনিকগণ একটি দ্রব্যকে একটি দেহ বা সত্ত্বার থেকে স্বতন্ত্র জ্ঞান করেন এবং দ্রব্যকে এক সাধারণ অবিনশ্বর উপাদান বলে ঘোষণা করে দেহ বা সত্ত্বাকে এক বা একাধিক দ্রব্য দ্বারা নির্মিত তথা নশ্বর যৌগ বলে উল্লেখ করেন।{{sfn|চম্পৎ রাই জৈন|১৯১৭|p=১৫}} |
|||
===অহিংসা=== |
|||
{{মূল নিবন্ধ|জৈনধর্মে অহিংসা}} |
|||
[[File:Ahimsa.svg|thumb|upright|হাতের তালুতে চক্রের চিহ্ন। এটি অহিংসার প্রতীক। মধ্যে ‘অহিংসা’ কথাটি লেখা আছে। চক্রটি [[ধর্মচক্র|ধর্মচক্রের]] প্রতীক। সত্য ও অহিংসার পথে নিরন্তর যাত্রার মাধ্যমে জন্ম-মৃত্যুর চক্রের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কথাটি এই প্রতীকের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে।]] |
|||
[[জৈনধর্মে অহিংসা|অহিংসা]] জৈনধর্মের প্রধান ও সর্বাধিক পরিচিত বৈশিষ্ট্য।<ref>{{harvnb|Dundas|2002|p=160}}</ref> কোনোরকম আবেগের তাড়নায় কোনো জীবিত প্রাণীকে হত্যা করাকেই জৈনধর্মে ‘হিংসা’ বলা হয়। এই ধরনের কাজ থেকে দূরে থাকাই জৈনধর্মে ‘অহিংসা’ নামে পরিচিত।{{sfn|Jain|2012|p=34}} প্রতিদিনের কাজকর্মে অহিংসার আদর্শটিকে প্রাধান্য দেওয়া জৈনধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।<ref>{{harvnb|Sethia|2004|p=2}}</ref><ref>{{harvnb|Dundas|2002|pp=176–177}}</ref> প্রত্যেক মানুষ নিজেদের মধ্যে বাক্যালাপ ও কোনোরকম আদানপ্রদানের সময় অহিংসার চর্চা করবে এবং কাজ, বাক্য বা চিন্তার মাধ্যমে অন্যকে আঘাত করা থেকে বিরত থাকবে – এই হল জৈনদের অহিংসা আদর্শের মূল কথা।<ref>{{harvnb|Shah|1987|p=20}}</ref> |
|||
===তত্ত্ব (সত্য)=== |
|||
মানুষ ছাড়াও সমস্ত জীবিত প্রাণীর প্রতিই জৈনরা অহিংসা ব্রত পালন করেন। এই আদর্শ যেহেতু বাস্তবক্ষেত্রে সম্পূর্ণ রূপে প্রয়োগ করা অসম্ভব, সেহেতু জৈনরা একটি ক্রমোচ্চ শ্রেণীশৃঙ্খলা মেনে চলেন। এই শ্রেণীশৃঙ্খলায় মানুষের পরে পশুপক্ষী, তারপর কীটপতঙ্গ ও তারপর গাছপালার স্থান রয়েছে। এই কারণেই জৈন ধর্মানুশীলনে নিরামিষ আহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অধিকাংশ জৈন দুগ্ধজাত নিরামিষ খাবার খেয়ে থাকেন। দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনের সময় যদি পশুদের প্রতি হিংসাত্মক আচরণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে, সেক্ষেত্রে সাধারণ নিরামিষ আহারই গ্রহণ করার নিয়ম। মানুষ ও পশুপাখির পর কীটপতঙ্গরা জৈন ধর্মানুশীলনের রক্ষাকবচ পাওয়ার উপযোগী বলে বিবেচিত হয়। ইচ্ছাকৃতভাবে কীটপতঙ্গদের ক্ষতি করা জৈন ধর্মানুশীলনে নিষিদ্ধ। উদাহরণ স্বরূপ, কীটপতঙ্গ মারার বদলে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। জৈনধর্মে ঐচ্ছিকভাবে ক্ষতি করা ও নির্দয় হওয়াকে হিংসার চেয়েও গুরুতর অপরাধ মনে করা হয়। |
|||
{{Main|তত্ত্ব (জৈনধর্ম)}} |
|||
জৈন দর্শনে "তত্ত্ব" বলতে সত্যকে বোঝায়। এটিই মুক্তিলাভের প্রধান অবলম্বন। দিগম্বর জৈনদের মতে তত্ত্বের সংখ্যা সাত: চেতন ("জীব"), অচেতন ("অজীব"); আত্মার কর্ম-সংক্রান্ত অভ্যন্তরমুখী প্রবাহ ("[[আস্রব]]"); আত্মার কর্ম-সংক্রান্ত কণাগুলির বন্ধন ("[[বন্ধ (জৈনধর্ম)|বন্ধ]]");{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|pp=১৮৮–১৯০}}{{sfn|জৈনি|১৯৮০|pp=২১৯–২২৮}} কর্ম-সংক্রান্ত কণাগুলির গতিরোধ ("[[সম্বর]]"); অতীতের কর্ম-সংক্রান্ত কণাগুলির নির্মূলীকরণ ("[[নির্জরা]]") এবং মুক্তি ("[[মোক্ষ]]")। শ্বেতাম্বর জৈনরা এগুলির সঙ্গে আরও দু’টি তত্ত্বকে যোগ করেন। এগুলি হল: সৎকর্ম ("পুণ্য") ও অসৎকর্ম ("পাপ")।{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|pp=১৭৭–১৮৭}}{{sfn|জৈনি|১৯৯৮|p=১৫১}}{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=৯৬–৯৮}} জৈন দর্শনে "তত্ত্বসমূহে বিশ্বাস"-কেই প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টি মনে করা হয়।{{sfn|জৈনি|১৯৯৮|p=১৫১}} সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে জৈনধর্মের আধ্যাত্মিক লক্ষ্য হল মোক্ষে উত্তীর্ণ হওয়া। কিন্তু অধিকাংশ জৈন গৃহীর কাছে এই লক্ষ্যটি হল সৎকর্মের মাধ্যমে উৎকৃষ্টতর পুনর্জন্ম লাভ এবং মোক্ষের পথে এক ধাপ অগ্রসর হওয়া।{{sfn|বেইলি|২০১২|p=১০৮}}{{sfn|লং|২০১৩|pp=১৮, ৯৮–১০০}} |
|||
===আত্মা ও কর্ম=== |
|||
মানুষ, পশুপাখি ও কীটপতঙ্গের পর জৈনরা গাছপালার প্রতি অহিংসা ব্রত পালন করেন। যতটা না করলেই নয়, তার চেয়ে বেশি ক্ষতি তাঁরা গাছপালার করেন না। যদিও তাঁরা মনে করেন, খাদ্যের প্রয়োজনে গাছপালার ক্ষতি করতেই হয়। তবে মানুষের টিকে থাকার ক্ষেত্রে এটা অপরিহার্য বলে তাঁরা এতটুকু হিংসা অনুমোদন করেন। কট্টরপন্থী জৈনরা এবং জৈন সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীরা মূল-জাতীয় সবজি (যেমন আলু, পিঁয়াজ, রসুন) খান না। কারণ, কোনো গাছকে উপড়ে আনতে গেলে গাছের ছোটো ছোটো অঙ্গগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।<ref>{{harvnb|Sangave|1980|p=260}}</ref> |
|||
{{Main|জৈনধর্মে কর্ম}} |
|||
[[File:Jiva.jpg|thumb|জৈনধর্মে "সংসারী জীব"গণের (দেহান্তরগামী আত্না) শ্রেণিবিভাগ]] |
|||
জৈনরা বিশ্বাস করেন, "প্রাচুর্যপূর্ণ ও চির-পরিবর্তনশীল আত্মা"-র অস্তিত্ব একটি স্বতঃপ্রমাণিত সত্য এবং স্বতঃসিদ্ধ বলেই এই ধারণাটির প্রমাণের কোনও প্রয়োজন নেই।{{sfn|জৈনি|১৯৯৮|p=১০৩}} জৈন মতে, অসংখ্য আত্মার অস্তিত্ব রয়েছে; কিন্তু প্রতি আত্মারই তিনটি করে [[গুণ (ভারতীয় দর্শন)|গুণ]]: "চৈতন্য" (চেতনা; সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ গুণ এটি), "সুখ" (পরম সুখ) ও "বীর্য" (স্পন্দনশীল শক্তি)।{{sfn|জৈনি|১৯৯৮|pp=১০৪–১০৬}} তাঁরা আরও মনে করেন যে, এই বীর্যই কর্ম-সংক্রান্ত কণাগুলিকে আত্মার কাছে টেনে আনে এবং বন্ধন সৃষ্টি করে; আবার এই বীর্যই আত্মার উৎকর্ষ-সাধন করে অথবা আত্মাকে দোষযুক্ত করে।{{sfn|জৈনি|১৯৯৮|pp=১০৪–১০৬}} জৈন ধর্মগ্রন্থগুলিতে বলা হয়েছে যে, আত্মা "পার্থিব শরীরের দ্বারা আবৃত" হয়ে অস্তিত্বমান থাকে এবং আত্মাও সম্পূর্ণভাবে শরীরকে পরিপূর্ণ করে রাখে।{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|p=১৯৪}} অন্যান্য সকল ভারতীয় ধর্মের মতোই জৈনধর্মেও কর্মকে বিধানের বিশ্বজনীন কারণ ও কার্য মনে করা হয়। যদিও এই ধর্মে কর্মকে একটিকে পার্থিব বস্তু (সূক্ষ্ম পদার্থ) হিসেবেও দেখা হয়, যা আত্মাকে বদ্ধ করতে পারে, আত্মার সঙ্গে আবদ্ধ অবস্থায় জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে যাত্রা করতে পারে এবং লোকসমূহে জীবগণের দুঃখ ও সুখকে প্রভাবিত করতে পারে।{{sfn|লং|২০১৩|pp=৯২–৯৫}} কর্মকে অস্পষ্ট এবং আত্মার সহজাত প্রকৃতি ও সংগ্রামের বস্তু মনে করা হয়। সেই সঙ্গে এটিকে পরবর্তী জন্মের একটি আধ্যাত্মিক অনুদ্ভূত শক্তিও জ্ঞান করা হয়।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=৯৯–১০৩}} |
|||
===সংসার=== |
|||
জীবনের ধরন ও ও অদৃশ্য জীবন সহ জীবনের আকৃতি সম্পর্কে জৈনদের ধারণা অত্যন্ত বিস্তারিত। জৈন ধর্মমতে, হিংসার পিছনে উদ্দেশ্য ও আবেগগুলি কাজের থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, যদি কেউ অযত্নের বশে কোনো জীবিত প্রাণীকে হত্যা করে এবং পরে তার জন্য অনুতাপ করে তবে, কর্মবন্ধন কমে আসে। অন্যদিকে ক্রোধ, প্রতিশোধ ইত্যাদি আবেগের বশে হত্যা করা গুরুতর অপরাধ বলে বিবেচিত হয়। ‘ভাব’ অর্থাৎ আবেগগুলি কর্মবন্ধনের কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়। কোনো সৈন্য আত্মরক্ষার জন্য কাউকে হত্যা করছে এবং কেউ ঘৃণা বা প্রতিশোধের বশে কাউকে হত্যা করছে – এই দুই হিংসার ধরন সম্পূর্ণ আলাদা। |
|||
{{main|সংসার (জৈনধর্ম)|প্রাণবাদ (জৈনধর্ম)}} |
|||
সংসারের নির্মাণ-কাঠামো সম্পর্কে ধারণা বিষয়ে জৈনধর্ম ও অন্যান্য ভারতীয় ধর্মগুলির মধ্যে মতদ্বৈধ আছে। জৈনধর্মে আত্মা ("জীব") হিন্দুধর্মের ন্যায় সত্য হিসেবে স্বীকৃত হলেও বৌদ্ধধর্মের অনুরূপ বিবেচিত হয়নি। পুনর্জন্মের চক্রটিরও জৈনধর্মে একটি সুস্পষ্ট সূত্রপাত ও সমাপ্তি রয়েছে।{{Sfn|জৈনি|১৯৮০|p=২২৬}} জৈন থিওজফি অনুযায়ী, প্রত্যেক আত্মা চুরাশি লক্ষ জন্মাবস্থা পার হয় এই সংসারে আসে,{{Sfn|জৈনি|১৯৮০|p=২২৮}}{{sfn|জৈনি|২০০০|pp=১৩০–১৩১}} যাতে তারা পাঁচ ধরনের শরীরের মধ্যে দিয়ে যায়: স্থলচর শরীর, জলচর শরীর, অগ্নিময় শরীর, বায়ুচর শরীর ও উদ্ভিজ্জ শরীর, যা আবার বৃষ্টিপাত থেকে শ্বাসপ্রশ্বাস পর্যন্ত ক্রমাগত সকল মানব ও অ-মানবীয় ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হয়।{{Sfn|জৈনি|১৯৮০|pp=২২৩–২২৫}} জৈনধর্মে জীবনের কোনও রূপকেই আঘাত করা পাপ, তাতে নেতিবাচক কর্মের প্রভাব পড়ে বলে মনে করা হয়।{{Sfn|জৈনি|১৯৮০|pp=২২৪–২২৫}}{{sfn|শেঠিয়া|২০০৪|pp=৩০–৩১}} জৈনধর্ম মতে আত্মার সূচনা হয় এক আদ্যকালীন অবস্থায় এবং কর্মানুসারে হয় তা উচ্চতর অবস্থায় বিবর্তিত হয় অথবা নিম্নতর অবস্থায় ফিরে যায়।{{Sfn|জৈনি|১৯৮০|pp=২২৭–২২৮}} জৈনধর্ম আরও বলে যে, "অভব্য" (অক্ষম) আত্মারা কখনই [[মোক্ষ]] লাভ করতে পারে না।{{Sfn|জৈনি|১৯৮০|p=২২৬}}{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=১০৪–১০৫}} এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, কোনও ইচ্ছাকৃত ও জঘন্য অশুভ কর্মের পরে আত্মা "অভব্য" অবস্থায় প্রবেশ করে।{{Sfn|জৈনি|১৯৮০|p=২২৫}} হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শনের কোনও কোনও শাখার অদ্বৈত মতবাদের বিরুদ্ধে গিয়ে জৈনধর্ম বলে আত্মা ভালো বা মন্দ দুইই হতে পারে।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=১০৪–১০৫}} জৈনধর্ম মতে, একজন "সিদ্ধ" (মোক্ষপ্রাপ্ত আত্মা) সংসারের উর্ধ্বে চলে যান এবং তিনিই সর্বোচ্চ লোকে ("সিদ্ধশীল") সর্বজ্ঞ হয়ে চিরকাল সেখানেই বাস করেন।{{Sfn|জৈনি|১৯৮০|pp=২২২–২২৩}} |
|||
===বিশ্বতত্ত্ব=== |
|||
জৈনধর্মে আত্মরক্ষার জন্য হিংসা বা যুদ্ধ মেনে নেওয়া হয়। তবে শান্তিপূর্ণ সমাধানসূত্র না পাওয়া গেলে তবেই এগুলি প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হয়।<ref name="Dundas2002a">{{harvnb|Dundas|2002|pp=162–163}}</ref> |
|||
{{Main|জৈন বিশ্বতত্ত্ব}} |
|||
{{Multiple image |
|||
| image1 = Jain universe.JPG |
|||
| caption1 = জৈন বিশ্বতত্ত্বে পুনর্জন্মলোক{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=৯০–৯২}} |
|||
| width1 = 165 |
|||
| image2 = Jain Cosmic Time Cycle.jpg |
|||
| caption2 = জৈন বিশ্বতত্ত্বে সময়ের বিভাজন |
|||
| width2 = 159 |
|||
}} |
|||
জৈন ধর্মগ্রন্থগুলিতে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মাণ্ড অনেক চিরন্তন "লোক" (অস্তিত্বের জগৎ) দ্বারা গঠিত। হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মে কাল ও ব্রহ্মাণ্ডকে চিরন্তন মনে করা হয়, কিন্তু জৈনধর্মে ব্রহ্মাণ্ডকে মনে করা হয় ক্ষণস্থায়ী।{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|p=২৪১}}{{sfn|লং|২০১৩|pp=৮৩–৮৫}} ব্রহ্মাণ্ড, দেহ, বস্তু ও কালকে আত্মা অর্থাৎ জীবের থেকে পৃথক জ্ঞান করা হয়। জৈন দর্শনে এদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে জীবন, জীবনযাপন, মৃত্যু ও পুনর্জন্ম ব্যাখ্যাত হয়েছে।{{sfn|লং|২০১৩|pp=৮৩–৮৫}} জৈন ব্রহ্মাণ্ডের তিনটি লোক বিদ্যমান: উর্ধ্বলোক, মধ্যলোক ও অধোলোক।{{sfn|নাথুভাই শাহ|১৯৯৮|p=২৫}} জৈনধর্মে বলা হয় যে, কালের আদি নেই এবং তা চিরন্তন;{{sfn|ডনিগার|১৯৯৯|p=৫৫১}} "কালচক্র" অর্থাৎ কালের মহাজাগতিক চক্রটি অনিবার পাক খাচ্ছে। ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মাণ্ডের এই অংশে দুই "অর"-এর (অপরিমেয় কাল) মধ্যে ছয়টি পর্যায় রয়েছে এবং প্রথম অরে ব্রহ্মাণ্ড উৎপাদিত হয় এবং পরবর্তী অরে ব্রহ্মাণ্ড বিনষ্ট হয়।{{sfn|বিজয় কে. জৈন|২০১১|p=৪৬}} এইভাবেই এটি বিশ্বের কালচক্রকে দুই চক্রার্ধে বিভক্ত করে: "উৎসর্পিণী" (আরোহণকারী, ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধি ও আনন্দের সময়) ও "[[অবসর্পিণী]]" (অবরোহণকারী, ক্রমবর্ধমান দুঃখ ও পাপাচারের সময়)।{{sfn|ডনিগার|১৯৯৯|p=৫৫১}}{{sfn|উপিন্দর সিং|২০১৬|p=৩১৩}}{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|pp=২৭১–২৭২}} এখানে বলা হয়েছে যে বর্তমানে বিশ্ব অবসর্পিণীর পঞ্চম অরে অবস্থিত, যা দুঃখ ও ধর্মীয় অধঃপতনে পরিপূর্ণ এবং যেখানে জীবিত সত্ত্বাদের উচ্চতা হ্রাস পায়। জৈনধর্ম মতে ষষ্ঠ অরের পর ব্রহ্মাণ্ড এক নতুন চক্রে পুনঃজাগরিত হবে।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|p=১৩}}{{sfn|চম্পৎ রাই জৈন|১৯২৯বি|p=১২৪}}{{sfn|দালাল|২০১০এ|p=২৭}} |
|||
=== ঈশ্বর === |
|||
[[মহাত্মা গান্ধী]] ছিলেন [[অহিংসা]] আদর্শের অন্যতম বিশিষ্ট প্রচারক ও পালনকর্তা। |
|||
[[File:Jain 24-Tirthankaras.jpg|thumb|upright|চব্বিশ জন তীর্থংকরের জৈন অনুচিত্র, [[জয়পুর]], আনুমানিক ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দ]] |
|||
{{Main|জৈনধর্মে ঈশ্বর}} |
|||
জৈনধর্ম [[ঈশ্বর-নিরপেক্ষতাবাদ|ঈশ্বর-নিরপেক্ষতাবাদী]] ধর্ম।{{sfn|জিমার|১৯৫৩|p=১৮২}} জৈন বিশ্বাসে [[জৈনধর্ম ও অ-সৃষ্টিবাদ|ব্রহ্মাণ্ড অসৃষ্ট]] ও চিরবিরাজমান;{{sfn|ফন গ্লাসপেনাপ|১৯২৫|p=২৪১}} এই কারণেই তা স্বাধীন এবং তার কোনও স্রষ্টা, শাসক, বিচারক বা ধ্বংসকর্তা নেই।{{sfn|লং|২০১৩|pp=৮৩–৮৫}}{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|pp=২৪১–২৪২}} এই-জাতীয় মত [[হিন্দুধর্ম]] ও [[আব্রাহামীয় ধর্মসমূহ|আব্রাহামীয় ধর্মগুলির]] বিপরীত হলেও [[বৌদ্ধধর্ম|বৌদ্ধধর্মের]] অনুরূপ।{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|pp=২৪১–২৪৩}} অবশ্য জৈনরা দেবতা ও নারকীয় সত্ত্বাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। তাঁরা মনে করেন যে, এই দেবতা ও নারকীয় সত্ত্বারাও পার্থিব সত্ত্বাদের মতো জন্মগ্রহণ করেন, মারা যান এবং পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন।{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|pp=২৪৭–২৪৯, ২৬২–২৬৩}}{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=২০–২১, ৩৪–৩৫, ৭৪, ৯১, ৯৫–৯৬, ১০৩}} জৈন ধর্মগ্রন্থগুলিতে বলা হয়েছে যে, কোনও দেবতার শরীরে সানন্দে বাস করার সৌভাগ্য কোনও আত্মা লাভ করতে পারেন তাঁর ইতিবাচক কর্মের জন্য{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|pp=২৬২–২৬৩}} এবং তাঁরা ঐহিক বিষয়ে অধিকতর অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের অধিকারী হন এবং মানবজগতে কী ঘটতে চলেছে তা পূর্বেই বুঝতে পারেন।{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|pp=২৬২–২৬৩}} অবশ্য তাঁদের অতীতের কর্ম-সঞ্জাত গুণাবলি ব্যয়িত হলে এই আত্মারা কীভাবে আবার মানুষ, পশুপাখি বা অন্য সত্ত্বা রূপে জন্মগ্রহণ করেন, তার ব্যাখ্যাও জৈনদের ধর্মগ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়।{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|pp=২৬২–২৬৩}}{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=৯১, ৯৫–৯৬}} জৈনধর্মে স-শরীরী উৎকৃষ্টতম আত্মাকে বলা হয় '[[অরিহন্ত (জৈনধর্ম)|অরিহন্ত]]'' (বিজয়ী) ও শরীর-বিহীন উৎকৃষ্টতম আত্মাকে বলা হয় ''[[সিদ্ধ]]'' (মুক্ত আত্মা)।{{Sfn|জৈনি|১৯৮০|pp=২২২–২২৩}}{{sfn|র্যানকিন|মার্ডিয়া|২০১৩|p=৪০}}{{sfn|জিমার|১৯৫৩|p=১৮২}} |
|||
===জ্ঞানতত্ত্ব=== |
|||
===অনেকান্তবাদ=== |
|||
{{Main|জৈন জ্ঞানতত্ত্ব}} |
|||
{{মূল নিবন্ধ|অনেকান্তবাদ}} |
|||
জৈন দর্শনে তিনটি "[[প্রমাণ (ভারতীয় দর্শন)|প্রমাণ]]" (জ্ঞানের নির্ভরযোগ্য উপায়) স্বীকৃত। জৈন দর্শন মতে, জ্ঞানের ভিত্তি "প্রত্যক্ষ" (ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে উপলব্ধি), "অনুমান" ও "শব্দ" (শাস্ত্রবাক্য অর্থাৎ প্রামাণিক সাক্ষ্য)।{{sfn|গ্রিমস|১৯৯৬|p=২৩৮}}{{sfn|সোনি|২০০০|pp=৩৬৭–৩৭৭}} "তত্ত্বার্থসূত্র", "পর্বাচরণসার", "নান্দী" ও "অনুযোগদ্বারিণী" প্রভৃতি গ্রন্থে এই ধারণাগুলি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=৭৫–৭৬, ১৩১, ২২৯–২৩০}}{{sfn|সোনি|২০০০|pp=৩৬৭–৩৭৭}} কোনও কোনও জৈন ধর্মগ্রন্থে "উপমান"-কে (আংশিক সাদৃশ্য বর্ণনা) একটি চতুর্থ নির্ভরযোগ্য উপায় বলে উল্লেখ করা হয়েছে, ঠিক যেভাবে অন্যান্য ভারতীয় ধর্মে [[প্রমাণ (ভারতীয় দর্শন)|জ্ঞানতত্ত্ব-সংক্রান্ত মতগুলি]] পাওয়া যায় সেইভাবেই।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=২২৯–২৩০}} জৈনধর্মে বলা হয় "জ্ঞান" পাঁচ প্রকারের –"[[কেবলজ্ঞান]]" (সর্বজ্ঞতা), "শ্রুতজ্ঞান" (শাস্ত্রজ্ঞান), "মতিজ্ঞান" (ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান), "অবধিজ্ঞান" (অন্তর্দৃষ্টি-সংক্রান্ত জ্ঞান) ও "মনঃপ্রয়ায়জ্ঞান" (টেলিপ্যাথি)।{{sfn|এস. এ. জৈন|১৯৯২|p=১৬}} জৈন ধর্মগ্রন্থ "তত্ত্বার্থসূত্র" অনুযায়ী, প্রথম দু’টি অপ্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং অবশিষ্ট তিনটি প্রত্যক্ষ জ্ঞান।{{sfn|বিজয় কে. জৈন|২০১১|p=৬}} |
|||
জৈনধর্মের দ্বিতীয় প্রধান আদর্শ হল ‘[[অনেকান্তবাদ]]’। জৈনদের কাছে, ‘অনেকান্তবাদ’ হল মুক্তমনস্ক হওয়া। এর মধ্যে সকল মতাদর্শ গ্রহণ ও বিভিন্ন বিশ্বাসের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা এর অঙ্গ। জৈনধর্ম এই ধর্মের অনুরাগীদের বিপরীত ও বিরুদ্ধ মতবাদগুলিকে বিবেচনা করার শিক্ষা দেয়। জৈনদের অনেকান্তবাদ ধারণাটি মহাত্মা গান্ধীর ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও অহিংসার আদর্শকে অনুপ্রাণিত করেছিল।<ref name = "hay">{{harvnb|Sethia|2004|pp=166–167}}</ref> |
|||
===মোক্ষ=== |
|||
অনেকান্তবাদ [[বহুত্ববাদ (দর্শন)|বহুত্ববাদকে]] (একাধিক মতবাদের সহাবস্থান) বিশেষ গুরুত্ব দেয়। সেই সঙ্গে মনে করে সত্য ও বাস্তবতাকে বিভিন্ন ও বৈচিত্র্যপূর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা উচিত। কারণ একটি মাত্র দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে তা সম্পূর্ণ বিচার করা যায় না।<ref name="Dundas2002">{{harvnb|Sethia|2004|pp=123–136}}</ref><ref name="kollerjurno">{{harvnb|Sethia|2004|pages=400–407}}</ref> |
|||
{{Main|মোক্ষ (জৈনধর্ম)|রত্নত্রয়|গুণস্থান}} |
|||
[[File:MahaveeJi.jpg|thumb|একটি [[জৈন মন্দির|জৈন মন্দিরের]] তিনটি [[শিখর]] (চূড়া) রত্নত্রয়ের প্রতীক]] |
|||
জৈনধর্ম অনুযায়ী, আত্মার পরিশুদ্ধিকরণ এবং মোক্ষ লাভ করা সম্ভব তিন রত্নের পথ অবলম্বন করে:{{sfn|বিজয় কে. জৈন|২০১১|p=৬}}{{sfn|কর্ট|২০০১এ|pp=৬–৭}}{{sfn|ফোর|২০১৫|pp=৯–১০, ৩৭}} "সম্যক দর্শন" (সঠিক দৃষ্টিকোণ; অর্থাৎ জীব বা আত্মার সত্যে বিশ্বাস ও গ্রহণ);{{sfn|জৈনি|১৯৯৮|pp=১৪১–১৪৭}} "সম্যক জ্ঞান" (সঠিক জ্ঞান, অর্থাৎ তত্ত্বসমূহের সংশয়হীন জ্ঞান);{{sfn|জৈনি|১৯৯৮|pp=১৪৮, ২০০}} ও "সম্যক চরিত্র" (সঠিক আচরণ, অর্থাৎ পঞ্চপ্রতিজ্ঞার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ আচরণ)।{{sfn|জৈনি|১৯৯৮|pp=১৪৮, ২০০}} জৈন ধর্মগ্রন্থগুলিতে [[মোক্ষ|মোক্ষের]] সহায়ক সন্ন্যাসপ্রথার উপর গুরুত্ব আরোপ করার জন্য একটি চতুর্থ রত্ন হিসেবে প্রায়শই "সম্যক তপ" (সঠিক তপস্যা) যোগ করে থাকে।{{sfn|কর্ট|২০০১এ|p=৭}} এই চার রত্নকে বলা হয় "মোক্ষমার্গ" (মোক্ষের পথ)।{{sfn|কর্ট|২০০১এ|pp=৬–৭}} |
|||
==প্রধান নীতিসমূহ== |
|||
এই তত্ত্বটিকে জৈনরা [[অন্ধের হস্তীদর্শন]] উপাখ্যানের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন। এই গল্পে এক এক জন অন্ধ এক হাতির এক একটি অঙ্গ স্পর্শ করেছিল। কেউ শুঁড়, কেউ পা, কেউ কান বা কেউ অন্য কিছু ধরেছিল। প্রত্যকে হাতির যে অঙ্গটি ধরেছিল, হাতি সেই রকম পশু বলে দাবি করে। হাতিটিকে সম্পূর্ণভাবে স্পর্শ না করতে পেরে তাদের জ্ঞানও সম্পূর্ণ হয় না।<ref name="hughes">{{harvnb|Sethia|2004|p=115}}</ref> অনেকান্তবাদের ধারণাটি পরে প্রসারিত হয় এবং স্যাদবাদ কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়। |
|||
===অহিংসা=== |
|||
{{anchor|অহিংসা}}{{Main|জৈনধর্মে অহিংসা}} |
|||
[[File:Ahinsa Parmo Dharm 1.jpg|thumb|[[জৈনধর্মে অহিংসা|অহিংসার]] প্রতীকী খোদাইচিত্র]] |
|||
জৈনধর্মে [[জৈনধর্মে অহিংসা|অহিংসা]] একটি মৌলিক মতবাদ।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|p=১৬০}} জৈন মতে, ব্যক্তিকে সকল সহিংস ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করতে হবে এবং অহিংসার প্রতি এমন এক অঙ্গীকার না করলে সকল ধর্মাচরণই বৃথা যাবে।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|p=১৬০}} জৈন ধর্মতত্ত্ব অনুযায়ী, হিংসা যতই সঠিক বা আত্মরক্ষামূলক হোক না কেন, ব্যক্তির উচিত কোনও সত্ত্বাকে হত্যা বা কোনও সত্ত্বার কোনও প্রকার ক্ষতি না করা। অহিংসা এই ধর্মে এমনই এক ধর্মীয় কর্তব্য।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|p=১৬০}}{{sfn|মারখাম|লোর|২০০৯|p=৭১}} "[[আচারাঙ্গসূত্র]]" ও "[[তত্ত্বার্থসূত্র]]" প্রভৃতি জৈন ধর্মগ্রন্থে বলা হয়েছে যে ব্যক্তিকে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ, স্থাণু বা সচল সকল প্রকার জীবিত সত্ত্বার হত্যা থেকে বিরত থাকতে হবে।{{sfn|প্রাইস|২০১০|p=৯০}}{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=১৬০–১৬২}} জৈন ধর্মতত্ত্ব এই শিক্ষা দেয় যে, কেউই অপর কোনও জীবিত সত্ত্বাকে হত্যা করবে না, অপরকে হত্যার নিমিত্তও হতে দেবে না, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনও হত্যায় সম্মতিও প্রদান করবে না।{{sfn|প্রাইস|২০১০|p=৯০}}{{sfn|মারখাম|লোর|২০০৯|p=৭১}} অধিকন্তু জৈনধর্ম শুধুমাত্র কর্মের মাধ্যমেই নয়, বরং বাক্য ও চিন্তার মধ্য দিয়েও সকল জীবের প্রতি অহিংসা নীতি গ্রহণের পক্ষপাতী।{{sfn|প্রাইস|২০১০|p=৯০}}{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=১৬০–১৬২}} এই ধর্ম এই শিক্ষা দেয় যে, কাউকে ঘৃণা করা বা কারও প্রতি সহিংস আচরণের পরিবর্তে "সকল জীবিত সত্ত্বার উচিত পরস্পরকে সাহায্য করা।"।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=১৬০–১৬২}}{{efn|সকল জৈন উপসম্প্রদায় অবশ্য এই বিষয়ে একমত নয়। উদাহরণস্বরূপ, প্রায় আড়াই লক্ষ অনুগামীর তেরাপন্থি জৈন পরম্পরা মনে করে দয়ার্দ্র চিত্তে দানের ন্যায় সৎকর্ম এবং পাপের মতো দুষ্কর্ম উভয়েই ব্যক্তির আত্মাকে জাগতিক নৈতিকতার বন্ধনে আবদ্ধ করে। এই পরম্পরায় মনে করায় মানুষের সীমাবদ্ধ দৃষ্টিকোণ থেকে যে কোনও কর্মই "চরম অহিংসতা"-র এক অপলাপে পৌঁছে দেয়। এই পন্থায় তাই সাধু ও সাধ্বীদের যে কোনও সত্ত্বাকে আঘাত করা থেকে প্রতিহত থেকে ও তাদের সাহায্য করে মোক্ষ অনুসন্ধান করতে বলে।{{sfn|ফ্লুগেল|২০০২|pp=১২৬৬–১২৬৭}}}} জৈনরা বিশ্বাস করেন যে, ব্যক্তির আত্মায় হিংসার এক নেতিবাচক প্রভাব পড়ে এবং হিংসা আত্মাকে ধ্বংসও করে দেয়, বিশেষত যখন হিংসা ইচ্ছাকৃতভাবে, ঘৃণা বা অযত্নের কারণে জন্ম নেয় অথবা যখন একজন পরোক্ষভাবে কোনও মানুষ বা মানবেতর জীবিত সত্ত্বাকে হত্যার কারণ হয় বা তাকে হত্যায় সম্মতি দেয়।{{sfn|Dundas|2002|pp=160–162}} |
|||
অহিংসার মতবাদটি হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মেও আছে, কিন্তু এটির সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটেছিল জৈনধর্মে।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|p=১৬০}}{{sfn|সুন্দররাজন|মুখোপাধ্যায়|১৯৯৭|pp=৩৯২–৪১৭}}{{sfn|ইজাওয়া|২০০৮|pp=৭৮–৮১}}{{sfn|শেঠিয়া|২০০৪|p=২}}{{sfn|উইন্টারনিৎজ|১৯৯৩|p=৪০৯}} কোনও কোনও জৈন পণ্ডিতের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, সর্বোচ্চ ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে অহিংসার ধর্মতাত্ত্বিক এই ভিত্তিটি অন্য জীবের প্রতি দান বা দয়াপ্রদর্শনের গুণ থেকে বা সকল জীবকে উদ্ধার করার একটি কর্তব্যবোধ থেকে উৎসারিত হয়নি, বরং এটি হয়েছে একটি অবিরাম আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ফল হিসেবে। এর ফলে আত্মা শুদ্ধ হয় এবং তা থেকে ব্যক্তির নিজস্ব আধ্যাত্মিক বিকাশ সুসম্পন্ন হয়, যা শেষ পর্যন্ত ব্যক্তির মোক্ষলাভের পথ উন্মুক্ত করে দেয় এবং তাকে পুনর্জন্মের চক্র থেকে মুক্ত করে।{{sfn|Dundas|2002|pp=88–89, 257–258}} জৈনরা বিশ্বাস করেন যে, কোনও সত্ত্বাকে আঘাত করলে [[জৈনধর্মে কর্ম|অসৎকর্মের]] উদ্ভব ঘটে, যা ব্যক্তির পুনর্জন্মের কারণ হয় এবং ভবিষতে তার ভালো থাকাকে বিঘ্নিত করে দুঃখেরও উৎপত্তি ঘটায়।{{sfn|টেলর|২০০৮|pp=৮৯২–৮৯৪}}{{sfn|গ্র্যানফ|১৯৯২}} |
|||
===অপরিগ্রহ=== |
|||
{{মূল নিবন্ধ|অপরিগ্রহ}} |
|||
[[অপরিগ্রহ]] হল জৈনধর্মের তৃতীয় প্রধান আদর্শ। ‘অপরিগ্রহ’ বলতে নির্লোভ হওয়া, অপরের দ্রব্য না নেওয়া ও জাগতিক কামনাবাসনা থেকে দূরে থাকাকে বোঝায়। জৈনরা যতটুকু প্রয়োজনীয়, তার চেয়ে বেশি নেওয়ার পক্ষপাতী নন। দ্রব্যের মালিকানা স্বীকৃত। তবে দ্রব্যের প্রতি আসক্তিশূন্যতা শিক্ষা দেওয়া হয়। জৈন ধর্মাবলম্বীরা অপ্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ ও যা আছে তার প্রতি আসক্তিশূন্য হবে – এই হল জৈনধর্মের শিক্ষা। জৈনধর্ম মনে করে তা না করলে দ্রব্যের প্রতি অধিক আসক্তির বশে ব্যক্তি নিজের ও অপরের ক্ষতিসাধন করতে পারেন। |
|||
===পঞ্চ মহাব্রত=== |
|||
{{আরও দেখুন|যম (হিন্দু দর্শন)#পঞ্চ যম}} |
|||
ব্রতের মাধ্যমে আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং তার মাধ্যমে ব্যক্তিগত চৈতন্যের বিকাশের দ্বারা আধ্যাত্মিক জাগরণের উপর জৈনধর্ম বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে।<ref name="Buswell2004">{{harvnb|Glasenapp|1999|pp=228–231}}</ref> কট্টরপন্থী অনুগামী ও সাধারণ অনুগামীদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্তরের ব্রতের বিধান এই ধর্মে দেওয়া হয়।<ref name="Buswell2004"/> এই ধর্মের অনুগামীরা পাঁচটি প্রধান ব্রত পালন করেন: |
|||
#[[জৈনধর্মে অহিংসা|অহিংসা]]: প্রথম ব্রতটি হল জৈন ধর্মাবলম্বী কোনো জীবিত প্রাণীর ক্ষতি করবে না। এর মধ্যে অন্যান্য প্রাণীর প্রতি কার্য, বাক্য বা চিন্তার মাধ্যমে ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক ক্ষতিসাধনের শ্রেণীবিভাগ করা আছে। |
|||
#[[সত্য]]: এই ব্রতটি হল সর্বদা সত্য কথা বলার ব্রত। অহিংসাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। তাই অন্যান্য আদর্শের সঙ্গে অহিংসার আদর্শের কোনো বিরোধ বাধলে, এই ব্রতের সাহায্য নেওয়া হয়। যেখানে সত্য বচন হিংসার কারণ হয়, সেখানে মৌন অবলম্বন করা হয়।<ref name="Buswell2004" /> |
|||
#[[অস্তেয়]]: ‘অস্তেয়’ শব্দের অর্থ চুরি না করা। যা ইচ্ছাক্রমে দেওয়া হয়নি, জৈনরা তা গ্রহণ করেন না।<ref name="Buswell2004"/> অন্যের থেকে ধনসম্পত্তি নিয়ে নেওয়া বা দুর্বলকে দুর্বলতর করাকে জৈনরা চুরি করা বলেন। তাই যা কিছু কেনা হয় বা যে পরিষেবা নেওয়া হয়, তার জন্য যথাযথ মূল্য দেওয়াই জৈনধর্মের নিয়ম। |
|||
#[[ব্রহ্মচর্য]]: গৃহস্থদের কাছে ব্রহ্মচর্য হল পবিত্রতা এবং সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের কাছে যৌনতা থেকে দূরে থাকা। যৌন ক্রিয়াকলাপ থেকে দূরে থেকে আত্মসংযমকেই ‘ব্রহ্মচর্য’ বলা হয়।<ref>{{সাময়িকী উদ্ধৃতি |লেখক=Mahajan PT, Pimple P, Palsetia D, Dave N, De Sousa A |শিরোনাম=Indian religious concepts on sexuality and marriage |সাময়িকী=Indian J Psychiatry |খণ্ড=55 |সংখ্যা নং=Suppl 2 |পাতাসমূহ=S256–62 | তারিখ=January 2013 |pmid=23858264 |pmc=3705692 |ডিওআই=10.4103/0019-5545.105547 |ইউআরএল=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3705692/|শেষাংশ২=Pimple |শেষাংশ৩=Palsetia |শেষাংশ৪=Dave |শেষাংশ৫=De Sousa }}</ref> |
|||
#[[অপরিগ্রহ]]: অপরিগ্রহ হল অনাসক্তি। এর মাধ্যমে জাগতিক বন্ধন থেকে দূরে থাকা এবং দ্রব্য, স্থান বা ব্যক্তির প্রতি অনাসক্তিকে বোঝায়।<ref name="Buswell2004"/> জৈন সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীরা সম্পত্তি ও সামাজিক সম্পর্ক সম্পূর্ণ ত্যাগ করেন। |
|||
পরবর্তীকালীন মধ্যযুগীয় জৈন পণ্ডিতেরা বহিঃশত্রুর ভীতিপ্রদর্শন বা হিংসার সম্মুখীন হয়ে অহিংসার নীতিটি পুনঃসমীক্ষা করে দেখেন। উদাহরণস্বরূপ, সাধ্বীদের রক্ষা করার জন্য সাধুদের সহিংস আচরণের তাঁরা যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেছিলেন।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=১৬২–১৬৩}}{{sfn|লোরেনজেন|১৯৭৮|pp=৬১–৭৫}} [[পল ডুন্ডাস|পল ডুন্ডাসের]] মতে, জৈন পণ্ডিত [[জিনদত্তসুরি]] মুসলমানদের দ্বারা মন্দির ধ্বংস ও জৈন নিপীড়নের সময়ই লিখেছিলেন যে, "ধর্মকর্মে আত্মনিয়োগকারী এমন কোনও ব্যক্তিকে যদি যুদ্ধ করতে বা হত্যা করতে বাধ্য করা হয়, তবে তিনি আধ্যাত্মিক গুণাবলির কিছুই হারাবেন না, বরং মুক্তিলাভ করবেন"।{{sfn|Dundas|2002|p=163}}<ref>মূল উদ্ধৃতি: "anybody engaged in a religious activity who was forced to fight and kill somebody would not lose any spiritual merit but instead attain deliverance"</ref> যদিও জৈন ধর্মগ্রন্থগুলিকে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে যুদ্ধ ও হত্যা ক্ষমা করার উদাহরণ অপেক্ষাকৃত হারে দুর্লভ।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=১৬২–১৬৩}}{{efn|বৌদ্ধ ও হিন্দুসাহিত্যের মতো জৈনসাহিত্যেও খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে হিংসা ও অহিংসার দিকগুলি নিয়ে দ্বিমত রয়েছে।{{sfn|ওলসন|২০১৪|pp=১–৭}}}} |
|||
সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের পাঁচটি মহাব্রত পালন করতে হয়। অন্যদিকে গৃহস্থ জৈনদের এই পঞ্চ মহাব্রত এগুলির ব্যবহারিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে যথাসম্ভব পালনের পরামর্শ দেওয়া হয়।<ref name="Buswell2004" /> |
|||
===অনেকান্তবাদ (বহুমুখী সত্য)=== |
|||
এছাড়াও জৈনধর্মে মনের চারটি আবেগকে চিহ্নিত করা হয়: ক্রোধ, অহং, অসদাচরণ ও লোভ। জৈন ধর্মমতে, ক্ষমার মাধ্যমে ক্রোধকে, বিনয়ের মাধ্যমে অহংকারকে, সত্যাচরণের মাধ্যমে অসদাচরণকে এবং সন্তুষ্টির মাধ্যমে লোভকে জয় করার কথা বলা হয়েছে। |
|||
{{Main|অনেকান্তবাদ}} |
|||
[[File:Medieval Jain temple Anekantavada doctrine artwork.jpg|thumb|[[অন্ধ ব্যক্তিগণ ও এক হস্তী|অন্ধ ব্যক্তিগণ ও এক হস্তীর]] চিত্রের মাধ্যমে জৈন মন্দিরে অনেকান্তবাদ ধারণাটির ব্যাখ্যা।]] |
|||
জৈনধর্মের দ্বিতীয় প্রধান নীতিটি হল "অনেকান্তবাদ"।।{{sfn|চরিত্রপ্রজ্ঞ|২০০৪|pp=৭৫–৭৯}}{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=২২৯–২৩১}} শব্দটি এসেছে "অনেকান্ত" অর্থাৎ "বহুমুখী" এবং "বাদ" অর্থাৎ "মতবাদ শব্দ দু’টির মিলনে।{{sfn|চরিত্রপ্রজ্ঞ|২০০৪|pp=৭৫–৭৯}}{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=২২৯–২৩১}} এই মতবাদ অনুযায়ী, সত্য ও বাস্তবতা জটিল এবং সবসময়ই তার বহু-অংশবিশিষ্ট দিক থাকে। এই মতবাদে আরও বলা হয়েছে যে, বাস্তবতার অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায়, কিন্তু তা ভাষা দ্বারা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করা যায় না। অনেকান্তবাদ বলে, মানুষের পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগের প্রয়াসটি আসলে "নয়" অর্থাৎ "সত্যের আংশিক প্রকাশ"।{{sfn|চরিত্রপ্রজ্ঞ|২০০৪|pp=৭৫–৭৯}} বলা হয় যে, মানুষ সত্যের অভিজ্ঞতার আস্বাদ পেতে পারে, কিন্তু তা সম্পূর্ণভাবে ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারে না। অনেকান্তবাদ মতে, অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করার প্রয়াসগুলি হল "স্যাৎ" বা "কিয়দংশে" বৈধ, কিন্তু তা "সম্ভবত, শুধুমাত্র একটি দৃষ্টিকোণ থেকে অসম্পূর্ণ" রয়েই যায়।<ref name=iepmahav>[http://www.iep.utm.edu/jain/ জৈন ফিলোজফি] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20150221042158/http://www.iep.utm.edu/jain/ |date=21 February 2015 }}, আইইপি, মার্ক ওয়েন ওয়েব, টেক্সাস টেক বিশ্ববিদ্যালয়</ref> অনেকান্তবাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এক অর্থে আধ্যাত্মিক সত্যগুলির অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায়, কিন্তু তা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করা যায় না।{{sfn|চরিত্রপ্রজ্ঞ|২০০৪|pp=৭৫–৭৯}} এই মতে, "একান্ত"-এ (একমুখিতা) বিশ্বাস এক মহাভ্রান্তি; কারণ সেখানে কিছু কিছু আপেক্ষিক সত্যকে পরম সত্য জ্ঞান করা হয়।{{sfn|সোয়ার্ৎজ|২০১৮}} এই মতবাদটি প্রাচীন। "সামান্নফল সুত্ত"-এর মতো বৌদ্ধ গ্রন্থেও এই মতবাদ পাওয়া যায়। জৈন আগমগুলিতে বলা হয়েছে, সকল প্রকার অধিবিদ্যামূলক প্রশ্নের উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে মহাবীরের উত্তরটি ছিল এক "সীমিত স্তরে হ্যাঁ" ("স্যাৎ")।{{sfn|মতিলাল|১৯৯০|pp=৩০১–৩০৫}}{{sfn|বালসারোউইকজ|২০১৫|pp=২০৫–২১৮}} এই গ্রন্থগুলি অনেকান্তবাদকে [[গৌতম বুদ্ধ|বুদ্ধের]] শিক্ষা থেকে একটি প্রধান পার্থক্য হিসেবে চিহ্নিত করে। বুদ্ধ মধ্যপন্থা শিক্ষা দিয়েছিলেন; অধিবিদ্যামূলক প্রশ্নের ক্ষেত্রে তিনি "হ্যাঁ, এটাই" বা "না, এটা নয়" এই জাতীয় চরম উত্তর দিতেন। অপরপক্ষে মহাবীর তাঁর অনুগামীদের পরম বাস্তবতাকে বুঝতে "সম্ভবত" কথাটি যুক্ত করে "হ্যাঁ, এটা" ও "না, এটা নয়" দুইই গ্রহণের শিক্ষা দিয়েছিলেন।{{sfn|মতিলাল|১৯৯৮|pp=১২৮–১৩৫}} জৈনধর্মে এক দ্বৈতবাদী অনেকান্তবাদের নির্মাণ-কাঠামোর মধ্যে স্থায়ী সত্ত্বাকে "[[জীব (জৈনধর্ম)|জীব]]" (আত্মা) ও "[[অজীব]]" (বস্তু) হিসেবে ধারণা করা হয়।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=৯০–৯৯, ১০৪–১০৫, ২২৯–২৩৩}} |
|||
পল ডুন্ডাসের মতে, সমসাময়িক কালে অনেকান্তবাদ ধারণাটিকে কোনও কোনও জৈন "বিশ্বজনীন ধর্মীয় সহিষ্ণুতার প্রচার", "বহুত্ব"-এর এক শিক্ষা এবং "অন্যান্য [নৈতিক, ধর্মীয়] মতবাদের প্রতি সহৃদয় আচরণ" হিসেবে দেখেন। ডুন্ডাস বলেছেন যে, এটি ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলি ও মহাবীরের উপদেশাবলির ভ্রান্ত ব্যাখ্যা।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=২৩২–২৩৪}} তাঁর মতে, মহাবীরের শিক্ষায় "বহুমুখিতা, বহুমুখী দৃষ্টিকোণ" হল [[পরম (দর্শন)|পরম সত্য]] ও মানব অস্তিত্ব বিষয়ক।{{sfn|শেঠিয়া|২০০৪|pp=৮৬–৯১}} তিনি দাবি করেন যে, খাদ্যের জন্য প্রাণীহত্যা, অবিশ্বাসী বা অন্য কোনও জীবিত সত্ত্বার বিরুদ্ধে হিংসাকে অনেকান্তবাদ মতে "সম্ভবত ঠিক" বলা হয়নি।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=২৩২–২৩৪}} উদাহরণস্বরূপ, জৈন সাধু ও সাধ্বীদের পঞ্চ মহাব্রত প্রসঙ্গে কঠোর নিয়ম রয়েছে এবং সেগুলির সম্পর্কেও কোনও "সম্ভবত" কথাটি খাটে না।{{sfn|লং|২০০৯|pp=৯৮–১০৬}} ডুন্ডাস আরও বলেছেন যে, একইভাবে প্রাচীনকাল থেকেই জৈনধর্ম বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্মের সঙ্গে সহাবস্থান করে আসছে; এই সকল ধর্মের জ্ঞানতত্ত্ব ও ধর্মবিশ্বাসের কিছু কিছু ক্ষেত্রে জৈনধর্মের সঙ্গে এগুলির মতভেদ আছে; ঠিক যেমন ওই দুই ধর্মও জৈনধর্মের সকল মতকে গ্রহণ করে না।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|p=২৩৩}} |
|||
==ঈশ্বর== |
|||
{{মূল নিবন্ধ|জৈনধর্মে ঈশ্বর}} |
|||
[[File:Photo of lord adinath bhagwan at kundalpur.JPG|thumb|প্রথম [[তীর্থঙ্কর]] [[ঋষভ (জৈন তীর্থঙ্কর)|ঋষভের]] মূর্তি। ইনি জৈন কালচক্রের অবসরপনি যুগে বর্তমান ছিলেন বলে জৈনদের ধারণা।]] |
|||
জৈনধর্ম কোনো সৃষ্টিকর্তা বা ধ্বংসকর্তা ঈশ্বরের ধারণা গ্রহণ করে না। এই ধর্মমতে জগৎ নিত্য। জৈনধর্ম মনে করে, প্রত্যেক আত্মার মধ্যেই [[মোক্ষ]]লাভ ও [[ঈশ্বর]] হওয়ার উপযুক্ত উপাদান রয়েছে। এই ধর্মমতে পূর্ণাত্মা দেহধারীদের বলা হয় ‘[[অরিহন্ত (জৈনধর্ম)|অরিহন্ত]]’ (বিজয়ী) এবং দেহহীন পূর্ণাত্মাদের বলা হয় [[সিদ্ধ]] (মুক্তাত্মা)। যে সকল অরিহন্ত অন্যদের মোক্ষলাভে সাহায্য করেন তাঁদের বলা হয় ‘[[তীর্থঙ্কর]]’। জৈনধর্মে [[উত্তর-অস্তিবাদ|উত্তর-অস্তিবাদী]] ধর্মমত মনে করা হয়।{{sfn|Zimmer|1952|p=182}} কারণ, এই ধর্ম মোক্ষলাভের জন্য কোনো সর্বোচ্চ সত্তার উপর নির্ভর করার কথা বলে না। তীর্থঙ্করেরা হলেন সহায় ও শিক্ষক, যিনি মোক্ষলাভের পথে সাহায্য করেন মাত্র। কিন্তু মোক্ষলাভের জন্য সংগ্রাম মোক্ষলাভে ইচ্ছুক ব্যক্তিকেই করতে হয়। |
|||
===অপরিগ্রহ (অনাসক্তি)=== |
|||
*''অরিহন্ত'' (''জিন''): একজন মানুষ যিনি সব ধ্রনের আন্তরিক আবেগকে জয় করেছেন এবং [[কেবল জ্ঞান]] লাভ করেছেন। এঁদের ‘কেবলী’ও (সর্বজ্ঞ সত্ত্বা) বলা হয়। দুই ধরনের অরিহন্ত হন:{{sfn|Sangave|2006|p = 16}} |
|||
{{anchor|অপরিগ্রহ}}{{Main|অপরিগ্রহ}} |
|||
#''সামান্য'' (সাধারণ বিজয়ী) – যে কেবলীরা শুধুমাত্র নিজের মোক্ষের কথাই ভাবেন। |
|||
জৈনধর্মের তৃতীয় প্রধান নীতিটি হল "অপরিগ্রহ", অর্থাৎ কোনও জাগতিক বস্তুর প্রতি অনাসক্তি।{{sfn|নাথুভাই শাহ|২০০৪|p=১১২}} জৈনধর্মে সাধু ও সাধ্বীদের ক্ষেত্রে কোনও সম্পত্তি, সম্পর্ক ও আবেগের প্রতি সম্পূর্ণ অনাসক্তির প্রয়োজন হয়।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=১১৭, ১৫২}} দিগম্বর সম্প্রদায়ে সাধু-সাধ্বীরা পরিযায়ী এবং শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ে তাঁরা এক স্থানে বাস করেন।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=১১৭, ১৫২}} জৈন গৃহস্থদের ক্ষেত্রে সৎভাবে উপার্জিত স্বল্প সম্পত্তি রক্ষণেরই উপদেশ দেওয়া হয় এবং অতিরিক্ত সম্পত্তি দান করে দিতে বলা হয়।{{sfn|নাথুভাই শাহ|২০০৪|p=১১২}} নাথুভাই শাহের মতে, অপরিগ্রহ নীতিটি পার্থিব ও মানসিক উভয়ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। পার্থিব সম্পদ বলতে বিভিন্ন ধরনের সম্পত্তিকে বোঝায়। মানসিক সম্পত্তি বলতে বোঝায় আবেগ, পছন্দ ও পছন্দ এবং কোনও ধরনের আসক্তিকে। কথিত হয় যে, সম্পদের প্রতি অপরীক্ষিত আসক্তি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতি করে।{{sfn|নাথুভাই শাহ|২০০৪|pp=১১২–১১৩}} |
|||
#''[[তীর্থঙ্কর]]'' – ‘তীর্থঙ্কর’ শব্দের অর্থ যিনি পার করেন বা মোক্ষ শিক্ষার এক গুরু।{{sfn|Balcerowicz|2009|p = 16}} তাঁর জৈন ধর্মমত প্রচার ও পুনরুজ্জীবিত করেন। এঁরাই আধ্যাত্মিক জীবনের আদর্শ। তাঁরা ‘চতুর্বিধ সংঘ’ (শ্রমণ বা সন্ন্যাসী, শ্রমণী বা সন্ন্যাসিনী, শ্রাবক বা পুরুষ অনুগামী ও শ্রাবৈকা বা নারী অনুগামী) পুনর্গঠন করেন।{{sfn|Balcerowicz|2009|p = 17}}<ref>{{harvnb|Shah|1998a|pp=2–3}}</ref> জৈনরা বিশ্বাস করেন [[জৈন বিশ্বতত্ত্ব|জৈন কালচক্রের]] প্রত্যেক অর্ধে ২৪ জন করে তীর্থঙ্কর জন্মগ্রহণ করেন। সর্বশেষ তীর্থঙ্করের নাম [[মহাবীর]]। তাঁর পূর্ববর্তী তীর্থঙ্কর [[পার্শ্বনাথ]] ও মহাবীর – এই দুই তীর্থঙ্করের অস্তিত্বই ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত।<ref>{{harvnb|Shah|1998a|pp=21–28}}</ref> {{sfn|Zimmer|1952|p = 182-183}} |
|||
===জৈন নীতিবিদ্যা ও পঞ্চ-মহাব্রত=== |
|||
*''সিদ্ধ'': সিদ্ধ ও অরিহন্তরা [[মোক্ষ (জৈনধর্ম)|মোক্ষ]] অর্জন করে অনন্ত আনন্দ, অনন্ত অন্তর্দৃষ্টি, অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত শক্তি সহকারে [[সিদ্ধশীল|সিদ্ধশীলে]] বসবাস করেন। |
|||
{{Main|জৈনধর্মের নীতিবিদ্যা}} |
|||
{{see also|যম (দর্শন)#পঞ্চ যম}} |
|||
[[File:Nishidhi stone with 14th century Old Kannada inscription from Tavanandi forest.JPG|thumb|upright|[[ডোড্ডাহুন্ডি নিশিধি শিলালিপি]], সল্লেখনা প্রতিজ্ঞার চিত্র সহ, চতুর্দশ শতাব্দী, [[কর্ণাটক]]]] |
|||
জৈনধর্ম পাঁচটি নৈতিক কর্তব্য শিক্ষা দেয়, যেগুলিকে এই ধর্মে বলা হয় পঞ্চপ্রতিজ্ঞা। গৃহস্থ জৈনরা এগুলিকে বলেন "অনুব্রত" এবং জৈন সাধু-সাধ্বীরা এগুলিকে বলেন "মহাব্রত"।{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|pp=২২৮–২৩১}} উভয়ের ক্ষেত্রেই এই ধর্মের নৈতিক অনুশাসনের প্রস্তাব করে যে, জৈনরা এক [[গুরু]], দেব (জিন), মতবাদের সঙ্গে পরিচিত হবেন এবং সেই ব্যক্তিকে পাঁচ অপরাধ হতে মুক্ত হতে হবে: ধর্ম সম্পর্কে সংশয়, জৈনধর্মের সত্য সম্পর্কে অস্পষ্টতা, জৈন শিক্ষা সম্পর্কে আন্তরিক আকাঙ্ক্ষাহীনতা, সহধর্মী জৈনদের স্বীকৃতি প্রদান করা থেকে বিরত থাকা এবং তাঁদের আধ্যাত্মিক অনুশীলনের প্রশংসা না করা।{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|p=২২৮}} এই কারণে জৈনরা পাঁচটি ব্রত বা প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন: |
|||
# "[[অহিংসা]]", ("ইচ্ছাকৃতভাবে হিংসা থেকে বিরত থাকা" বা "কাউকে আঘাত না করা"):{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|p=২২৮}} জৈনরা প্রথমেই যে প্রধান ব্রত বা প্রতিজ্ঞাটি পালন করেন সেটি হল অপর কোনও মানুষ এবং সেই সঙ্গে সকল জীবিত সত্ত্বার (নির্দিষ্টভাবে পশুপাখিদের) ক্ষতি না করা।{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|p=২২৮}} এটিই জৈনধর্মের সর্বোচ্চ নৈতিক কর্তব্য। এটি যে শুধু ব্যক্তির কার্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল, তা-ই নয়, বরং বাক্য ও চিন্তাভাবনার মধ্যেও অহিংসতাকে স্থান দেওয়ার কথা উপদেশ দিত।<ref name=pkshah5v>{{citation |last=শাহ |first=প্রবীণ কে. |title=ফাইভ গ্রেট ভওজ (মহা-ব্রতজ) অফ জৈনিজম |url=http://www.fas.harvard.edu/~pluralsm/affiliates/jainism/jainedu/5greatvows.htm |publisher=হার্বার্ড ইউনিভার্সিটি লিটারেচার সেন্টার |date=2011 |access-date=7 May 2017 |archive-url=https://web.archive.org/web/20141231033127/http://www.fas.harvard.edu/~pluralsm/affiliates/jainism/jainedu/5greatvows.htm |archive-date=31 December 2014 |url-status=live |df=dmy-all }}</ref>{{sfn|বিজয় কে. জৈন|২০১২|p=৩৩}} |
|||
# "[[সত্য]]" ("সত্যবাদিতা"): এই ব্রতটি হল সর্বদা সত্য কথা বলার। মিথ্যা না বলা বা যা অসত্য তা না বলার এবং সেই সঙ্গে অন্যকেও মিথ্যা বলতে উৎসাহিত না করা বা অন্যের অসত্য বচনকে অনুমোদন না করা।<ref name=pkshah5v/>{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|pp=২২৮–২৩১}} |
|||
# "[[অস্তেয়]]" ("চুরি না করা"): জৈন গৃহস্থের স্বেচ্ছাপূর্বক প্রদত্ত কোনও জিনিস গ্রহণ করা কর্তব্য নয়।{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|p=২২৮}}{{sfn|বিজয় কে. জৈন|২০১২|p=৬৮}} এছাড়াও কোনও জিনিস প্রদত্ত হলেও জৈন সাধু-সাধ্বীদের তা গ্রহণের আগে অনুমতি গ্রহণ করতে হয়।{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|p=২৩১}} |
|||
# "[[ব্রহ্মচর্য]]" (ইন্দ্রিয়-সংযম"): জৈন সাধু-সাধ্বীদের পক্ষে যৌনতা ও ইন্দ্রিয়-বিলাসিতা নিষিদ্ধ। গৃহস্থের পক্ষে ব্রহ্মচর্য ব্রতের অর্থ দাম্পত্যসঙ্গীর প্রতি সৎ ও বিশ্বস্ত থাকা।<ref name=pkshah5v/>{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|pp=২২৮–২৩১}} |
|||
# "[[অপরিগ্রহ]]" ("অনাসক্তি"): এই ব্রতটি পার্থিব ও মনস্তাত্ত্বিক সম্পত্তির প্রতি অনাসক্তির এবং চাহিদা ও লোভ এড়িয়ে চলার উপদেশ দেয়।{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|pp=২২৮–২৩১}} জৈন সাধু ও সাধ্বীরা সম্পত্তি ও সামাজিক সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন, কিছুই নিজেদের সম্পদ হিসেবে সঞ্চয় করে রাখেন না এবং কারও প্রতি আসক্ত থাকেন না।{{sfn|নাথুভাই শাহ|২০০৪|p=১১২}}{{sfn|লং|২০০৯|p=১০৯}} |
|||
জৈনধর্ম সাতটি সম্পূরক ব্রত পালনেরও উপদেশ দেয়। এর মধ্যে তিনটিকে বলা হয় "গুণব্রত" ও চারটিকে বলা হয় "শিক্ষাব্রত"।{{sfn|বিজয় কে. জৈন|২০১২|p=৮৭–৮৮}}{{sfn|টুকোল|১৯৭৬|p=৫}} জৈন সাধু ও সাধ্বীরা অতীতকালে জীবনের শেষপর্বে "[[সল্লেখনা]]" (বা "সান্থারা") নামে এক "ধর্মীয় মৃত্যুবরণ"-এর ব্রত পালন করতেন। কিন্তু বর্তমানে এই ব্রতপালনের ঘটনা দুর্লভ।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=১৭৯–১৮০}} এই ব্রতে সাধু-সাধ্বীরা স্বেচ্ছায় ধীরে ধীরে খাদ্যগ্রহণ ও জলপান কমিয়ে দিয়ে অনাসক্তির সঙ্গে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করে নিতেন।{{sfn|জৈনি|২০০০|p=১৬}}{{sfn|টুকোল|১৯৭৬|p=৭}} মনে করা হয় যে, এই ব্রত পালনের মাধ্যমে নেতিবাচক কর্মের প্রভাব কমে যায় এবং তা আত্মার পুনর্জন্মে প্রভাব বিস্তার করে।{{sfn|উইলিয়ামস|১৯৯১|pp=১৬৬–১৬৭}} |
|||
== ধর্মানুশীলন == |
|||
===সন্ন্যাসবাদ=== |
|||
{{মূল নিবন্ধ|সন্ন্যাস (জৈনধর্ম)}} |
|||
[[File:Jain meditation.jpg|thumb|ধ্যানরতা জৈন সন্ন্যাসিনী]] |
|||
জৈনধর্মে সন্ন্যাস প্রথাকে উৎসাহ দেওয়া হয় এবং সম্মান করা হয়। জৈন সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীরা অত্যন্ত কঠোর ও পবিত্র জীবন যাপন করেন। তাঁরা জৈনধর্মের পঞ্চ মহাব্রত সম্পূর্ণত পালন করেন। তাঁদের স্থায়ী বাসস্থান বা বিষয়সম্পত্তি কিছুই নেই। দূরত্ব যাই হোক, তাঁরা খালি পায়ে হেঁটে যাতায়াত করেন। [[চতুর্মাস্য|চতুর্মাস্যের]] চার মাস বাদে বছরের অন্যান্য সময় তাঁরা এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ান। তাঁরা টেলিফোন বা বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন না। তাঁরা রান্না করেন না। ভিক্ষা করে খান। তাঁরা সাধারণত মুখ ঢাকার জন্য একটি কাপড়ের খণ্ড রাখেন যাতে হাওয়ায় ভাসমান জীবাণুদের ক্ষতি না হয়। তাঁদের অধিকাংশই ঝাঁটার মতো দেখতে একটি জিনিস নিয়ে ঘোরেন। রায়োহরণ নামে এই ঝাঁটার মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের সামনের রাস্তা ঝাঁট দিতে দিতে হাঁটেন। বসার আগেও তাঁরা বসার জায়গাটি ঝাঁট দিয়ে নেন, যাতে কোনো কীটপতঙ্গ তাঁদের চাপে মারা না যায়।<ref>{{harvnb|Dundas|2002|pp=152, 163–164}}</ref> |
|||
==ধর্মানুশীলন প্রথা== |
|||
জৈনদের উৎসবে সন্ন্যাসীদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক নয়। এঁরা পুরোহিত নন। যদিও কোনো কোনো সম্প্রদায়ে এমন একজন পূজারিকে বিশেষ দৈনিক অনুষ্ঠানগুলি ও মন্দিরের অন্যান্য পৌরোহিত্যকর্মের জন্য নিযুক্ত করা হয়, যিনি নিজে জৈন নন।{{sfn|Dundas|2002|p=204}} |
|||
===কৃচ্ছব্রত ও সন্ন্যাস=== |
|||
=== প্রার্থনা === |
|||
{{Main|কৃচ্ছব্রত|জৈন সন্ন্যাসপ্রথা}} |
|||
জৈনরা কোনো সুবিধা বা পার্থিব চাহিদা পূরণ অথবা পুরস্কারের আশায় আবেগশূন্য দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করেন না। <ref name="Shah1998a">{{harvnb|Shah|1998a|p=251}}</ref> তাঁরা প্রার্থনা করেন কর্মবন্ধন নাশ ও মোক্ষলাভের জন্য।<ref name="Nayanar 2005b, p.35 Gāthā 1.29">Nayanar (2005b), p.35 Gāthā 1.29</ref> ‘বন্দেতদ্গুণলব্ধায়ে’ (সেই দেবতাদের কাছে সেই গুণাবলির কামনায় আমরা প্রার্থনা করি) – জৈনদের এই প্রার্থনা বাক্যের মাধ্যমে তাঁদের প্রার্থনার মূল কথাটি বোঝা যায়।<ref name="Nayanar 2005b, p.35 Gāthā 1.29"/> |
|||
{{multiple image |
|||
==== নবকার মন্ত্র ==== |
|||
| image1 = Ellora, cave 33, Digambar Jain guru (9841591645).jpg |
|||
[[নবকার মন্ত্র]] হল জৈনধর্মের একটি মৌলিক প্রার্থনা। এটি যে কোনো সময় পাঠ করা যায়। দেবত্ব অর্জনের জন্য সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক গুণগুলিকে এই মন্ত্রের দ্বারা উপাসনা করা হয়। এই মন্ত্রে কোনো ব্যক্তিবিশেষের নাম নেই। জৈনধর্মে পূজা বা প্রার্থনার উদ্দেশ্য হল জাগতিক কামনা ও বন্ধনকে ধ্বংস করা এবং আত্মার মোক্ষ অর্জন। |
|||
| width1 = 120 |
|||
| caption1 = দিগম্বর সাধু |
|||
| image2 = Acharya Vijayavallabhasuri.jpg |
|||
| width2 = 155 |
|||
| caption2 = শ্বেতাম্বর-দেরবাসী সাধু |
|||
}} |
|||
{{multiple image |
|||
| image1 = Jain 1.jpg |
|||
| caption1 = এক শ্বেতাম্বর সাধ্বী (বিংশ শতাব্দীর আদিভাগ) |
|||
| width1 = 106 |
|||
| image2 = Viramati Mataji.jpg |
|||
| caption2 = এক দিগম্বর সাধ্বী |
|||
| width2 = 157 |
|||
}} |
|||
প্রধান ভারতীয় ধর্মগুলির মধ্যে জৈনধর্মেই কৃচ্ছব্রত সর্বাপেক্ষা কঠোর।{{sfn|কর্ট|২০০১এ|pp=১১৮–১২২}}{{sfn|কিউভার্নস্টর্ম|২০০৩|p=১১৩}}{{sfn|কিউভার্নস্টর্ম|২০০৩|pp=১৬৯–১৭৪, ১৭৮–১৯৮ পাদটীকা সহ}} কৃচ্ছব্রতীর জীবনে থাকে নগ্নতা (যা বস্ত্রের প্রতিও অনাসক্তির প্রতীক), উপবাস, শারীরিক কৃচ্ছসাধনা ও তপস্যা। এগুলির উদ্দেশ্য হল অতীত কর্মকে দগ্ধ করা এবং নতুন কর্মের উৎপাদন বন্ধ করা। জৈনধর্মে এই দুইই সিদ্ধ অবস্থায় উপনীত হওয়ার ও মোক্ষলাভের ক্ষেত্রে আবশ্যক মনে করা হয়।{{sfn|কর্ট|২০০১এ|pp=১১৮–১২২}}{{sfn|কিউভার্নস্টর্ম|২০০৩|pp=২০৫–২১২ পাদটীকা সহ}}{{sfn|বালসারোউইকজ|২০১৫|pp=১৪৪–১৫০}} |
|||
"তত্ত্বার্থসূত্র" ও "উত্তরাধ্যয়ন সূত্র" ইত্যাদি জৈন ধর্মগ্রন্থে বিস্তারিতভাবে কৃচ্ছসাধনার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তীকালীন জৈন গ্রন্থগুলিতে ছ’টি বাহ্যিক ও ছ’টি আন্তরিক অনুশীলনের কথা প্রায়শই পুনরুল্লিখিত হয়েছে।{{sfn|কর্ট|২০০১এ|pp=১২০–২১}} বাহ্যিক কৃচ্ছসাধনার মধ্যে পড়ে সম্পূর্ণ উপবাস, সীমিত পরিমাণে খাদ্যগ্রহণ, নির্দিষ্ট খাদ্যসামগ্রীই গ্রহণ, সুস্বাদু খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকা, মাংসের কৃচ্ছসাধন এবং মাংসকে রক্ষণ (অর্থাৎ, লোভের উৎপত্তি ঘটাতে পারে এমন কিছু এড়িয়ে চলা)।{{sfn|কর্ট|২০০১এ|pp=১২০–১২২}} আন্তরিক কৃচ্ছসাধনার মধ্যে পড়ে অনুতাপ, স্বীকারোক্তি, সাধু-সাধ্বীদের সম্মান প্রদর্শন ও সহায়তা করা, অধ্যয়ন, ধ্যান এবং দেহ পরিত্যাগের জন্য শারীরিক চাহিদাগুলিকে উপেক্ষা করা।{{sfn|কর্ট|২০০১এ|pp=১২০–১২২}} বাহ্যিক ও আন্তরিক কৃচ্ছসাধনার তালিকা গ্রন্থ ও পরম্পরাভেদে ভিন্ন ভিন্ন।{{sfn|কিউভার্নস্টর্ম|২০০৩|p=১৮২ সঙ্গে পাদটীকা ৩}}{{sfn|জনসন|১৯৯৫|pp=১৯৬–১৯৭}} কৃচ্ছসাধনাকে কামনার নিয়ন্ত্রণ এবং জীবের (আত্মা) পরিশুদ্ধিকরণের একটি উপায় হিসেবে দেখা হয়।{{sfn|কিউভার্নস্টর্ম|২০০৩|pp=১৬৯–১৭৪, ১৭৮–১৯৮ সঙ্গে পাদটীকা}} মহাবীর প্রমুখ তীর্থংকরেরা বারো বছর ধরে কৃচ্ছসাধনা করে এই জাতীয় ব্রতের উদাহরণ স্থাপন করেছিলেন।{{sfn|কর্ট|২০০১এ|pp=১২১–১২২}}{{sfn|শান্তি লাল জৈন|১৯৯৮|p=৫১}}{{sfn|বালসারোউইকজ|২০১৫|pp=১৫–১৮, ৪১–৪৩}} |
|||
জৈন সন্ন্যাসী সংগঠন বা "সংঘ" চার শ্রেণিতে বিন্যস্ত: "সাধু" (সন্ন্যাসী, "মুনি"), "সাধ্বী" (সন্ন্যাসিনী, "আর্যিকা"), "[[শ্রাবক (জৈনধর্ম)|শ্রাবক]]" (পুরুষ গৃহস্থ) ও "শ্রাবিকা" (গৃহস্থ নারী)। শেষোক্ত দুই শ্রেণি কৃচ্ছব্রতী ও স্বশাসিত আঞ্চলিক সমাবেশে তাঁদের "গছ" বা "সমুদায়" নামক সন্ন্যাসী সংগঠনগুলির পৃষ্ঠপোষকতা করে।{{sfn|কর্ট|২০০১এ|pp=৪৮–৪৯}}{{sfn|বাল্লসারোউইকজ|২০০৯|p=১৭}}{{sfn|নাথুভাই শাহ|২০০৪|pp=২–৩}} জৈন সন্ন্যাসপ্রথায় ওষ্ঠাধর ঢেকে রাখাকে উৎসাহিত করা হয়। সেই সঙ্গে "দণ্ডাসন" নামে উলের সুতো সহ এক ধরনের দীর্ঘ দণ্ড ব্যবহার করতে হয়, যাতে পথে এসে পড়া পিঁপড়ে ও কীটপতঙ্গদের আলতো করে সরিয়ে দেওয়া যায়।{{sfn|বিজয় কে. জৈন|২০১৩|p=১৯৭}}{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|p=১৫২, ১৬৩–১৬৪}}{{sfn|জৈনি|১৯৯৮|p=১৯০}} |
|||
===খাদ্য ও উপবাস=== |
|||
{{Main|জৈন নিরামিশাহারপন্থা|জৈনধর্মে উপবাস}} |
|||
সকল জীবিত সত্ত্বার প্রতি অহিংসার নীতিটিই জৈন সংস্কৃতিকে [[জৈন নিরামিশাহারপন্থা|নিরামিশপন্থী]] করে তুলেছে। ধর্মপ্রাণ জৈনরা [[দুগ্ধ-নিরামিশাহার]] অভ্যাস করেন, অর্থাৎ তাঁরা ডিম না খেলেও কোনও দুগ্ধজাত খাদ্যের উৎপাদনের সময় প্রাণীদের প্রতি হিংসাত্মক আচরণ না হলে সেই খাদ্য গ্রহণ করেন। প্রাণীকল্যাণের বিষয়টি গুরুত্ব পেলে অবশ্য খাদ্য বিষয়ে [[ভেগানিজম|প্রাণীজ পণ্য ব্যবহার থেকে বিরত থাকাই]] উৎসাহিত করা হয়।{{sfn|ভুর্স্ট|২০১৫|p=১০৫}} জৈন সাধু, সাধ্বী ও কোনও কোনও অনুগামী আলু, পিঁয়াজ ও রসুনের মতো কন্দমূল ব্যবহার থেকে বিরত থাকেন, যাতে এই সব শিকড়গুলি উপড়ানোর সময় ক্ষুদ্র জীব-জীবাণু ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। এছাড়া কন্দ ও অঙ্কুরের উদ্গমকে উচ্চতর জীবন্ত সত্ত্বার একটি বৈশিষ্ট্য বলেও গণ্য করা হয়।{{sfn|সানগেভ|১৯৮০|p=২৬০}}{{efn|জৈনধর্মের অহিংসা নীতিতে কোনও সাধু বা সাধ্বীকে বৃক্ষ সহ সকল জীবিত সত্ত্বাকে স্পর্শ অথবা বিরক্ত করা থেকে বিরত থাকতে হয়। এই ধর্মে জলে সাঁতার কাটা, আগুন জ্বালানো বা নেভানো, শূন্যে হস্ত আস্ফালনও নিষিদ্ধ। কারণ, এই ধরনের কাজগুলি সেই সব বস্তুর অবস্থায় স্থিত জীবদের নিপীড়ন বা আঘাত করতে পারে।{{sfn|টেলর|২০০৮|pp=৮৯২–৮৯৪}}}} জৈন সাধু ও ধর্মপ্রাণ গৃহস্থেরা সূর্যাস্তের পর খাদ্যগ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। এটিকে তাঁরা বলেন "রাত্রি-ভোজন-ত্যাগ-ব্রত"।{{sfn|জৈনি|২০০০|p=২৮৫}} দিগম্বর সম্প্রদায়ের সাধুরা দিনে একবার মাত্র ভোজন আরও কঠিনতর এক ব্রত পালন করেন।{{sfn|জৈনি|২০০০|p=২৮৫}} |
|||
জৈনরা নির্দিষ্টভাবে উৎসবের সময় উপবাস করেন।{{sfn|উইলি|২০০৯|p=৮৫}} "উপবাস" ছাড়াও এটিকে "তপস্যা" বা "ব্রত"-ও বলা হয়।{{sfn|উইলি|২০০৯|pp=৮৫–৮৬}} ব্যক্তিবিশেষ নিজের সামর্থ্য অনুযায়ীও উপবাস করতে পারেন।{{sfn|রাম ভূষণ প্রসাদ সিং|২০০৮|pp=৯২–৯৪}} দিগম্বর জৈনেরা "দশ-লক্ষণ-পর্ব" উপলক্ষ্যে উপবাস করেন দিনে একবার বা দুইবার খাদ্য গ্রহণ করে, দশ দিন ধরে উষ্ণ জল পান করে বা উৎসবের প্রথম ও শেষ দিনটিতে সম্পূর্ণ উপবাস করে।{{sfn|উইলি|২০০৯|p=৭২}} এটি কোনও জৈন সাধু-সাধ্বীর এই পর্যায়ের ধর্মানুশীলনের অনুকরণ।{{sfn|উইলি|২০০৯|p=৭২}} শ্বেতাম্বর জৈনরা অনুরূপভাবে আট দিনের "পর্যুষণ" উৎসবে "সম্বৎসরী-প্রতিক্রমণ" সহ একই প্রথা অনুশীলন করেন।{{sfn|উইলি|২০০৯|pp=৭২, ৮৫–৮৬}} কথিত হয় যে, এই প্রথার মাধ্যমে ব্যক্তির আত্মা থেকে কর্মের প্রভাব মুক্ত হয় এবং ব্যক্তি পূণ্য অর্জন করেন।{{sfn|Wiley|2009|p=85}} "একদিবসীয়" উপবাসের সময়কাল ৩৬ ঘণ্টা, যা শুরু হয় পূর্বদিন সূর্যাস্তের থেকে এবং শেষ হয় মূল উপবাস-দিনের পরদিন সূর্যোদয়ের ৪৮ মিনিট পরে।{{sfn|উইলি|২০০৯|p=৮৫}} গৃহস্থদের মধ্যে উপবাস বিশেষভাবে পালন করেন নারীরা। এর মাধ্যমে নারীরা তাঁদের ধর্মানুরাগ ও পবিত্রতা বজায় রাখেন, নিজেদের পরিবারের জন্য পূণ্য অর্জন করেন এবং ভাবীকালের জন্য কল্যাণ সুরক্ষিত করেন। এক-একটি সামাজিক ও সহায়তামূলক নারীগোষ্ঠীর মধ্যেও কিছু কিছু ধর্মীয় উপবাস প্রথা আয়োজিত হয়।{{sfn|উইলি|২০০৯|p=৮৬}}বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে বন্ধুবান্ধব ও পরিবারের মধ্যে দীর্ঘকালীন উপবাস অনুষ্ঠিত হয়।{{sfn|উইলি|২০০৯|p=৮৬}} |
|||
===উপবাস=== |
|||
অধিকাংশই বছরের বিভিন্ন সময়ে উপবাস করেন। বিশেষত [[জৈনধর্মে উপবাস|উৎসবের সময় উপবাস]] জৈনধর্মে একটি বিশেষ প্রথা। বিভিন্ন ভাবে উপবাস করা যায়। এটি উপবাসকর্তার সামর্থের উপর নির্ভর করে। কেউ দিনে একবার বা দুবার খান, কেউ সারাদিন শুধু জল পান করেন, কেউ সূর্যাস্তের পরে খান, কেউ রান্না করা খাবার খান না, কেউ চিনি, তেল বা নুন ছাড়া নির্মিত রান্না খান। উপবাসের উদ্দেশ্য হল আত্মসংযম অনুশীলন এবং মনকে শুদ্ধ করে প্রার্থনায় অধিকতর মানসিক শক্তি প্রয়োগ। |
|||
===ধ্যান=== |
===ধ্যান=== |
||
{{ |
{{main|জৈন ধ্যান}} |
||
{{multiple image |
|||
জৈনরা [[জৈন ধ্যান|সাময়িকা]] নামে এক ধ্যানপদ্ধতি গড়ে তুলেছে। ‘সাময়িকা’ কথাটি এসেছে ‘[[সময়]]’ কথাটি থেকে। সাময়িকার উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ শান্তির অনুভূতি পাওয়া ও আত্মার অপরিবর্তনশীলতা অনুধাবন করা। এই ধরনের ধ্যানের মূল ভিত্তি বিশ্ব ও আত্মার পুনঃপুনঃ আগমনের ধারণা।<ref>{{harvnb|Jaini|1998|pp=180–182}}</ref> [[পর্যুশন]] উৎসবের সময় সাময়িকা ধ্যান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মনে করা হয়, ব্যক্তির আবেগগুলি নিয়ন্ত্রণ ও সামঞ্জস্যবিধানে ধ্যান বিশেষ সহকারী। মনের চিন্তাভাবনা যেহেতু ব্যবহার, কাজ ও উদ্দেশ্য লাভের পথে বিশেষ প্রভাবশালী তাই ভিতর থেকে এগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার উপর জৈনধর্মে বিশেষ জোর দেওয়া হয়।<ref>{{harvnb|Shah|1998a|pp=128–131}}</ref> |
|||
| image1 = Jain meditation.jpg |
|||
| width1 = 171 |
|||
| image2 = Shravanabelagola_Bahubali_wideframe.jpg |
|||
| width2 = 153 |
|||
| footer = বাঁদিকে: জৈন সাধ্বীদের ধ্যান, ডানদিকে: দশম শতাব্দীতে নির্মিত দণ্ডায়মান ধ্যানভঙ্গিমায় ([[কায়োৎসর্গ]] ভঙ্গি) [[গোম্মতেশ্বর মূর্তি]] |
|||
}} |
|||
জৈনধর্ম ধ্যানকে ধর্মানুশীলনের একটি আবশ্যিক অঙ্গ মনে করে। কিন্তু এই ধর্মে ধ্যানের উদ্দেশ্যে হিন্দুধর্মে বা বৌদ্ধধর্মে ধ্যানের উদ্দেশ্য থেকে অনেকটাই আলাদা।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=১৬৬–১৬৯}} অন্যান্য ভারতীয় ধর্মে ধ্যানের উদ্দেশ্য রূপান্তরমূলক অন্তর্দৃষ্টি বা আত্ম-উপলব্ধি হলেও জৈনধর্মে ধ্যানের উদ্দেশ্য হল কর্ম-সংক্রান্ত আসক্তি ও কর্মক্রিয়া বন্ধ করা।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=১৬৬–১৬৯}} [[পদ্মনাভ জৈনী|পদ্মনাভ জৈনীর]] মতে, "[[সামায়িক]]" হল জৈনধর্মে "ধ্যানের সংক্ষিপ্ত পর্যায়সমূহ"-এর এক অনুশীলন, যা আবার "শিক্ষাবর্ত" অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক সংযমের অঙ্গ।{{sfn|জৈনি|১৯৯৮|pp=১৮০–১৮১}} সামায়িকের উদ্দেশ্য হল মানসিক প্রশান্তি অর্জন, যা কিনা দ্বিতীয় শিক্ষাবর্ত।{{efn|প্রথমটি হল "দেশবকশিক" (আবদ্ধ পরিমণ্ডলে বাস করে জাগতিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ রাখা)। তৃতীয়টি হল "পোসধোপবাস" (শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমী ও চতুর্দশী তিথিতে উপবাস)। চতুর্থটি হল "দান" (জৈন সাধু, সাধ্বী বা আধ্যাত্মিক ব্যক্তিদের ভিক্ষাপ্রদান)।{{sfn|জৈনি|১৯৯৮|pp=১৮০–১৮১}}}} সাধু-সাধ্বীরা দিনে অন্তত তিনবার সামায়িক অভ্যাস করেন। কিন্তু একজন গৃহস্থ এটিকে জৈন মন্দিরে পূজা এবং অন্যান্য সেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত করে নেন।{{sfn|জৈনি|১৯৯৮|pp=১৮০–১৮২}}{{sfn|এস. এ. জৈন|১৯৯২|p=২৬১}}{{sfn|নাথুভাই শাহ|২০০৪|pp=১২৮–১৩১}} জনসন ও জৈনির মতে সামায়িক ধ্যানের থেকে বেশি কিছুর দ্যোতক এবং জৈন গৃহস্থের কাছে এটি "সাময়িকভাবে সন্ন্যাস মর্যাদা অর্জনের" একটি স্বেচ্ছামূলক আচার।{{sfn|Johnson|1995|pp=189–190}}{{efn|ডুন্ডাসের মতে, আদিকালীন জৈনধর্মে সম্ভবত সামায়িকের অর্থ ছিল সম্যক চরিত্র।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|p=১৭০}}}} |
|||
===আচার-অনুষ্ঠান ও পূজা=== |
|||
জৈনরা ছয়টি কর্তব্য পালন করেন। ‘আবশ্যক’ নামে পরিচিত এই কর্তব্যগুলি হল: ‘সম্যিকা’ বা (শান্তি অনুশীলন), ‘চতুর্বিংশতি’ (তীর্থঙ্কর বন্দনা), ‘বন্দন’ (গুরু ও সন্ন্যাসীদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন), [[প্রতিক্রমণ]] (অন্তর্দৃষ্টি), [[কায়োৎসর্গ]] (স্থির থাকা) ও প্রত্যখ্যন (ত্যাগ)।<ref>{{harvnb|Jaini|1998|p=190}}</ref> |
|||
{{Main|জৈন আচার-অনুষ্ঠান}} |
|||
[[File:Shravanbelgola Gomateshvara feet prayer1.jpg|thumb|upright|[[বাহুবলী|বাহুবলীর]] একটি মূর্তির পায়ে প্রার্থনা]] |
|||
জৈনদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ে অনেক আচার-অনুষ্ঠান প্রচলিত রয়েছে। ডুন্ডাসের মতে, শ্বেতাম্বর জৈনদের মধ্যে গৃহস্থদের আচার-অনুষ্ঠানগত পথটি "কৃচ্ছসাধনার মূল্যবোধ দ্বারা অতিমাত্রায় পরিপূরিত"। এখানে অনুষ্ঠানগুলি পালিত হয় তীর্থংকরদের সম্মানে বা তাঁদের কৃচ্ছব্রতী জীবনের ঘটনাবলি উদ্যাপনের উদ্দেশ্যে অথবা কোনও কৃচ্ছব্রতীর মনস্তাত্ত্বিক ও পার্থিব জীবনকে পুরোভাগে রেখে তা অবলম্বন করার জন্য।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=১৮৭–১৮৯}}{{sfn|জৈনি|১৯৯৮|pp=১৬২–১৬৫, ২৯৫–২৯৬}} এই ধর্মের চরম অনুষ্ঠানটি হল "সল্লেখনা"। এটি হল খাদ্য ও পানীয় ত্যাগ করে এক কৃচ্ছব্রতীর স্বেচ্ছায় ধর্মসম্মত মৃত্যুবরণ।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=১৮৭–১৮৯}} দিগম্বর জৈনরাও একই ধারণা পোষণ করে। কিন্তু জীবনচক্র ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলি এক প্রকারে হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানেরই অনুরূপ।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=১৮৭–১৮৯}} এই পারস্পরিক মিলগুলি দেখা যায় প্রধানত জীবনচক্র-সংক্রান্ত (হিন্দু মতে ষোড়শ সংস্কার) আচার-অনুষ্ঠানগুলিতে। সম্ভবত জৈন ও হিন্দু সমাজের মধ্যে সহাবস্থানের কারণেই এই মিল দেখা গিয়েছিল এবং এই অনুষ্ঠানগুলিকে প্রয়োজনীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ বলে জ্ঞান করা হত।{{sfn|জৈনি|১৯৯৮|pp=২৯১–২৯৯}}{{sfn|উইলি|২০০৯|pp=১৮৬–১৮৭}} |
|||
জৈনরা আনুষ্ঠানিকভাবে অসংখ্য দেবদেবীর পূজা করে।{{sfn|জৈনি|১৯৯৮|pp=১৬২–১৬৫, ২৯৫–২৯৬}} এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে [[অরিহন্ত (জৈনধর্ম)|জিনদের]] পূজা বিশেষ প্রচলিত। জৈনধর্মে দেবতা হিসেবে জিন কোনও [[অবতার]] নন, বরং কোনও কৃচ্ছব্রতী তীর্থংকরের প্রাপ্ত সর্বজ্ঞতার সর্বোচ্চ অবস্থা।{{sfn|জৈনি|১৯৯৮|pp=২৯৫–২৯৯}} চব্বিশ জন তীর্থংকরের মধ্যে জৈনরা প্রধানত চারজনকে পূজা করেন: [[মহাবীর]], [[পার্শ্বনাথ]], [[নেমিনাথ]] ও [[ঋষভনাথ]]।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|p=৪০}} তীর্থংকর ব্যতীত অন্যান্য সন্তদের মধ্যে দিগম্বর সম্প্রদায়ে [[বাহুবলী|বাহুবলীর]] ভক্তিমূলক পূজা বহুল প্রচলিত।{{sfn|কর্ট|২০১০|pp=১৮২–১৮৪}} "[[পঞ্চ কল্যাণক]]" অনুষ্ঠানগুলি আয়োজিত হয় তীর্থংকরদের জীবনের পাঁচটি ঘটনার স্মরণে। এগুলির মধ্যে রয়েছে: "[[পঞ্চ কল্যাণক প্রতিষ্ঠা মহোৎসব]]", "পঞ্চ কল্যাণক পূজা " ও "স্নাত্রপূজা"।{{sfn|জৈনি|১৯৯৮|pp=১৯৬, ৩৪৩, ৩৪৭}}{{sfn|জৈনি|১৯৯৮|pp=১৯৬–১৯৯}} |
|||
==দর্শন== |
|||
{{মূল নিবন্ধ|জৈন দর্শন}} |
|||
===আত্মা ও কর্ম=== |
|||
{{মূল নিবন্ধ|জৈনধর্মে কর্ম}} |
|||
জৈন দর্শন অনুসারে, আত্মার সহজাত গুণ হল এর পবিত্রতা। এই আত্মা অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত অন্তর্দৃষ্টি, অনন্ত আনন্দ ও অনন্ত শক্তির সকল গুণ তার আদর্শ অবস্থায় বহন করে।<ref>{{harvnb|Jaini|1998|pp = 104–106}}</ref> বাস্তব ক্ষেত্রে যদিও এই গুণগুলি আত্মার সঙ্গে ‘[[জৈনধর্মে কর্ম|কর্ম]]’ নামে এক পদার্থের যোগের ফলে বাধা প্রাপ্ত হয়।<ref name=Jaini107>{{harvnb|Jaini|1998|p=107}}</ref> জৈনধর্মের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল আত্মাকে কর্মের বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে [[মোক্ষ (জৈনধর্ম)|মোক্ষ]] লাভ করা। |
|||
[[File:A Jain ritual offerings and puja recital at a temple, worship in Jainism.jpg|thumb|left|upright|জৈন পূজার্চনার অন্যতম অঙ্গ নৈবেদ্য উৎসর্গ ও মন্ত্রপাঠ।{{sfn|উইলি|২০০৯|pp=৪৫–৪৬, ২১৫}}]] |
|||
আত্মা ও কর্মের সম্পর্কটি সোনার উপমার সাহায্যে বোঝানো হয়। প্রাকৃতিক অবস্থায় সোনার মধ্যেও নানান অশুদ্ধ দ্রব্য মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। একই ভাবে আদর্শ বা আত্মার পবিত্র অবস্থাও কর্মের অশুদ্ধ অবস্থার সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। সোনার মতোই আত্মাকেও যথাযথ পদ্ধতিতে শুদ্ধ করতে হয়।<ref name=Jaini107/> জৈনদের কর্মবাদ ব্যবহৃত হয় ব্যক্তিগত কাজে দায়িত্ব আরোপ করার জন্য এবং এটি অসাম্য, যন্ত্রণা ও দুঃখের ব্যাখ্যা করার জন্য প্রদর্শিত হয়। |
|||
জৈনধর্মে মৌলিক অনুষ্ঠানটি হল দেবতার দর্শন। এই দেবতাদের মধ্যে থাকেন জিন,{{sfn|লিন্ডসে জোনস|২০০৫|p=৪৭৭১}} বা অন্য [[যক্ষ|যক্ষ ও যক্ষিণীগণ]], ব্রহ্মাদেব প্রমুখ দেবদেবীগণ, ৫২ জন বীর, [[পদ্মাবতী (জৈনধর্ম)|পদ্মাবতী]], [[অম্বিকা (জৈনধর্ম)|অম্বিকা]] ও ১৬ জন বিদ্যাদেবী ([[সরস্বতী]] ও [[লক্ষ্মী]] সহ)।{{sfn|উইলি|২০০৯|pp=৩৩, ৫৯, ৯২, ১৩৮, ১৯১}}{{sfn|কর্ট|১৯৮৭|pp=২৩৫–২৫৫}}{{sfn|মিশ্র|রায়|২০১৬|pp=১৪১–১৪৮}} তেরাপন্থি দিগম্বরেরা তাঁদের আনুষ্ঠানিক পূজা শুধু তীর্থংকরদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন।{{sfn|দালাল|২০১০এ|p=৩৬৫}} পূজানুষ্ঠানকে বলা হয় "দেবপূজা"। জৈনদের সকল উপ-সম্প্রদায়েই এই দেবপূজার চল রয়েছে।{{sfn|জৈনি|১৯৯৮|pp=১৯৯–২০০}} সাধারণত গৃহস্থ জৈন সাদামাটা বস্ত্র পরিধান করে নৈবেদ্যের থালা নিয়ে মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করে হাঁটু গেড়ে বসে [[নমস্কার]] করে, তারপর মন্ত্রপাঠ ও প্রার্থনা সম্পূর্ণ করে। ক্ষেত্রবিশেষে মন্দিরের পুরোহিত সেই গৃহস্থকে সাহায্য করেন। তারপর গৃহস্থ নৈবেদ্য রেখে দিয়েই মন্দির ছেড়ে বেরিয়ে যান।{{sfn|জৈনি|১৯৯৮|pp=১৯৯–২০০}} |
|||
জৈনদের আচারগুলির মধ্যে "[[অভিষেক]]" অর্থাৎ দেবমূর্তির আনুষ্ঠানিক স্নান অন্তর্গত।{{sfn|প্রতাপাদিত্য পাল|১৯৮৬|p=২৯}} কোনও কোনও জৈন সম্প্রদায়ে পূজারি (যাঁকে "উপাধ্যে" বলা হয়) নিয়োগ করা হয় মন্দিরের পূজানুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্য। ক্ষেত্রবিশেষে জৈন মন্দিরে হিন্দু পুরোহিতও পূজার্চনা করেন।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=২০৪–২০৫}}{{sfn|সালভাডোরি|১৯৮৯|pp=১৬৯–১৭০}} সাড়ম্বরে পূজায় অন্ন, টাটকা ও শুকনো ফল, ফুল, নারকেল, মিষ্টান্ন ও অর্থ নৈবেদ্য হিসেবে প্রদান করা হয়। কেউ কেউ কর্পূরের দীপ প্রজ্বলিত করে এবং চন্দনের তিলক দেয়। এছাড়াও ভক্তেরা ধর্মগ্রন্থ (বিশেষত তীর্থংকরদের জীবনকাহিনি) পাঠ করেন।{{sfn|বাব|১৯৯৬|pp=৩২–৩৩}}{{sfn|উইলি|২০০৯|pp=৪৫–৪৬, ২১৫}} |
|||
===রত্নত্রয়=== |
|||
{{মূল নিবন্ধ|রত্নত্রয়}} |
|||
আত্মার [[মোক্ষ (জৈনধর্ম)|মোক্ষ]] অর্জনের জন্য জৈনধর্মে নিম্নোক্ত রত্নত্রয়ের কথা বলা হয়েছে:{{sfn|Jain|2011|p=6, 15}} |
|||
# সম্যক দর্শন – সঠিক অন্তর্দৃষ্টি ও সত্যের অনুসন্ধান এবং একই সঙ্গে সকল বস্তুকে স্পষ্টভাবে দেখার পথে বাধা সৃষ্টিকারী কুসংস্কারগুলিকে বর্জন। |
|||
# সম্যক জ্ঞান – জৈন আদর্শগুলি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান। |
|||
# সম্যক চরিত্র – জৈন আদর্শগুলি জীবনে প্রয়োগ। |
|||
হিন্দু ও বৌদ্ধদের মতো ধর্মপ্রাণ জৈনরাও [[মন্ত্র|মন্ত্রের]] কার্যকরিতায় বিশ্বাস করেন এবং নির্দিষ্ট কিছু ধ্বনি ও শব্দকে স্বাভাবিকভাবেই পবিত্র, শক্তিশালী ও আধ্যাত্মিক মনে করেন।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=৮১–৮২}}{{sfn|নায়নার|২০০৫|p=৩৫}} সর্বাধিক বিখ্যাত মন্ত্রগুলির মধ্যে জৈনধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ে যেটি বহুলভাবে স্বীকৃত, সেটি হল "[[ণমোকার মন্ত্র|পঞ্চ নমস্কার]]"। জৈনরা এটিকে চিরন্তন এবং প্রথম তীর্থংকরের যুগ থেকে প্রচলিত মনে করা হয়।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=৮১–৮২}}{{sfn|ভুর্স্ট|২০১৫|p=১০৭}} মধ্যযুগীয় পূজানুষ্ঠানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তীর্থংকর-সহ "ঋষিমণ্ডল"-এর তান্ত্রিক রেখাচিত্রগুলি।{{sfn|গঘ|২০১২|pp=১–৪৭}} জৈনদের তান্ত্রিক প্রথায় মন্ত্র ও আচার-অনুষ্ঠানের ব্যবহার হয় পুনর্জন্মের লোকে পূণ্যার্জনের লক্ষ্যে।{{sfn|কর্ট|২০০১বি|pp=৪১৭–৪১৯}} |
|||
===তত্ত্ব=== |
|||
জৈন [[অধিবিদ্যা|অধিবিদ্যার]] ভিত্তি সাত অথবা নয়টি মৌলিক আদর্শ। এগুলি ‘[[তত্ত্ব (জৈনধর্ম)|তত্ত্ব]]’ নামে পরিচিত। তত্ত্বগুলির মাধ্যমে মানুষের দুর্ভাগ্যের প্রকৃতি এবং জীবনের চরম লক্ষ্য আত্মার [[মোক্ষ (জৈনধর্ম)|মোক্ষ]] লাভের জন্য উক্ত দুর্ভাগ্যের সমাধানের কথা বলা হয়েছে:<ref>{{harvnb|Glasenapp|1999|p=177}}</ref> |
|||
# জীব: জীবি সত্ত্বার সারবস্তুকে বলে ‘জীব’। এটি এমন এমন এক বস্তু যা দেহে অবস্থান করে, অথচ দেহ অপেক্ষা পৃথক। চৈতন্য, জ্ঞান ও ধারণা এর মৌলিক বৈশিষ্ট্য। |
|||
# অজীব: পদার্থ, স্থান ও সময় নিয়ে গঠিত প্রাণহীন বস্তুসকল। |
|||
# অস্রব: আত্মায় কর্মের (অজীবের একটি বিশেষ রূপ) আবির্ভাবের কারণে সৃষ্ট জীব ও অজীবের সংযোগ। |
|||
# বন্ধ: কর্ম জীবকে মুখোশের আড়ালে বদ্ধ করে এবং যথাযথ জ্ঞান ও ধারণার সত্য অধিকার থেকে জীবকে বিরত রাখে। |
|||
# সংবর: সঠিক চরিত্রের দ্বারা কর্মের আবির্ভাব স্তব্ধ করা সম্ভব। |
|||
# নির্জরা: তপশ্চর্যার মাধ্যমে অস্তিত্ববান কর্মকে পরিহার করা যায়। |
|||
# [[মোক্ষ (জৈনধর্ম)|মোক্ষ]]: যে মুক্ত আত্মা কর্মকে পরিহার করেছে এবং পবিত্রতা, যথাযথ জ্ঞান ও ধারণার স্বকীয় গুণাবলি অর্জন করেছে। |
|||
=== উৎসব === |
|||
কোনো কোনো গবেষক আরও দুটি শ্রেণী যুক্ত করেছেন: ‘পুণ্য’ (স্তবনীয়) ও ‘পাপ’ (স্তবের অযোগ্যতা)। এগুলি কর্মের সঙ্গে যুক্ত ক্রিয়া। |
|||
{{Main|জৈন উৎসবসমূহ}} |
|||
===স্যাদবাদ=== |
|||
[[File:Das Lakshana (Paryusana) celebrations, New York City Jain temple 2.JPG|thumb|[[নিউ ইয়র্ক সিটি|নিউ ইয়র্ক সিটির]] [[জৈন সেন্টার অফ আমেরিকা|জৈন সেন্টার অফ আমেরিকায়]] আয়োজিত [[দশলক্ষণ]] (পর্যুষণ) উৎসব]] |
|||
[[File:Mahavra 1900 art.jpg|thumb|মহাবীর জৈন দার্শনিক ধারণাগুলি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিস্তারিতভাবে ‘অনেকান্তবাদ’ ব্যবহার করেছিলেন ([[রাজস্থান|রাজস্থানের]] চিত্রকলা, ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ)।]] |
|||
সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বাৎসরিক জৈন উৎসবটিকে শ্বেতাম্বর জৈনরা বলেন "পর্যুষণ" এবং দিগম্বর জৈনরা বলেন "দশলক্ষণ পর্ব "। [[হিন্দু পঞ্জিকা|ভারতীয় পঞ্জিকার]] সৌরচান্দ্র [[ভাদ্র (হিন্দু পঞ্জিকা)|ভাদ্রপদ]] (ভাদ্র) মাসের কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী তিথি থেকে এই উৎসব শুরু হয়। গ্রেগরিয়ান পঞ্জিকা অনুসারে এই সময়টি অগস্ট বা সেপ্টেম্বর মাসে পড়ে।{{sfn|দালাল|২০১০এ|pp=১৬৪, ২৮৪}}{{sfn|মেলটন|২০১১|p=৬৭৩}} শ্বেতাম্বর জৈনরা আট দিন এবং দিগম্বর জৈনরা এই উৎসব দশ দিন ধরে পালন করেন।{{sfn|দালাল|২০১০এ|pp=১৬৪, ২৮৪}} এই সময়টিতে জৈন শ্রাবক-শ্রাবিকারা উপবাস ও প্রার্থনা করেন। এই উৎসবের সময় পাঁচটি প্রতিজ্ঞার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।{{sfn|মেলটন|২০১১|p=৬৭৩}} শ্বেতাম্বর জৈনরা এই সময় ''কল্পসূত্র'' পাঠ করেন; দিগম্বর জৈনরা পাঠ করেন তাঁদের নিজস্ব ধর্মগ্রন্থগুলি। এই উৎসবটি হল এমন এক সময় যখন জৈনরা সক্রিয়ভাবে জীবহিংসা নিবারণের জন্য প্রযত্ন করেন। এই সময় তাঁরা পশুপাখিদের মুক্তি দেন এবং প্রাণীহত্যার প্রতিরোধ করেন।{{sfn|দালাল|২০১০এ|pp=১৬৪, ২৮৪}} |
|||
স্যাদবাদ হল [[অনেকান্তবাদ]] ধারণা থেকে উৎসারিত একটি মতবাদ। এই মতবাদে প্রতিটি শব্দবন্ধ বা অভিব্যক্তির শুরুতে ‘স্যাদ’ উপসর্গটি যুক্ত করে অনেকান্তকে ব্যাখ্যা করেছে।<ref>{{harvnb|Sangave|2006|p=48}}</ref> সংস্কৃত ভাষায় ‘স্যাদ্’ শব্দমূলটির অর্থ ‘হয়তো’। তবে স্যাদবাদের ক্ষেত্রে এই শব্দটির অর্থ ‘কোনো কোনো উপায়ে’ বা ‘কোনো কোনো মতে’। সত্য যেহেতু জটিল, তাই কোনো একক উপায়ে এটির পূর্ণ প্রকৃতিটিকে প্রকাশ করা যায় না। সেই কারণে একটি অনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি বোঝাতে এবং বক্তব্যের মধ্যে থেকে রক্ষণশীলতাকে বাদ দিতে প্রতিটি অভিব্যক্তিমূলক শব্দের গোড়ায় ‘স্যাৎ’ কথাটি যুক্ত করা হয়েছে।<ref>{{harvnb|Koller|2000|pp=400–407}}</ref> স্যাদবাদের সাতটি অনির্দিষ্ট ধারণা বা [[সপ্তভঙ্গি]] হল:<ref name = "grimes">{{harvnb|Sangave|2006|pp=48–50}}</ref> |
|||
#''স্যাদ্-অস্তি''—কোনো কোনো উপায়ে, এটি আছে; |
|||
#''স্যাদ্-নাস্তি''—কোনো কোনো উপায়ে, এটি নেই; |
|||
#''স্যাদ্-অস্তি-নাস্তি''—কোনো কোনো উপায়ে, এটি আছে এবং এটি নেই; |
|||
#''স্যাদ্-অস্তি-অবক্তব্যঃ''—কোনো কোনো উপায়ে এটি আছে এবং এটি বর্ণনার অতীত; |
|||
#''স্যাদ্-নাস্তি-অবক্তব্যঃ''—কোনো কোনো উপায়ে এটি নেই এবং এটি বর্ণনার অতীত; |
|||
#''স্যাদ্-অস্তি-নাস্তি-অবক্তব্যঃ''—কোনো কোনো উপায়ে এটি আছে, এটি নেই এবং এটি বর্ণনার অতীত; |
|||
#''স্যাদ্-অবক্তব্যঃ''—কোনো কোনো উপায়ে এটি অবক্তব্য। |
|||
{{Quote box |
|||
সাতটি অভিব্যক্তির মাধ্যমে সময়, স্থান, বস্তু ও আকারের দৃষ্টিকোণ থেকে সত্যের জটিল ও বহুমুখী প্রকৃতিটিকে প্রকাশ করা হয়েছে।<ref name="grimes" /> সত্যের জটিলতাকে অস্বীকার করা হল গোঁড়ামি-প্রসূত বিপথগামিতা।<ref name="kollerjurno"/> |
|||
|quote = '''ক্ষমাশীলতা''' |
|||
<poem> |
|||
আমি সকল জীবকে ক্ষমা করছি, |
|||
সকল জীব আমাকে ক্ষমা করুক। |
|||
জগতে সকলে আমার বন্ধু, |
|||
আমার কোনও শত্রু নেই। |
|||
</poem> |
|||
|source = — ''জৈন উৎসবের শেষ দিনের প্রার্থনা''{{sfn|দালাল|২০১০এ|p=২৮৪}} |
|||
|bgcolor=#FFDDBB |
|||
|align = left |
|||
}} |
|||
উৎসবের শেষ দিনটির কেন্দ্রে থেকে প্রার্থনা ও ধ্যানসভা। এটি "সম্বৎসরী" নামে পরিচিত। জৈনরা এই দিনটিকে প্রায়শ্চিত্ত, সকলকে ক্ষমা করার, সকল জীবের থেকে ক্ষমা চাওয়ার, শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থনার এবং জগতের সকলকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করার দিন মনে করেন।{{sfn|দালাল|২০১০এ|pp=১৬৪, ২৮৪}} অন্যের প্রতি "''[[মিচ্ছামি দুক্কদম]]''" বা "''খমাৎ খম্না''" বলে ক্ষমাপ্রার্থনা করা হয়। এর অর্থ হল, "যদি আমি জ্ঞানত বা অজ্ঞানত বাক্য বা কর্মের মাধ্যমে তোমার প্রতি কোনও অন্যায় করে থাকি, তবে আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি।" "পর্যুষণ" কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল "বিশ্বস্ত থাকা" বা "একত্রিত হওয়া"।{{sfn|কর্ট|১৯৯৫|p=১৬০}} |
|||
[[মহাবীর জয়ন্তী|মহাবীর জন্ম কল্যাণক]] উৎসবটি আয়োজিত হয় মহাবীরের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে। ভারতীয় পঞ্জিকার চান্দ্রসৌর [[চৈত্র]] মাসের ত্রয়োদশী তিথিতে মহাবীর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। গ্রেগরিয়ান পঞ্জিকা অনুসারে এই দিনটি মার্চ বা এপ্রিল মাসে পড়ে।{{sfn|দালাল|২০১০এ|p=২২০}}{{sfn|নাথুভাই শাহ|২০০৪|p=২১১}} এই উৎসব উপলক্ষ্যে জৈনরা মন্দির, তীর্থ ও পুণ্যস্থানে যাত্রা করেন এবং মহাবীরের শোভাযাত্রা বের করেন। ভারতের [[বিহার]] রাজ্যের রাজধানী [[পটনা|পটনার]] উত্তরে মহাবীরের জন্মস্থান বলে কথিত কুন্দগ্রামে জৈনরা বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।{{sfn|দালাল|২০১০এ|p=২২০}} [[দীপাবলি (জৈনধর্ম)|দীপাবলির পরের দিনটি]] জৈনরা মহাবীরের [[মোক্ষ (জৈনধর্ম)|মোক্ষলাভের]] দিন হিসেবে উদ্যাপন করেন।{{sfn|পেশিলিস|রাজ|২০১৩|p=৮৬}} হিন্দুদের [[দীপাবলি]] উৎসবটিও এই একই দিনেই (কার্তিক অমাবস্যা) উদ্যাপিত হয়। এই দিন জৈন মন্দির, বাড়ি, কার্যালয় ও দোকানগুলি [[প্রদীপ]] ও বৈদ্যুতিক বাতি দিয়ে সাজানো হয়। আলো জ্ঞানের এবং অজ্ঞান দূরীকরণের প্রতীক। এই দিন মিষ্টি বিতরণ করা হয়। দীপাবলির সকালে সারা বিশ্বে জৈন মন্দিরগুলিতে মহাবীরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনার পর "নির্বাণ লাড়ু" বিতরিত হয়। জৈন নববর্ষও দীপাবলির পরদিনই শুরু হয়।{{sfn|পেসিলিস|রাজ|২০১৩|p=৮৬}} হিন্দুদের [[অক্ষয়তৃতীয়া]] ও [[রাখিবন্ধন|রাখিবন্ধনের]] মতো উৎসবগুলি জৈনরাও পালন করেন।{{sfn|পেসিলিস|রাজ|২০১৩|p=৮৫}}{{sfn|দালাল|২০১০এ|p=১৬৪}} |
|||
স্যাদবাদ হল আংশিক দৃষ্টিভঙ্গির তত্ত্ব।<ref name="Grimes202">{{harvnb|Sangave|2006|pp=50–51}}</ref> ‘নয়বাদ’ কথাটি দুটি [[সংস্কৃত]] শব্দ নিয়ে গঠিত: ‘নয়’ (আংশিক দৃষ্টিভঙ্গি) ও ‘বাদ’ (দর্শন মতবাদ বা বিতর্ক)। এই মতে একটি দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। প্রতিটির বস্তুর অনন্ত দিক রয়েছে। কিন্তু যখন আমরা সেটি কোনো একটি মতের দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করি, আমরা শুধুমাত্র সেই মতের সঙ্গে যুক্ত দিকগুলি নিয়েই আলোচনা করি এবং অন্যান্য দিকগুলি অগ্রাহ্য করি।<ref name="Grimes202" /> নয়বাদের মতে দার্শনিক বিবাদের উৎপত্তির কারণ দৃষ্টিভঙ্গির বিভ্রান্তি এবং আমরা সেই দৃষ্টিভঙ্গিগুলিই গ্রহণ করি যেগুলি ‘আমাদের অনুসরণের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি’। আমরা হয়তো তা বুঝতে পারি না। ভাষা ও সত্যের জটিল প্রকৃতির বোধগম্যতার সীমাবদ্ধতার মধ্যে কথা বলতে গিয়ে মহাবীর নয়বাদের ভাষা ব্যবহার করেন। নয়বাদ সত্যের একটি আংশিক অভিপ্রকাশ। এটি আমাদের সত্যকে অংশ ধরে ধরে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে।<ref>{{harvnb|Shah|1998b|p=80}}</ref> |
|||
==সম্প্রদায় ও প্রথাসমূহ== |
|||
অনেকান্তবাদে অধিকতর পোষাকিভাবে দেখানো হয়েছে যে, বস্তু তাদের গুণাবলি ও অস্তিত্বের ধরন অনুসারে অনন্ত। মানুষের সীমাবদ্ধ ধারণাশক্তি দিয়ে তার সকল দিক ও সকল রূপের ধারণা করা যায় না। শুধুমাত্র কেবলবাদীরাই বস্তুর সকল দিক ও রূপের ধারণা করতে পারেন। অন্যরা শুধু আংশিক জ্ঞান অর্জন করতে পারে।<ref>{{harvnb|Jaini|1998|p=91}}</ref> এই মত অনুসারে, একজন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি সর্বোচ্চ সত্যের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না।<ref name="Dundas2002"/> |
|||
{{Main|জৈন সম্প্রদায়সমূহ}} |
|||
{{multiple image |
|||
| image1 = Mahavir.jpg |
|||
| width1 = 125 |
|||
| caption1 = দিগম্বর [[মহাবীর|মহাবীরের]] মূর্তি |
|||
| image2 = Shri Simandhar Swami.jpg |
|||
| width2 = 125 |
|||
| caption2 = শ্বেতাম্বর [[সীমান্ধর স্বামী|সীমান্ধর স্বামীর]] মূর্তি |
|||
}} |
|||
জৈন সমাজ দু’টি প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত: [[দিগম্বর]] ও [[শ্বেতাম্বর]]। দিগম্বর সাধুরা কোনও বস্ত্র পরিধান করেন না; সাধ্বীরা শুধু সেলাই-না-করা অনাড়ম্বর [[শাড়ি]] পরেন। দিগম্বর সাধ্বীদের বলা হয় "[[আর্যিকা]]"। অন্যদিকে শ্বেতাম্বর সাধু-সাধ্বীরা সবাই সেলাই-না-করা সাদা কাপড় পরেন।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|p=৪৫}} |
|||
জৈন বিশ্বাস অনুযায়ী, [[চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য|চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের]] শাসনকালে আচার্য ভদ্রবাহু এক দ্বাদশ-বর্ষ-ব্যাপী দুর্ভিক্ষের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং নিজের শিষ্যদের নিয়ে কর্ণাটকে চলে গিয়েছিলেন। কথিত আছে, আচার্য ভদ্রবাহুর শিষ্য [[স্থুলভদ্র]] [[মগধ|মগধে]] থেকে যান।{{sfn|ক্লার্ক|বেয়ার|২০০৯|p=৩২৬}} আচার্য ভদ্রবাহু ফেরার পর দেখেন যে, যাঁরা মগধে রয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা শ্বেত বস্ত্র পরিধান করতে শুরু করেছেন। যে জৈনরা নগ্ন থাকতেন তাঁদের কাছে এই রীতিটি গ্রহণযোগ্য হয়নি।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|p=৪৭}} জৈনদের প্রথাগত বিশ্বাস অনুযায়ী এইভাবেই দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের বিভাজন শুরু হয়। দিগম্বরেরা নগ্ন থাকেন এবং শ্বেতাম্বরেরা শ্বেত বস্ত্র পরিধান করেন।{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|p=৪৬}} দিগম্বরেরা এটি জৈনদের "অপরিগ্রহ" নীতির বিরোধী মনে করেছিলেন। কারণ, এই নীতি অনুযায়ী জৈনদের বস্ত্রের প্রতিও অনাসক্ত হয়ে সম্পূর্ণ নগ্নাবস্থায় থাকতে হত। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে শ্বেতাম্বরেরা বলভীর মহাসভা আয়োজন করেন। এই সভায় দিগম্বরেরা যোগ দেননি। এই সভাতেই শ্বেতাম্বর জৈনরা তাঁদের রক্ষিত সেই সব গ্রন্থগুলিকে প্রামাণ্য ধর্মশাস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করেন, যেগুলিকে দিগম্বরেরা বরাবরই প্রত্যাখ্যান করে এসেছিলেন। মনে করা হয় যে, এই ধর্মসভার মাধ্যমেই জৈনদের প্রধান দু’টি সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐতিহাসিক বিভাজনটি দৃঢ় ভিত্তি লাভ করে।{{sfn|প্রাইস|২০১০|pp=১০৪–১০৫}}{{sfn|ফোর|২০১৫|pp=২১–২২}} দিগম্বর মতবাদের প্রাচীনতম নথিটি [[কুন্দকুন্দ]] কর্তৃক প্রাকৃত ভাষায় লেখা ''সুত্তপহুদ'' গ্রন্থে পাওয়া যায়।{{sfn|জৈনি|১৯৯১|p=৩}} |
|||
===গুণস্থান=== |
|||
==ইতিহাস== |
|||
{{মূল নিবন্ধ|জৈনধর্মের ইতিহাস}} |
|||
===উৎস=== |
|||
{{আরও দেখুন|জৈনধর্মের কালরেখা}} |
|||
জৈনধর্মের উৎস অজ্ঞাত।<ref name="flugelP" />{{sfn|Glasenapp|1999|p=13}} জৈনধর্ম হল একটি অনন্তকালীন দর্শন।{{sfn|Zimmer|1952|pp=x, 180-181}} [[জৈন বিশ্বতত্ত্ব#কালচক্র|জৈন কালচক্র]] অনুসারে, কালচক্রের প্রত্যেক অর্ধে চব্বিশ জন বিশিষ্ট মানুষ [[তীর্থঙ্কর|তীর্থঙ্করের]] পর্যায়ে উন্নীত হন এবং মানুষকে মোক্ষের পথ প্রদর্শন করেন। তাই এঁদের বলা হয় মানুষের আধ্যাত্মিক সহায়ক।{{sfn|Rankin|2013|p=40}} মহাবীরের পূর্বসূরী তথা ২৩তম তীর্থঙ্কর [[পার্শ্বনাথ]] ছিলেন একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব।{{sfn|Zimmer|1952|pp=182-183}}{{sfn|Glasenapp|1999|pp=16-17}} তিনি খ্রিস্টপূর্ব ৯ম-৭ম শতাব্দীর মধ্যবর্তী কোনো এক সময়ে জীবিত ছিলেন।{{sfn|Zimmer|1952|pp=183}}{{sfn|Glasenapp|1999|pp=23-24}}<ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি|লেখক=Paul Dundas|শিরোনাম=Jainism|প্রকাশক=Encyclopaedia Britannica|বছর=2013|ইউআরএল= http://www.britannica.com/EBchecked/topic/299478/Jainism}}</ref>{{sfn|Jaini|1998|p=10}} আনুশাসনিক ধর্মগ্রন্থগুলিতে পার্শ্বনাথের অনুগামীদের উল্লেখ আছে। ''উত্তরাধ্যয়ন'' সূত্রের একটি কিংবদন্তিতে পার্শ্বনাথের শিষ্যদের সঙ্গে মহাবীরের শিষ্যদের সাক্ষাতের কথা আছে। এই সাক্ষাতের ফলে পুরনো ও নতুন জৈন শিক্ষাদর্শের মিলন ঘটেছিল।<ref name="Jacobi Herman page 465"/> |
|||
দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর জৈনদের পার্থক্য রয়েছে তাদের প্রথা ও রীতিনীতি এবং পোষাক-নীতিতে, {{sfn|জোন্স|রায়ান|২০০৭|p=২১১}}{{sfn|উমাকান্ত পি. শাহ|১৯৮৭|p=৫}}{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=৩১–৩৩}} উপদেশাবলির ব্যাখ্যায়{{sfnজৈনি|২০০০|pp=২৭–২৮}}{{sfn|উমাকান্ত পি. শাহ|১৯৮৭|p=৫}} এবং জৈন ইতিহাস প্রসঙ্গে (বিশেষত তীর্থংকর প্রসঙ্গে)।{{sfn|কৈলাস চন্দ জৈন|১৯৯১|p=১২}}{{sfn|নাথুভাই শাহ|২০০৪|pp=৭৩–৭৪}}{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|p=২১}}{{sfn|উমাকান্ত পি. শাহ|১৯৮৭|p=১৭}}{{sfn|উমাকান্ত পি. শাহ|১৯৮৭|pp=৭৯–৮০}} তাঁদের সন্ন্যাসের নিয়মের মধ্যেও পার্থক্য আছে,{{sfn|দালাল|২০১০এ|p=১৬৭}} যেমন আছে দুই সম্প্রদায়ের [[মূর্তিতত্ত্ব|মূর্তিতত্ত্বে]]।{{sfn|দালাল|২০১০এ|p=১৬৭}} শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ে সাধুর তুলনায় সাধ্বী বেশি,{{sfn|কর্ট|২০০১এ|p=৪৭}} যেখানে দিগম্বর সম্প্রদায় প্রধানত সাধুদের নিয়েই গঠিত{{sfn|ফুগেল|২০০৬|pp=৩১৪–৩৩১, ৩৫৩–৩৬১}} এবং দিগম্বরেরা মনে করেন যে, পুরুষেরা আত্মার মোক্ষলাভের পথে অধিকতর এগিয়ে থাকে।{{sfn|লং|২০১৩|pp=৩৬–৩৭}}{{sfn|হার্ভে|২০১৬|pp=১৮২–১৮৩}} অন্যদিকে শ্বেতাম্বর জৈনরা মনে করেন যে, নারীরাও কৃচ্ছসাধনের মাধ্যমে মোক্ষলাভ করতে পারেন{{sfn|হার্ভে|২০১৬|pp=১৮২–১৮৩}}{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=৫৫–৫৯}} এবং বলেন যে, উনবিংশ তীর্থংকর [[মাল্লীনাথ]] ছিলেন নারী।{{sfn|ভ্যালেলি|২০০২|p=১৫}} শেষোক্ত মতটি দিগম্বর জৈনেরা প্রত্যাখ্যান করেন।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|p=৫৬}} |
|||
খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ধমান মহাবীর জৈনধর্মের সবচেয়ে প্রভাবশালী শিক্ষকে পরিণত হন। জৈনরা তাঁকে ২৪তম এবং এই কালচক্রের সর্বশেষ তীর্থঙ্কর রূপে শ্রদ্ধা করেন। জৈন বিশ্বাস অনুযায়ী, তিনি এমন এক ব্যক্তিত্ব যিনি শুরু থেকেই বহু প্রাচীনকালে প্রতিষ্ঠিত একটি ধর্মের অনুগামী।<ref name="Jacobi Herman page 465">Jacobi Herman, Jainism IN Encyclopedia of Religion and Ethics Volume 7, James Hastings (ed.) page 465</ref> |
|||
[[মথুরা]] অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে [[কুষাণ সাম্রাজ্য|কুষাণ সাম্রাজ্যের]] সমসাময়িক কালের (আনুমানিক খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী) অনেক জৈন মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে।{{sfn|জৈনি|২০০০|p=১৬৭}} সেই সব মূর্তিতে তীর্থংকরদের দেখা গিয়েছে নগ্ন অবস্থায় এবং সাধুদের দেখা গিয়েছে বাঁ-কাঁধে বস্ত্রাবৃত অবস্থায়, যাকে জৈনশাস্ত্রে "অর্ধফলক" (অর্ধ-বস্ত্রাবৃত) বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।{{sfn|জৈনি|২০০০|p=১৬৭}} মনে করা হয় যে, [[যাপনীয়]] শাখাটির উৎপত্তি এই "অর্ধফলক" ধারণাটির থেকেই। এই শাখায় দিগম্বরদের নগ্নতা-নীতির সঙ্গে বেশ কয়েকটি শ্বেতাম্বর বিশ্বাসও গৃহীত হয়েছিল।{{sfn|জৈনি|২০০০|p=১৬৭}} ফ্লুগেলের মতে, আধুনিক যুগে নতুন জৈন ধর্মীয় আন্দোলনগুলি হল "প্রাথমিকভাবে জৈনধর্মের ভক্তিবাদী রূপ", যার সঙ্গে "জৈন মহাযান" শৈলীর ভক্তিবাদের একটি সাদৃশ্য রয়েছে।{{sfn|ফ্লুগেল|২০০৫|pp=১৯৪–২৪৩}} |
|||
===কিংবদন্তিমূলক ইতিহাস=== |
|||
জৈন কিংবদন্তি অনুসারে, [[সকলপুরুষ]] নামে তেষট্টি জন বিশিষ্ট সত্ত্বা এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন।<ref name=devdutt>{{harvnb|Glasenapp|1999|pp=134–135}}</ref> জৈন কিংবদন্তিমূলক ইতিহাস এই সত্ত্বাদের কর্মকাণ্ডের সংকলন।<ref>{{harvnb|Dundas|2002|p=12}}</ref> সকলপুরুষদের মধ্যে চব্বিশ জন তীর্থঙ্কর, বারো জন [[চক্রবর্তী]], নয় জন বলদেব, নয় জন বাসুদেব ও নয় জন প্রতিবাসুদেব রয়েছেন।<ref name=devdutt/> |
|||
==শাস্ত্র ও ধর্মগ্রন্থ== |
|||
চক্রবর্তীরা হলেন বিশ্বের সম্রাট ও জাগতিক রাজ্যের প্রভু।<ref name=devdutt/> তাঁর জাগতিক ক্ষমতা প্রচুর। তাও বিশ্বের বিশালতার তুলনায় তাঁর আকাঙ্ক্ষাগুলিকে তিনি খাটো হিসেবে দেখেন। [[জৈন পুরাণ|জৈন পুরাণগুলিতে]] বারো জন চক্রবর্তীর তালিকা পাওয়া যায়। তাঁদের গায়ের রং সোনালি।<ref>{{harvnb|Shah|1987|p=72}}</ref> জৈন ধর্মশাস্ত্রে উল্লিখিত একজন শ্রেষ্ঠ চক্রবর্তী হলেন ভরত। কিংবদন্তি অনুসারে, তাঁর নামেই দেশের নাম হয়েছে ‘ভারতবর্ষ’।{{sfn|Jain|1991|p=5}} |
|||
{{Main|জৈন সাহিত্য}} |
|||
{{Multiple images |
|||
| image1 = Jain Agamas.jpeg |
|||
| caption1 = ''শ্রুত জ্ঞান'' (পূর্ণ শাস্ত্রজ্ঞান) সম্বলিত ফলক |
|||
| width1 = 83 |
|||
| image2 = Suryaprajnapati Sutra.jpg |
|||
| caption2 = সূর্যপ্রজ্ঞপ্তিসূত্র, খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ বা তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত শ্বেতাম্বর জৈনদের একটি জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্রন্থ। উপরে: আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে রচিত উক্ত গ্রন্থের একটি পুথি।<ref>[http://www.schoyencollection.com/23-religions/living-religions/23-17-jainism/astronomy/ms-5297 সূর্যপ্রজ্ঞপ্তিসূত্র] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20170615024618/http://www.schoyencollection.com/23-religions/living-religions/23-17-jainism/astronomy/ms-5297 |date=15 June 2017 }}, দ্য শোয়েন কালেকশন, লন্ডন/অসলো</ref> |
|||
| width2 = 150 |
|||
| image3 = Mangulam inscription.jpg |
|||
| caption3 = খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর [[মঙ্গুলম]] অভিলিখন |
|||
| width3 = 150 |
|||
}} |
|||
জৈনদের প্রামাণ্য ধর্মশাস্ত্রগুলিকে বলা হয় "আগম"। কথিত আছে, অনেকটা প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলির মতো এগুলিও [[মৌখিক প্রথা|মৌখিক প্রথার]] মাধ্যমে প্রচলিত ছিল।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=৬০–৬১}} মনে করা হয় যে, এগুলির উৎস হল তীর্থংকরদের উপদেশাবলি, যা তাঁদের "[[গণধর]]" অর্থাৎ প্রধান শিষ্যগণ "শ্রুত জ্ঞান" হিসেবে পরম্পরাক্রমে ছড়িয়ে দিতেন।{{sfn|চম্পৎ রাই জৈন|১৯২৯বি|p=১৩৫–১৩৬}}{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|pp=১০৯–১১০}} শ্বেতাম্বর জৈনরা মনে করেন যে, কথ্য শাস্ত্রভাষাটি ছিল [[অর্ধমাগধী]]; অন্যদিকে দিগম্বর জৈনরা এই শাস্ত্রভাষাটিকে এক ধরনের ধ্বনি-অনুনাদ মনে করেন।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=৬০–৬১}} |
|||
শ্বেতাম্বরেরা বিশ্বাস করেন যে তাঁরা জৈনদের আদি ৫০টি শাস্ত্রের ৪৫টি সংরক্ষণ করেছেন (হারিয়ে গিয়েছে শুধু একটি অঙ্গ শাস্ত্র ও চারটি পূর্ব শাস্ত্র); কিন্তু দিগম্বরেরা মনে করেন যে সবগুলিই হারিয়ে গিয়েছে{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|p=৬১}}{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|pp=১১২-১১৩, ১২১–১২২}} এবং আচার্য [[ভূতাবলি]] ছিলেন শেষ সাধু যাঁর মূল প্রামাণ্য ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে আংশিক জ্ঞান ছিল। তাঁদের মতে, দিগম্বর আচার্যেরা চার "অনুযোগ" সহ আদিতম জ্ঞাত দিগম্বর জৈন ধর্মগ্রন্থগুলি পুনঃসৃজন ঘটিয়েছিলেন।{{sfn|বিজয় কে. জৈন|২০১৬|p=বারো}}{{sfn|জৈনী|১৯৯৮|p=৭৮–৮১}}{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|p=১২৪}} দিগম্বর ধর্মগ্রন্থগুলি আংশিকভাবে প্রাচীনতর শ্বেতাম্বর ধর্মগ্রন্থগুলির সঙ্গে সহমত পোষণ করে, কিন্তু সেই সঙ্গে জৈনদের প্রধান দুই সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থের মধ্যে কিছু লক্ষণীয় পার্থক্যও বিদ্যমান।{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|pp=১২১–১২২}} খ্রিস্টীয় ৬০০ থেকে ৯০০ অব্দের মধ্যবর্তী সময়ে দিগম্বর জৈনেরা অপ্রধান প্রামাণ্য শাস্ত্র রচনা করে তাকে চারটি অংশ বা "বেদ"-এ ভাগ করেন: ইতিহাস, সৃষ্টিবিদ্যা, দর্শন ও নীতিবিদ্যা।{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|pp=১২৩–১২৪}}{{efn|এগুলি হিন্দুধর্মের চার [[বেদ]] হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির।{{sfn|দালাল|২০১০এ|pp=১৬৪–১৬৪}}}} |
|||
নয় জন করে বলদেব, বাসুদেব ও প্রতিবাসুদেব রয়েছেন। কোনো কোনো দিগম্বর ধর্মগ্রন্থে তাঁদের যথাক্রমে বলদেব, নারায়ণ ও প্রতিনারায়ণ নামে উল্লেখ করা হয়েছে। [[ভদ্রবাহু|ভদ্রবাহুর]] ''[[জিনচরিত]]'' (খ্রিস্টপূর্ব ৩য়-৪র্থ অব্দ) গ্রন্থে এই ভ্রাতৃমণ্ডলীর উৎসের কথা বলা হয়েছে।<ref name=jaini2000>{{harvnb|Jaini|2000|p=377}}</ref> বলদেবরা হলেন অহিংস যোদ্ধা। বাসুদেবরা সহিংস যোদ্ধা এবং প্রতিবাসুদেবরা হলেন মূলত খলনায়ক।কিংবদন্তি অনুসারে, বাসুদেবরা প্রতিবাসুদেবদের শেষ পর্যন্ত হত্যা করেছেন। নয় জন বলদেবের মধ্যে আট জন মোক্ষ লাভ করেছেন এবং সর্বশেষ জন স্বর্গে গিয়েছেন। বাসুদেবরা তাঁদের হিংসাত্মক কার্যকলাপের জন্য নরকে গিয়েছেন। সত্যের জন্য কাজ করতে চেয়েও শুধুমাত্র সহিংসতা অবলম্বনের জন্য তাঁদের এই শাস্তি হয়েছে।<ref name="Shah1987">{{harvnb|Shah|1987|pp=73–76}}</ref> |
|||
জৈনধর্মের সর্বাধিক জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী ধর্মগ্রন্থগুলি হল এই ধর্মের অপ্রধান সাহিত্য। এগুলির মধ্যে "[[কল্পসূত্র]]" বিশেষভাবে শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ে জনপ্রিয়তা লাভ করে। শ্বেতাম্বরেরা ভদ্রবাহুকে (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দ) এই গ্রন্থের রচয়িতা মনে করেন। এই প্রাচীন পণ্ডিত দিগম্বর সম্প্রদায়েও সম্মানিত হয়ে থাকেন। তাঁরা মনে করেন যে, ইনিই তাঁরের প্রাচীন দক্ষিণ কর্ণাটক অঞ্চলে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁদের পরম্পরার সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন।{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|pp=১২৫–১২৬}} অপরদিকে শ্বেতাম্বরেরা মনে করেন যে ভদ্রবাহু নেপালে চলে গিয়েছিলেন।{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|pp=১২৫–১২৬}} উভয় সম্প্রদায়ই তাঁর চরিত "নির্যুক্তি" ও "সংহিতা"-গুলিকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। [[উমাস্বাতী]] রচিত প্রাচীনতম প্রাপ্ত সংস্কৃত গ্রন্থ "[[তত্ত্বার্থসূত্র]]" জৈনধর্মের সকল সম্প্রদায়েই প্রামাণিক বলে বিবেচিত হয়।{{Sfn|জোনস|রায়ান|২০০৭|pp=৪৩৯–৪৪০}}{{efn|"জৈনদের কাছে "তত্ত্বার্থসূত্র" নামে পরিচিত গ্রন্থটি জৈনদের সকল চারটি পরম্পরাতেই তাঁদের ধর্মের আদিতম, সর্বাধিক প্রামাণ্য ও সর্ব-সমন্বিত সংক্ষিপ্তসার বলে স্বীকৃত হয়।"{{sfn|উমাস্বাতী|১৯৯৪|p=এগারো–তেরো}}}}{{sfn|ডুন্ডাস|২০০৬|pp=৩৯৫–৩৯৬}} দিগম্বর সম্প্রদায়ে কুন্দকুন্দ কর্তৃক রচিত গ্রন্থগুলি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন হয়ে থাকে এবং এগুলি ঐতিহাসিকভাবে প্রভাবশালীও বটে।{{sfn|ফিনেগান|১৯৮৯|p=২২১}}{{sfn|বারকারোউইকজ|২০০৩|pp=২৫–৩৪}}{{sfn|চট্টোপাধ্যায়|২০০০|p=২৮২–২৮৩}} অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জৈন ধর্মগ্রন্থ হল "[[সময়সার]]", "[[রত্নকরন্দ শ্রাবকাচার]]" ও "[[নিয়মসার]]"।{{sfn|জৈনি|১৯৯১|p=৩২–৩৩}} |
|||
===রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা=== |
|||
==বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্মের সঙ্গে তুলনা== |
|||
===তামিলনাড়ু=== |
|||
{{main|জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম|জৈনধর্ম ও হিন্দুধর্ম}} |
|||
এই জৈন ধর্মই অন্যতম সত্য একটা ধর্ম, এই ধর্মের অনুসারীরা উচ্চ দর্শনবাদে বিশ্বাস করে। |
|||
হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন তিন ধর্মই কর্ম ও পুনর্জন্মের ন্যায় ধ্যানধারণা ও মতবাদে বিশ্বাসী; এই তিন ধর্মের উৎসব-অনুষ্ঠান ও সন্ন্যাসপ্রথার মধ্যেও অনেক সাদৃশ্য আছে।{{sfn|সলোমন|হিগিনস|১৯৯৮|pp=১১–২২}}{{sfn|অ্যাপেলটন|২০১৬|pp=১–২১, ২৫–২৭, ৫৭–৫৮, ৮২–৮৪}}{{sfn|ম্যাকফাউল|২০০৬|pp=২৭–২৮}} তিন ধর্মের কোনওটিই চিরন্তন স্বর্গ বা নরক অথবা বিচারদিনে বিশ্বাস করে না। দেবদেবীতে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস, মূল মতবাদের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করা এবং প্রার্থনা, আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসবে যোগদানের ক্ষেত্রে তিন ধর্মই অনুগামীদের স্বাধীনতা দিয়ে থাকে। তিন ধর্মেই অহিংসার ন্যায় নীতিকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়,{{sfn|শ|ডেমি|২০১৭|p=৬৩৫|quote=Ahiṃsā (to do no harm) is a significant aspect of three major religions: Jainism, Hinduism and Buddhism<br>বঙ্গানুবাদ: অহিংসা তিনটি প্রধান ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ দিক: জৈনধর্ম, হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম}} কামনা, ব্যক্তির কর্ম, উদ্দেশ্যের সঙ্গে দুঃখকে যুক্ত করে এবং আধ্যাত্মিকতাকে অজ্ঞানতামুক্ত শান্তি, পরম সুখাবস্থা ও মোক্ষের উপায় মনে করা হয়।{{sfn|সলোমন|হিগিনস|১৯৯৮|pp=১৮–২২}}{{sfn|ম্যাকফাউল|২০০৬|pp=২৭–৪০}} |
|||
অস্তিত্বের স্বরূপ-সংক্রান্ত দার্শনিক মতের দিক থেকে জৈনধর্ম বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের ভিন্ন মত পোষণ করে। তিন ধর্মই ক্ষণস্থায়িত্বে বিশ্বাস করে। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম "[[অনাত্তা]]"-র ("চিরন্তন সত্ত্বা বা আত্মার অনস্তিত্ব") ধারণাটি যোগ করে। হিন্দুধর্ম চিরন্তন অপরিবর্তনীয় [[আত্মা (হিন্দুধর্ম)|আত্মার]] তত্ত্বে বিশ্বাস করে, যেখানে জৈনধর্ম চিরন্তন কিন্তু পরিবর্তনশীল "জীব"-এর ("আত্মা") ধারণায় বিশ্বাস করে।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=৮৭–৮৮}}{{sfn|উইলি|২০০৪|pp=২–৫}{{sfn|লং|২০১৩|pp=১২২–১২৫}} জৈন বিশ্বাসে, প্রধানত পুনর্জন্মের চক্রে চিরন্তন জীব অসংখ্য এবং "সিদ্ধ"-দের (মোক্ষপ্রাপ্ত) সংখ্যা নগন্য।{{sfn|হিরিয়ান্না|১৯৯৩|pp=১৫৭–১৫৮, ১৬৮–১৬৯}} জৈনধর্মের বিপরীতে হিন্দু দর্শন [[অদ্বৈতবাদ|অদ্বৈতবাদে]] বিশ্বাস করে। অদ্বৈত মতে, জীব ও [[ব্রহ্ম]] ভিন্ন নয়, বরং পরস্পর সংযুক্ত।{{sfn|হিরিয়ান্না|১৯৯৩|pp=৫৪–৬২, ৭৭–৮২, ১৩২}}{{sfn|পেরেট|২০১৩|pp=২৪৭–২৪৮}}{{sfn|বার্টলি|২০১৩|pp=১–১০, ৭৬–৭৯, ৮৭–৯৮}} |
|||
===অবনমন=== |
|||
হিন্দুধর্ম ও জৈনধর্মে আত্মার অস্তিত্বকে স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলে মনে করা হয়। অধিকাংশ হিন্দু দার্শনিক শাখায় আত্মাকে অবিনশ্বর, অনন্ত ও অপরিবর্তনীয় ("[[বিভু]]") মনে করা হয়; তবে কোনও কোনও আত্মাকে আণবিকও মনে করেন। আত্মা ও ব্রহ্ম বিষয়ক হিন্দু ধারণাটি সাধারণত আলোচিত হয় অদ্বৈত বা দ্বৈতবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে। অন্যদিকে জৈনধর্মে ব্রহ্মের অধিবিদ্যামূলক ধারণাটিকে খারিজ করা হয় এবং জৈন দর্শন মনে করে যে, আত্মা চিরপরিবর্তনশীল এবং প্রত্যেক জীবনকালে দেহ বা বস্তুর সঙ্গে আবদ্ধ, তদনুযায়ী একটি সীমায়িত আকার ধরে এক জীবন্ত সত্ত্বার সমগ্র শরীরে সঞ্চারিত হয়।{{sfn|জৈনি|১৯৯৮|pp=৫৮, ১০২–১০৫}} |
|||
==বিশ্বতত্ত্ব== |
|||
{{Expand section|date=সেপ্টেম্বর ২০২১}} |
|||
===কালচক্র=== |
|||
জৈনধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সাদৃশ্য প্রধানত বেদের প্রামাণিকতা ও ব্রহ্ম ধারণার অস্বীকারে। অন্যদিকে জৈনধর্ম ও হিন্দুধর্ম উভয়ের আত্মার অস্তিত্বকে স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলে গ্রহণ করে।{{sfn|দালাল|২০১০বি|pp=১৭৪–১৭৫}}{{sfn|সলোমন|হিগিননস|১৯৯৮|pp=১৮–২২}} জৈন ও হিন্দুদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক সুপ্রচলিত, বিশেষত ভারতের উত্তর, মধ্য ও পশ্চিমাঞ্চলে।{{sfn|জুয়েরগেনসমেয়ার|২০১১|p=৫৪}}{{sfn|কেল্টিং|২০০৯|pp=২০৬ টীকা ৪}} আদি ঔপনিবেশিক যুগের কয়েকজনের মত ছিল যে, বৌদ্ধধর্মের মতো জৈনধর্মও আংশিকভাবে হিন্দু বর্ণপ্রথার ফলে জাতিচ্যুত একটি শাখা।{{sfn|নেসফিল্ড|১৮৮৫|pp=১১৬–১১৭}}{{sfn|পোপ|১৮৮০|pp=৪০–৪১}} কিন্তু পরবর্তীকালের গবেষকেরা এটিকে পাশ্চাত্য গবেষকদের ভ্রান্তি বলেই স্বীকার করে নিয়েছেন।{{sfn|অ্যালবার্টস|২০০৭|pp=২৫৮–২৫৯}} জৈন সমাজের ইতিহাসে যে জাতিব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তার ভিত্তি মানুষের জন্ম ছিল না। বরং জৈনধর্ম মানুষের পরিবর্তনে মনোনিবেশ করেছিল, সমাজ পরিবর্তনে নয়।{{sfn|জুয়েরগেনসমেয়ার|২০১১|p=৫৪}}{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=১৪৭–১৪৯, ৩০৪ টীকা ২৪}}{{sfn|বাব|১৯৯৬|pp=১৩৭–১৪৫, ৫৪, ১৭২}}{{sfn|সানগেভ|১৯৮০|pp=৭৩, ৩১৬–৩১৭}}{{efn|[[রিচার্ড গমব্রিচ]] ও অন্যান্য গবেষকদের মতে বৌদ্ধধর্মও প্রাচীন বর্ণপ্রথা প্রত্যাখ্যান করেনি বা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেনি। এই ধর্মটিও পুনর্জন্ম ও দুঃখের হাত থেকে ব্যক্তির মুক্তির উপরেই দৃষ্টি আরোপ করেছিল। বহির্ভারতের বৌদ্ধ সমাজে ও সংঘগুলিতে বর্ণপ্রথার কথা নথিবদ্ধ হয়েছে। গমব্রিচ বলেছেন, "কোনও কোনও আধুনিকতাবাদী তো এতদূর পর্যন্ত বলেছেন যে বুদ্ধ সামগ্রিকভাবে বর্ণপ্রথার বিরুদ্ধে ছিলেন: কিন্তু কার্যত তা নয়, বরং [এটি] পাশ্চাত্য লেখকদের [রচনা থেকে] সংগৃহীত ভ্রান্তিগুলির একটি।" (মূল উদ্ধৃতি: "Some modernists go so far as to say that the Buddha was against caste altogether: this is not the case, but is one of the mistakes picked up from western authors."){{sfn|গমব্রিক|২০১২|pp=৩৪৪–৩৫৩ পাদটীকা সহ}}{{sfn|অ্যালবার্টস|২০১৭|pp=২৫৮–২৫৯}}{{sfn|ফ্লোরিডা|২০০৫|pp=১৩৪–১৩৭}}}} |
|||
==জৈন সম্প্রদায়== |
|||
{{Expand section|date=সেপ্টেম্বর ২০২১}} |
|||
===জনপরিসংখ্যান=== |
|||
তিন ধর্মেই সন্ন্যাসপ্রথার অস্তিত্ব রয়েছে।{{sfn|জনস্টন|২০০০|pp=৬৮১–৬৮৩}}{{sfn|ক্যালিয়াট|২০০৩এ|pp=৩০–৩৪ সঙ্গে পাদটীকা ২৮}} তিন ধর্মেই সন্ন্যাসপ্রথার নিয়ম, পদমর্যাদাক্রম, বর্ষাকালে [[চতুর্মাস্য]] ব্রতের নিয়ম এবং ব্রহ্মচর্যের নিয়ম একই।{{sfn|ক্যালিয়াট|২০০৩এ|pp=৩০–৩৪ সঙ্গে পাদটীকা ২৮ }} এগুলির উৎপত্তি মহাবীর বা বুদ্ধেরও পূর্বে।{{sfn|জনস্টন|২০০০|pp=৬৮১–৬৮৩}} জৈন ও হিন্দু সন্ন্যাসী সম্প্রদায় প্রথাগতভাবেই পরিযায়ী জীবন যাপন করে থাকেন, অন্যদিকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা সংঘের (মঠ) আশ্রয়ে থাকতে পছন্দ করেন এবং সংঘের প্রাঙ্গনেই বসবাস করেন।{{sfn|হিরাকাওয়া|১৯৯৩|pp=৪–৭}} বৌদ্ধ সন্ন্যাস প্রথায় সন্ন্যাসীদের সংঘের স্বাতন্ত্র্যসূচক রক্তাভ বস্ত্র ছাড়া বাইরে যেতে বা কাষ্ঠপাত্র ব্যবহার করতে বারণ করা হয়।{{sfn|জনস্টন|২০০০|pp=৬৮১–৬৮৩}} অপরপক্ষে জৈন সন্ন্যাসপ্রথায় সন্ন্যাসীদের হয় নগ্ন অবস্থায় (দিগম্বর সম্প্রদায়ে) অথবা শ্বেতবস্ত্র পরে (শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ে) থাকতে হয় এবং জৈন সন্ন্যাসীদের মধ্যে ভিক্ষাপাত্র হিসেবে কাষ্ঠপাত্র বা শুকনো লাউয়ের খোলা দিয়ে তৈরি শূন্য পাত্র ব্যবহারের বৈধতা আছে কিনা তা নিয়ে দ্বিমত আছে।{{sfn|জনস্টন|২০০০|pp=৬৮১–৬৮৩}}{{efn|জৈন সন্ন্যাসীদের বস্ত্র বা ভিক্ষাপাত্রের ন্যায় ভিক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরণ ন্যায্য বা বৈধ কিনা তা মোক্ষলাভের পথে এক প্রতিবন্ধকতা জ্ঞান করা হয়। জৈনধর্মের বিভিন্ন উপসম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদের এটি একটি প্রধান উপাদান থেকে যায় এবং দিগম্বর-শ্বেতাম্বর বিভাজনের জন্য এই বিবাদ অংশতভাবে দায়ী। যদিও বিভাজনের এই শিকড়টিকে শুধুমাত্র সন্ন্যাসীদের বস্ত্র ও ভিক্ষাপাত্রের মধ্যে বিভাজনের মধ্যে আবদ্ধ রাখলে সেটি হবে অতিমাত্রায় অতিসরলীকরণ।{{sfn|বালসারোউইকজ|২০১৫|pp=৪২–৪৩}}}} |
|||
===আচার-অনুষ্ঠান=== |
|||
হিন্দুদের মতো জৈনরাও মনে করে যে আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে হিংসা ন্যায্য<ref>"নিশীথভাষ্য" ("নিশীথসূত্র" গ্রন্থে) ২৮৯; জিনদত্ত সুরি: "উপদেশরসায়ন" ২৬; ডুন্ডাস পৃ. ১৬২–১৬৩; তাহতিনেন পৃ. ৩১</ref> এবং যে সৈন্য যুদ্ধে শত্রু বধ করে সে বৈধ কর্তব্যই পালন করে।<ref>জিন্দল পৃ. ৮৯–৯০; লেইডল পৃ. ১৫৪–১৫৫; জৈনি, পদ্মনাভ এস.: ''অহিংসা অ্যান্ড "জাস্ট ওয়ার" ইন জৈনিজম'', মূল গ্রন্থ: ''অহিংসা, অনেকান্ত অ্যান্ড জৈনিজম'', সম্পা. তারা শেঠিয়া, নতুন দিল্লি ২০০৪, পৃ. ৫২–৬০; তাহতিনেন পৃ. ৩১</ref> জৈন সম্প্রদায় নিজেদের আত্মরক্ষার বিষয়ে সামরিক শক্তির ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিয়েছিল। ইতিহাসে জৈন রাজন্যবর্গ, সেনানায়ক ও সৈনিকের উল্লেখও পাওয়া যায়।<ref>হরিসেন, "বৃহৎকথাকোষ" ১২৪ (১০ম শতাব্দী); জিন্দল পৃ. ৯০–৯১; সানগেভ পৃ. ২৫৯</ref> জৈন ও হিন্দু সম্প্রদায় প্রায়শই অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও পরস্পরের প্রতি অনুকুল ভাব পোষণ করে এসেছে। কোনও কোনও হিন্দু মন্দিরের প্রাঙ্গনে কোনও জৈন তীর্থংকরের মূর্তি সম্মানের সঙ্গে স্থান পেয়েছে।{{sfn|লং|২০০৯|pp=৫–৬}}{{sfn|শর্মা|ঘোষাল|২০০৬|pp=১০০–১০৩}} আবার [[বাদামি গুহামন্দিরসমূহ]] ও [[খাজুরাহো|খাজুরাহোর]] মন্দির চত্বরের মতো জায়গায় হিন্দু ও জৈন স্থাপত্য পাশাপাশিই গড়ে উঠেছিল।{{sfn|মিশেল|২০১৪|p=৩৮–৫২, ৬০–৬১}}{{sfn|রিং|ওয়াটসন|শেলিংগার|১৯৯৬|pp=৪৬৮–৪৭০}} |
|||
===সম্প্রদায় ও শাখা=== |
|||
দ্বাদশঅঙ্গ,জৈনকল্পসূত্র,জৈনভাগবতীসূত্র |
|||
== |
==শিল্পকলা ও স্থাপত্য== |
||
{{Main|জৈন শিল্পকলা}} |
|||
{{Expand section|date=সেপ্টেম্বর ২০২১}} |
|||
[[File:Detail of a leaf with the birth of mahavira.jpg|thumb|upright|মহাবীরের জন্ম, "[[কল্পসূত্র]]"-এর পুথিচিত্র (আনুমানিক ১৩৭৫-১৪০০ খ্রিস্টাব্দ)]] |
|||
==মতামত== |
|||
{{Multiple images |
|||
{{Expand section|date=সেপ্টেম্বর ২০২১}} |
|||
| image1 = "Sihanamdika ayagapata", Jain votive plate, Kankali Tila, Mathura dated 25-50 CE.jpg |
|||
===নেতিবাচক=== |
|||
| caption1 = [[অয়গপত|সিহনামদিক অগয়পত]], ২৫-৩০ খ্রিস্টাব্দ, [[কঙ্কালী টিলা]], মথুরা, [[উত্তরপ্রদেশ]] |
|||
| width1 = 135 |
|||
| image2 = KHANDAGIRI AND UDAYGIRI Cave Inscriptions 1.jpg |
|||
| caption2 = উদয়গিরি-খণ্ডগিরিতে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর একটি পাথর-কাটা গুহার অভিলিখনসমূহ, [[ওডিশা]]<ref>[http://asi.nic.in/asi_monu_tktd_orissa_udaigiricaves.asp উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি গুহাসমূহ] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20151029012248/http://asi.nic.in/asi_monu_tktd_orissa_udaigiricaves.asp |date=29 October 2015 }}, ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ, ভারত সরকার</ref> |
|||
| width2 = 188 |
|||
}} |
|||
ভারতীয় শিল্পকলা ও স্থাপত্যে জৈনধর্মের অবদান বেশ গুরুত্বপূর্ণ। জৈন শিল্পকলায় তীর্থংকর ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের জীবনের কিংবদন্তিগুলি প্রদর্শিত হয়ে থাকে। এর মধ্যে এঁদের দেখা যায় উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান অবস্থায় ধ্যানরত ভঙ্গিতে। তীর্থংকরদের রক্ষাকারী অনুচর আত্মা যক্ষ ও [[যক্ষিণী|যক্ষিণীদেরও]] তাঁদের মূর্তির সঙ্গে দেখা যায়।{{sfn|নাথুভাই শাহ|১৯৯৮|p=১৮৪}} আদিতম জ্ঞাত জৈন মূর্তিটি বর্তমানে [[পটনা]] জাদুঘরে রক্ষিত। এটি আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর মূর্তি।{{sfn|নাথুভাই শাহ|১৯৯৮|p=১৮৪}} পার্শ্বনাথের ব্রোঞ্জ মূর্তি রক্ষিত আছে মুম্বইয়ের প্রিন্স অফ ওয়েলস জাদুঘর ও পটনা জাদুঘরে; এগুলি খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে নির্মিত।{{sfn|উমাকান্ত পি. শাহ|১৯৮৭|p=৯৫}} |
|||
"অয়গপত" নামে এক ধরনের মানতপূর্তি ফলক প্রথম দিকের শতাব্দীগুলিতে জৈনধর্মে দান ও পূজার জন্য ব্যবহৃত হত। [[স্তুপ]], [[ধর্মচক্র]] ও [[ত্রিরত্ন|ত্রিরত্নের]] ন্যায় জৈন পূজার্চনার কেন্দ্রীয় বস্তু ও নকশা দ্বারা এই ফলকগুলি সজ্জিত থাকত। ভারতের [[উত্তরপ্রদেশ]] রাজ্যের [[মথুরা|মথুরার]] নিকট [[কঙ্কালী টিলা]] ইত্যাদি প্রাচীন জৈন ক্ষেত্রগুলিতে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের সময় এমন অসংখ্য প্রস্তরফলক আবিষ্কৃত হয়েছে। এই ধরনের ফলক দানের প্রথা নথিবদ্ধ হয়ে আছে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত।{{sfn|কিশোর|২০১৫|pp=১৭–৪৩}}{{sfn|জৈন|ফিশার|১৯৭৮|pp=৯–১০}} বিভিন্ন সত্ত্বাকে নিয়ে এককেন্দ্রীয়ভাবে উপবিষ্ট তীর্থংকরদের উপদেশসভা "[[সমবসরণ]]" জৈন শিল্পকলার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু।{{sfn|উইলি|২০০৯|p=১৮৪}} |
|||
===ইতিবাচক=== |
|||
[[রাজস্থান]] রাজ্যের [[কীর্তিস্তম্ভ|চিতোরের জৈন স্তম্ভ]] জৈন স্থাপত্যের একটি সুন্দর উদাহরণ।{{sfn|ওয়েন|২০১২বি|pp=১–২}} জৈন গ্রন্থাগারগুলিতে অলংকৃত পুথিগুলি রক্ষিত আছে। এগুলির মধ্যে জৈন বিশ্বতত্ত্ব রেখাচিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যাত হয়েছে।{{sfn|নাথুভাই শাহ|১৯৯৮|p=১৮৩}} অধিকাংশ চিত্র ও অলংকরণে "পঞ্চ কল্যাণক" নামে পরিচিত ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি চিত্রিত। এগুলি গৃহীত হয়েছিল তীর্থংকরদের জীবনকথা থেকে। প্রথম তীর্থংকর ঋষভনাথ চিত্রিত হয়ে থাকেন হয় পদ্মাসনে বা "কায়োৎসর্গ" (দণ্ডায়মান) ভঙ্গিতে। অন্য তীর্থংকরদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য তাঁর কাঁধ পর্যন্ত আলম্বিত কেশরাশিতে। তাঁর ভাস্কর্যের বৃষচিহ্নও খচিত থাকে।{{sfn|নাথুভাই শাহ|১৯৯৮|p=১১৩}} চিত্রকলায় তাঁর বিবাহ বা [[ইন্দ্র]] কর্তৃক তাঁর মস্তকে তিলক অঙ্কনের মতো জীবনের ঘটনাবলি চিত্রিত হয়েছে। অন্যান্য চিত্রে তাঁকে দেখা যায় অনুগামীদের মৃৎপাত্র উপহার দিতে; এছাড়াও তাঁকে দেখা গৃহ অঙ্কন করতে, তাঁত বুনতে এবং মাতা মারুদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।{{sfn|জৈন|ফিশার|১৯৭৮|p=১৬}} চব্বিশ জন তীর্থংকরের প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা প্রতীক ছিল; এগুলির তালিকা পাওয়া যায় "তিলোয়পন্নতি", "কহবালী" ও "প্রবচনসারোধার" ইত্যাদি গ্রন্থে।{{sfn|নাথুভাই শাহ|১৯৯৮|p=১৮৭}} |
|||
== পাদটীকা == |
|||
{{সূত্র তালিকা|২}} |
|||
===মন্দির=== |
|||
==তথ্যসূত্র== |
|||
{{Main|জৈন মন্দির}} |
|||
{{refbegin|2}} |
|||
{{প্রধান জৈন মন্দিরসমূহ}} |
|||
*{{Citation |
|||
জৈন মন্দিরকে বলা হয় "দেরাসর" বা "বসদি"।{{sfn|বাব|১৯৯৬|p=৬৬}} মন্দিরে থাকে তীর্থংকরদের মূর্তি। এই মূর্তিগুলির কয়েকটি প্রতিষ্ঠিত, কয়েকটি চালনীয়।{{sfn|বাব|১৯৯৬|p=৬৬}} মন্দিরের দু’টি অংশ থাকে: গর্ভগৃহ ও নাটমন্দির। এর মধ্যে তীর্থংকর মূর্তি থাকে গর্ভগৃহে।{{sfn|বাব|১৯৯৬|p=৬৬}} মূর্তিগুলির একটিকে বলা হয় "মূলনায়ক" (প্রধান দেবতা)।{{sfn|বাব|১৯৯৬|p=৬৮}} জৈন মন্দিরগুলির সম্মুখে প্রায়শই "[[মানস্তম্ভ]]" (সম্মানের স্তম্ভ) নামে একটি স্তম্ভ নির্মাণ করা হয়।{{sfn|সেটার|১৯৮৯|p=১৯৫}} মন্দির নির্মাণ করাকে এক পুণ্যকর্ম জ্ঞান করা হয়।{{sfn|সানগেভ|২০০১|p=১৮৮}} |
|||
|last=Aïnouche |
|||
|first=Linda |
|||
প্রাচীন জৈন স্মারকগুলির অন্যতম হল [[মধ্যপ্রদেশ|মধ্যপ্রদেশের]] ভেলসার ([[বিদিশা]]) কাছে উদয়গিরি পাহাড়, [[মহারাষ্ট্র|মহারাষ্ট্রে]] [[ইলোরা গুহাসমূহ|ইলোরা]], [[গুজরাত|গুজরাতে]] [[পালিতানা মন্দিরসমূহ|পালিতানা মন্দিরসমূহ]] এবং [[রাজস্থান|রাজস্থানে]] [[আবু পর্বত|আবু পর্বতের]] কাছে দিলওয়াড়ার জৈন মন্দিরসমূহ।<ref>{{citation |last=বারিক |first=বিভূতি |title=প্ল্যান টু বিউটিফাই খণ্ডগিরি – মনুমেন্ট রিভ্যাম্প টু অ্যাট্র্যাক্ট মোর ট্যুরিস্টস |url=http://www.telegraphindia.com/1150623/jsp/odisha/story_27206.jsp |work=[[দ্য টেলিগ্রাফ (কলকাতা)|দ্য টেলিগ্রাফ]] |date=22 June 2015 |location=[[ভুবনেশ্বর]] |access-date=16 February 2016 |archive-url=https://web.archive.org/web/20160223232545/http://www.telegraphindia.com/1150623/jsp/odisha/story_27206.jsp |archive-date=23 February 2016 |url-status=live |df=dmy-all }}</ref> [[রণকপুর|রণকপুরের]] [[রণকপুর জৈন মন্দির|চৌমুখ মন্দিরটিকে]] সুন্দরতম জৈন মন্দিরগুলির একটি বলে বিবেচনা করা হয়। এই মন্দিরটি বিস্তারিত খোদাইচিত্রের জন্য বিখ্যাত।{{sfn|সহদেব কুমার|২০০১|p=১০৬}} জৈন ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী, [[শিখরজি|শিখরজিতে]] চব্বিশজন জৈন তীর্থংকরের মধ্যে কুড়ি জন এবং অন্যান্য অনেক সাধু মোক্ষ লাভ করেছিলেন (অর্থাৎ পুনর্জন্ম ব্যতিরেকে দেহত্যাগ করেছিলেন এবং তাঁদের আত্মা [[সিদ্ধশীল|সিদ্ধশীলে]] প্রবেশ করেছিল)। উত্তরপূর্ব ঝাড়খণ্ডে অবস্থিত [[শিখরজি]] তাই একটি তীর্থস্থান হিসেবে গণ্য হয়।{{Sfn|কর্ট|২০১০|pp=১৩০–১৩৩}}{{efn|কোনও কোনও গ্রন্থে এই স্থানটিকে সম্মেত পর্বত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।{{sfn|জেকবি|১৯৬৪|p=২৭৫}}}} শ্বেতাম্বর মূর্তিপূজক সম্প্রদায়ের কাছে পবিত্রতম পুণ্যস্থান হল পালিতানা মন্দিরসমূহ।{{sfn|বার্জার|২০১০|p=৩৫২}} শিখরজির সঙ্গে দু’টি ক্ষেত্রকে [[জৈন সমাজ]] সকল তীর্থস্থানের মধ্যে পবিত্রতম মনে করেন।<ref>{{citation|url=http://philtar.ucsm.ac.uk/encyclopedia/jainism/murti.html |title="মূর্তিপূজকস, জৈনিজম", ''এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়নস'' (ফিলটার), ক্যামব্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয় |url-status=dead |archiveurl=https://web.archive.org/web/20071013131021/http://philtar.ucsm.ac.uk/encyclopedia/jainism/murti.html |archivedate=13 October 2007 |df= }}</ref> [[জৈন চত্বর, খাজুরাহো|খাজুরাহোর জৈন চত্বর]] ও [[পাট্টাডাকাল#জৈন মন্দির|জৈন নারায়ণ মন্দির]] একটি [[ইউনেস্কো]] [[বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান|বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের]] অংশ।<ref>{{citation |url= https://whc.unesco.org/en/list/240 |title= খাজুরাহো গ্রুপ অফ মনুমেন্টস |publisher= ইউনেস্কো |access-date= 14 March 2017 |archive-url= https://web.archive.org/web/20170218144204/https://whc.unesco.org/en/list/240/ |archive-date= 18 February 2017 |url-status=live |df= dmy-all }}</ref><ref>{{citation |url= https://whc.unesco.org/en/list/239 |title= গ্রুপ অফ মনুমেন্টস অ্যাট পাট্টাডাকাল |publisher= ইউনেস্কো |access-date= 14 March 2017 |archive-url= https://web.archive.org/web/20140326134122/https://whc.unesco.org/en/list/239 |archive-date= 26 March 2014 |url-status=live |df= dmy-all }}</ref> [[শ্রবণবেলগোলা]], [[সাবীর কম্বড বসদি]] বা সহস্র স্তম্ভ ও [[ব্রহ্মা জিনালয়]] হল [[কর্ণাটক|কর্ণাটকের]] গুরুত্বপূর্ণ জৈন কেন্দ্র।{{sfn|বুতালিয়া|স্মল|২০০৪|p=৩৬৭}}{{sfn|ফার্গুসন|১৮৭৬|p=২৭১}}{{sfn|পাণ্ড্য|২০১৪|p=১৭}} [[মাদুরাই|মাদুরাইয়ের]] আশেপাশে ২৬টি গুহা, ২০০টি প্রস্তরবেদি, ৬০টি অভিলিখন এবং শতাধিক ভাস্কর্য পাওয়া গিয়েছে।<ref>{{citation |author=এস. এস. কবিতা |url=http://www.thehindu.com/life-and-style/namma-madurai-history-hidden-inside-a-cave/article4051011.ece |title=নাম্মা মাদুরাই: হিস্ট্রি হিডেন ইনসাইড আ কেভ |work=[[দ্য হিন্দু]] |date=31 October 2012 |access-date=15 November 2013 |archive-url=https://web.archive.org/web/20140103053626/http://www.thehindu.com/life-and-style/namma-madurai-history-hidden-inside-a-cave/article4051011.ece |archive-date=3 January 2014 |url-status=live |df=dmy-all }}</ref> |
|||
|title=Le don chez les Jaïns en Inde |
|||
|url=http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=37236 |
|||
খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয়-প্রথম শতাব্দীর উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি গুহাসমূহ তীর্থংকর ও দেবদেবীদের খোদাইচিত্রে এবং [[হাতিগুম্ফা শিলালিপি]] সহ একাধিক শিলালিপিতে সমৃদ্ধ।<ref>{{citation |url=http://www.proel.org/index.php?pagina=alfabetos/dravidi |title=সোর্স |work=proel.org |access-date=13 January 2019 |archive-url=https://web.archive.org/web/20181201132912/http://www.proel.org/index.php?pagina=alfabetos%2Fdravidi |archive-date=1 December 2018 |url-status=live |df=dmy-all }}</ref>{{sfn|উপিন্দর সিং|২০১৬|p=৪৬০}} [[বাদামি গুহামন্দিরসমূহ|বাদামি]], [[মাঙ্গি-টুঙ্গি]] ও ইলোরা গুহাসমূহের জৈন গুহা মন্দিরগুলিকেও গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয়।{{sfn|ওয়েন|২০১২বি|p=৫০}} [[সিট্টনবসল গুহা]] মন্দিরটি জৈন শিল্পকলার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এর মধ্যে একটি আদিযুগীয় গুহাবাস এবং অজন্তার সঙ্গে তুলনীয় উন্নতমানের সদ্যোরঙ্গ (ফ্রেস্কো) চিত্র সহ মধ্যযুগীয় পাথরে কাটা মন্দির পাওয়া গিয়েছে। গুহার ভিতরে রয়েছে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর [[তামিল-ব্রাহ্মী]] অভিলিখন সহ সতেরোটি প্রস্তরবেদি।<ref>{{citation |author=এস. এস. কবিতা |url=http://www.thehindu.com/features/metroplus/preserving-the-past/article100194.ece |title=প্রিজার্ভিং দ্য পাস্ট |work=[[দ্য হিন্দু]] |date=3 February 2010 |access-date=15 November 2013 |archive-url=https://web.archive.org/web/20140103060244/http://www.thehindu.com/features/metroplus/preserving-the-past/article100194.ece |archive-date=3 January 2014 |url-status=live |df=dmy-all }}</ref> খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর [[কালুগুমলই জৈন বেদিসমূহ|কাঝুগুমলই মন্দির]] দক্ষিণ ভারতে জৈনধর্মের পুনরুজ্জীবনের স্মৃতি বহন করে।<ref>{{citation |url=http://www.hindu.com/2003/09/15/stories/2003091503060500.htm |title=আরিট্টপট্টি ইন্সক্রিপশন থ্রোজ লাইট অন জৈনিজম |work=[[দ্য হিন্দু]] |date=15 September 2003 |access-date=15 November 2013 |archive-url=https://web.archive.org/web/20131123051449/http://www.hindu.com/2003/09/15/stories/2003091503060500.htm |archive-date=23 November 2013 |url-status=live |df=dmy-all }}</ref> |
|||
|year=2012 |
|||
|publisher=L'Harmattan |
|||
<gallery mode="packed" caption="ভারতে ও বহির্ভারতে বিভিন্ন শৈলীর জৈন মন্দির"> |
|||
|isbn=978-2-296-57019-1 |
|||
File:Jain Temple Ranakpur.jpg|[[রণকপুর জৈন মন্দির]] |
|||
File:Delwada.jpg|[[দিলওয়াড়া মন্দিরসমূহ]] |
|||
File:Le temple de Parshvanath (Khajuraho) (8638423582).jpg|[[পার্শ্বনাথ মন্দির, খাজুরাহো]] |
|||
File:Jain temples on Girnar mountain aerial view.jpg|[[গিরনার জৈন মন্দিরসমূহ]] |
|||
File:Jal Mandir.The Jain Temple at Pawapur,.jpg|[[জল মন্দির]], [[পাওয়াপুরী]] |
|||
File:Lodurva Temples.jpg|[[লোধ্রুব|লোধ্রুব জৈন মন্দির]] |
|||
File:Templejaindanvers.jpg|[[বেলজিয়ামে জৈন মন্দির|জৈন মন্দির]], [[অ্যান্টওয়ের্পট]], [[বেলজিয়াম]] |
|||
<!--Please DO NOT add any more images here, there are QUITE enough already, thanks!--> |
|||
</gallery> |
|||
=== তীর্থ === |
|||
{{Main|তীর্থ (জৈনধর্ম)}} |
|||
[[File:Shikharji Parasnath Giridih.jpg|thumb|upright|[[শিখরজি]]]] |
|||
জৈন তীর্থক্ষেত্রগুলি নিম্নোক্ত শ্রেণিগুলিতে বিভক্ত:{{sfn|টিৎজে|১৯৯৮|p=}} |
|||
* সিদ্ধক্ষেত্র{{snds}}যে-সকল ক্ষেত্রকে কোনও এক অরিহন্ত (কেবলিন্) বা তীর্থংকরের [[মোক্ষ (জৈনধর্ম)|মোক্ষ]] লাভের স্থান বলে মনে করা হয়। যেমন: [[কৈলাস পর্বত|অষ্টপদ]], [[শিখরজি]], [[গিরনার]], [[পাওয়াপুরী]], [[পালিতানা]], [[মাঙ্গি-তুঙ্গি]] ও [[চম্পাপুরী]] ([[অঙ্গ (রাজ্য)|অঙ্গের]] রাজধানী)। |
|||
* অতিশয়ক্ষেত্র{{snds}}যে-সকল ক্ষেত্রকে দৈব ঘটনাস্থল বলে মনে করা হয়। যেমন: [[মহাবীরজি]], [[ঋষভদেও]], [[কুন্দলপুর]], [[তিজারা জৈন মন্দির|তিজারা]] ও [[আহারজি]]। |
|||
* পুরাণক্ষেত্র{{snds}যে-সকল ক্ষেত্রে মহাপুরুষেরা বাস করেছিলেন। যেমন: [[অযোধ্যা]], [[বিদিশা]], [[হস্তিনাপুর]] ও [[রাজগির]]। |
|||
* জ্ঞানক্ষেত্র{{snds}}যে-সকল ক্ষেত্র বিশিষ্ট আচার্যদের স্মৃতিধন্য বা শিক্ষাকেন্দ্র। যেমন: [[শ্রবণবেলগোলা]]। |
|||
[[পাকিস্তান|পাকিস্তানের]] [[সিন্ধুপ্রদেশ|সিন্ধুপ্রদেশে]] জৈন সম্প্রদায় [[নগরপকর জৈন মন্দির|নগরপকর জৈন মন্দিরটি]] নির্মাণ করেছিল। যদিও একটি ইউনেস্কো আপাত-স্থিরীকৃত বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান আবেদন অনুযায়ী, নগরপকর জৈনধর্মের একটি "প্রধান ধর্মীয় কেন্দ্র বা তীর্থস্থান" নয়, কিন্তু "১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর সর্বশেষ জৈন ধর্মাবলম্বীরা [পাকিস্তান] ত্যাগ করার" পূর্বাবধি এক সময় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র ছিল।<ref>[https://whc.unesco.org/en/tentativelists/6111/ নগরপকর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20170510093259/https://whc.unesco.org/en/tentativelists/6111/ |date=10 May 2017 }}, আপাত-স্থিরীকৃত তালিকা, বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী কেন্দ্র</ref> |
|||
===মূর্তি ও ভাস্কর্য=== |
|||
{{Main|জৈন ভাস্কর্য}} |
|||
[[File:Thirthankara Suparshvanath Museum Rietberg RVI 306.jpg|thumb|upright|তীর্থংকর [[সুপার্শ্বনাথ|সুপার্শ্বনাথের]] একটি মূর্তি]] |
|||
জৈন ভাস্কর্যে সাধারণত চব্বিশজন তীর্থংকরের কোনও না কোনও একজনকে দেখা যায়। এঁদের মধ্যে পার্শ্বনাথ, ঋষভনাথ ও মহাবীর অধিকতর জনপ্রিয়। এঁদের প্রায়ই [[পদ্মাসন]] বা "কায়োৎসর্গ" ভঙ্গিতে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখা যায়। এঁরা ছাড়া অরিহন্ত, [[বাহুবলী]] ও [[অম্বিকা (জৈনধর্ম)|অম্বিকার]] ন্যায় রক্ষয়িত্রী দেবদেবীরাও জনপ্রিয়।{{sfn|আরোরা|২০০৭|p=৪০৫}} চতুর্পাক্ষিক মূর্তিগুলিও জনপ্রিয়। তীর্থংকর মূর্তিগুলি একই রকম দেখতে, এগুলিকে শুধু প্রত্যেক তীর্থংকরের পৃথক পৃথক প্রতীক দ্বারা চিহ্নিত করা যায়। ব্যতিক্রম শুধুই পার্শ্বনাথ। তাঁর মূর্তিতে একটি সর্পখচিত মুকুট দেখা যায়। দিগম্বর সম্প্রদায়ের মূর্তিগুলিও নগ্ন এবং অনাড়ম্বর; অন্যদিকে শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের মূর্তিগুলি বস্ত্রাবৃত এবং সুসজ্জিত অবস্থায় থাকে।{{sfn|কর্ট|২০১০|p=১৮৪}} |
|||
অধুনা [[কর্ণাটক]] রাজ্যের [[শ্রবণবেলগোলা|শ্রবণবেলগোলার]] একটি পর্বতচূড়ায় ৯৮১ খ্রিস্টাব্দে [[পশ্চিম গঙ্গ রাজবংশ|গঙ্গ]] মন্ত্রী ও সেনানায়ক [[চবুন্দরায়]] বাহুবলী [[গোমতেশ্বর|গোমতেশ্বরের]] {{convert|18|m|ft|adj=on|abbr=off}} দীর্ঘ একশিলা মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন। ''[[দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া]]'' কর্তৃক আয়োজিত একটি এসএমএস সমীক্ষায় এটি ভারতের সাত আশ্চর্যের মধ্যে প্রথম হিসেবে বিবেচিত হয়। |
|||
<ref>{{citation |url=http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/2256323.cms |title=অ্যান্ড ইন্ডিয়া’জ ৭ ওয়ান্ডারস আর |newspaper=[[দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া]] |date=5 August 2007 |access-date=3 January 2013 |archive-url=https://web.archive.org/web/20121018033432/http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/2256323.cms |archive-date=18 October 2012 |url-status=live |df=dmy-all }}</ref> ২০১৫ সালে [[মহারাষ্ট্র|মহারাষ্ট্রের]] [[নাসিক জেলা|নাসিক জেলায়]] {{convert|33|m|ft|abbr=on}} দীর্ঘ [[অহিংসার মূর্তি]] (ঋষভনাথের মূর্তি) নির্মিত হয়।<ref>{{citation |url=http://timesofindia.indiatimes.com/city/nashik/70-crore-plan-for-idol-installation-at-Mangi-Tungi/articleshow/50037188.cms |title=৭০-ক্রোড় প্ল্যান ফর আইডল ইনস্টলেশন অ্যাট মাঙ্গি-টুঙ্গি|work=[[দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া]] |date=4 December 2015 |last=বোটেকর |first=অভিলাষ |agency=টিএনএন |location=[[নাসিক]] |access-date=7 February 2016 |archive-url=https://web.archive.org/web/20160119161127/http://timesofindia.indiatimes.com/city/nashik/70-crore-plan-for-idol-installation-at-Mangi-Tungi/articleshow/50037188.cms |archive-date=19 January 2016 |url-status=live |df=dmy-all }}</ref> জৈনদের মূর্তি প্রায়শই নির্মিত হয় [[অষ্টধাতু]], [[আকোটা ব্রোঞ্জ]], [[পিতল]], [[সোনা]], [[রুপো]], [[একশিলা]], [[পাথর-খোদাই]] ও মূল্যবান পাথরে।{{sfn|প্রতাপাদিত্য পাল|১৯৮৬|p=২২}}<ref>{{Citation|url=http://www.metmuseum.org/toah/hd/jais/hd_jais.htm|title=মেট মিউজিয়াম|access-date=16 April 2017|archive-url=https://web.archive.org/web/20170506060348/http://www.metmuseum.org/toah/hd/jais/hd_jais.htm|archive-date=6 May 2017|url-status=live|df=dmy-all}}</ref> |
|||
=== প্রতীক === |
|||
{{Main|জৈন প্রতীক}} |
|||
{{Multiple image |
|||
| image1 = Om jaïn orange.svg |
|||
| caption1 = [[ওঁ#জৈনধর্ম|জৈনধর্মে ওঁ]] |
|||
| width1 = 90 |
|||
| image2 = Jain flag.jpg |
|||
| caption2 = [[জৈন পতাকা]] |
|||
| width2 = 169 |
|||
}} |
}} |
||
জৈন মূর্তি ও শিল্পকলার মধ্যে স্বস্তিক [[ওঁ#জৈনধর্ম|ওঁ]] ও "অষ্টমঙ্গল" জাতীয় প্রতীকচিহ্নগুলি দেখা যায়। জৈনধর্মে "ওঁ" প্রতীকটি পঞ্চ-পরমেষ্ঠির (অরিহন্ত, [[অশিরি]], [[আচার্য]], [[উপজ্ঝয়]] ও মুনি) আদ্যক্ষরের ("অ-অ-আ-উ-ম") সমষ্টি মনে করা হয়।<ref>{{citation |url=http://www.cs.colostate.edu/~malaiya/om.html |title=ওঁ – সিগনিফিকেন্স ইন জৈনিজম, ল্যাঙ্গুয়েজেস অ্যান্ট স্ক্রিপ্টস অফ ইন্ডিয়া , কলোরাডো রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়|work=cs.colostate.edu }}</ref>{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|pp=৪১০–৪১১}} আবার এই "ওঁ" প্রতীকটি এই ধর্মের "[[ণমোকার মন্ত্র|ণমোকার মন্ত্রের]]" পাঁচ পংক্তির আদ্যক্ষরেরও সমষ্টি বটে।{{Sfn|আগরওয়াল|২০১২|p=১৩৫}}{{Sfn|আগরওয়াল|২০১৩|p=৮০}} "[[অষ্টমঙ্গল]]" হল আটটি পবিত্র প্রতীকের সমন্বয়ায়িত রূপ।{{sfn|টিৎজে|১৯৯৮|p=২৩৪}} দিগম্বর সম্প্রদায়ে এগুলি হল [[ছত্র]], [[ধ্বজ]], [[কলস]], [[চামর]], [[দর্পণ]], আসন, [[হাতপাখা]] ও পাত্র। শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ে এগুলি হল স্বস্তিক, "[[শ্রীবৎস]]", "[[নন্দাবর্ত]]", "বর্ধমানক" (খাদ্যপাত্র), "ভদ্রাসন" (আসন), [[কলস]], দর্পণ ও জোড়া মাছ।{{Sfn|টিৎজে|১৯৯৮|p=২৩৪}} |
|||
*{{Citation |
|||
|last=Cort |
|||
চক্রের উপর করতলের চিহ্নটি [[জৈনধর্মে অহিংসা|অহিংসার]] প্রতীক। এখানে চক্রটি [[ধর্মচক্র|ধর্মচক্রের]] প্রতীক, যা অবিশ্রান্তভাবে অহিংসা নীতি অনুসরণের মাধ্যমে সংসার চক্রে পরিভ্রমণ বন্ধ হওয়ার দ্যোতক। [[জৈন পতাকা|জৈন পতাকার]] পাঁচটি রং একাধারে [[পঞ্চ-পরমেষ্ঠি]] ও পঞ্চ প্রতিজ্ঞার প্রতীক।{{sfn|বিজয় কে. জৈন|২০১২|p=চার}} [[স্বস্তিক]] চিহ্নের চারটি বাহু জৈনধর্ম মতে পুনর্জন্মের ক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত চার ধরনের জীবের প্রতীক: মাববসত্ত্বা, দেবসত্ত্বা, নারকীয় সত্ত্বা ও মানবেতর সত্ত্বা।{{sfn|কর্ট|২০০১এ|p=১৭}}{{sfn|জান্সমা|জৈন|২০০৬|p=১২৩}} স্বস্তিকের উপর তিনটি বিন্দু প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলিতে বর্ণিত আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অত্যাবশ্যক রত্নত্রয়ের (সম্যক দর্শন, সম্যক জ্ঞান, সম্যক চরিত্র) প্রতীক।{{sfn|কর্ট|২০০১এ|pp=১৭–১৮}} |
|||
|first=John E. |
|||
|title=The Jain Knowledge Warehouses : Traditional Libraries in India |
|||
১৯৭৪ সালে মহাবীরের নির্বাণের ২৫০০ বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে জৈন সমাজ তাদের ধর্মের জন্য একক একটি সমন্বিত প্রতীক গ্রহণ করে।{{Sfn|রবিনসন|২০০৬|p=২২৫}} এই প্রতীকে তিন লোক (স্বর্গ, মানবলোক ও নরক) প্রদর্শিত হয়। সর্বোপরি অর্ধ-চক্রাকার অংশটি ছিল তিন লোকের উর্ধ্বে অবস্থিত সিদ্ধশীলের প্রতীক। জৈন স্বস্তিক ও অহিংসার চিহ্নটিও অন্তর্ভুক্ত হয়; সেই সঙ্গে হয় ''[[পরস্পরোপগ্রহো জীবানাম]]'' এই জৈন মন্ত্রটিও।{{sfn|সানগাভে|২০০১|p=১২৩}} এই মন্ত্রটি গৃহীত হয়েছিল উমাস্বাতী রচিত "তত্ত্বার্থসূত্র" গ্রন্থের ৫.২১ সংখ্যক সূত্র থেকে। এটির অর্থ হল "আত্মাগণ একে অপরের সেবায় আত্মনিয়োগ করুক"।{{sfn|ভ্যালেলি|২০১৩|p=৩৫৮}} |
|||
|journal=Journal of the American Oriental Society |
|||
|volume=115 |
|||
==ইতিহাস== |
|||
|issue=1 |
|||
{{Main|জৈনধর্মের ইতিহাস}} |
|||
|year=1995 |
|||
[[File:Photo of lord adinath bhagwan at kundalpur.JPG|thumb|upright|[[ঋষভনাথ]], মনে করা হয় তিনি ১০<sup>১৬৩১</sup> বছর আগে জীবিত ছিলেন; তাঁকেই প্রথাগতভাবে জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মনে করা হয়।]] |
|||
|doi=10.2307/605310 |
|||
===প্রাচীন যুগ=== |
|||
|page=77|jstor=605310 |
|||
{{See also|জৈনধর্মের কালরেখা|শ্রমণ}} |
|||
{{Multiple images |
|||
| image1 = Ashoka Pillar at Feroze Shah Kotla, Delhi 03.JPG |
|||
| caption1 = অশোকের জৈন অভিলিখন (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২৩৬ অব্দ) |
|||
| width1 = 157 |
|||
| image2 = Shrine with Four Jinas (Rishabhanatha (Adinatha)), Parshvanatha, Neminatha, and Mahavira) LACMA M.85.55 (1 of 4).jpg |
|||
| caption2 = চার জিনের (ঋষভনাথ (আদিনাথ), পার্শ্বনাথ, নেমিনাথ ও মহাবীর) ''চৌমুখ'' ভাস্কর্য, [[ল্যাকমা]]ম খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী |
|||
| width2 = 166 |
|||
}} |
}} |
||
{{Multiple images |
|||
*{{citation |
|||
| image1 = Udayagiri Caves - Rani Gumpha 01.jpg |
|||
|last=Dundas |
|||
| caption1 = খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে [[মহামেঘবাহন রাজবংশ|মহামেঘবাহন সাম্রাজ্যের]] রাজা [[খরবেল]] কর্তৃক নির্মিত [[উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি গুহাসমূহ]] |
|||
|first=Paul |
|||
| width1 = 160 |
|||
|title=The Jains |
|||
| image2 = La grotte Jain Indra Sabha Ellora Caves, India.jpg |
|||
|url=http://books.google.com/books?id=jdjNkZoGFCgC |
|||
| caption2 = [[ইলোরা গুহাসমূহ|ইলোরা গুহাসমূহে]] ইদ্রসভা গুহা। এটি হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মেরও স্মারক-সম্বলিত। |
|||
|year=2002 |
|||
| width2 = 160 |
|||
|publisher=Routledge |
|||
| align = |
|||
|isbn=978-0-415-26605-5}} |
|||
| direction = |
|||
*{{citation |
|||
| total_width = |
|||
|last=Glasenapp |
|||
| alt1 = |
|||
|first=Helmuth Von |
|||
| width = |
|||
|title=Jainism: An Indian Religion of Salvation |
|||
| Kalagumalai = https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Kazhugumalai_Jain_beds_(8).jpg |
|||
|year=1999 |
|||
|location = Delhi |
|||
|publisher=Motilal Banarsidass |
|||
|url=http://books.google.co.in/books/about/Jainism.html?id=WzEzXDk0v6sC |
|||
|isbn=81-208-1376-6}} |
|||
*{{citation |
|||
|title=Jaina Sutras Part I |
|||
|series=Sacred Books of the East |
|||
|volume=22 |
|||
|url=http://www.sacred-texts.com/jai/sbe22/index.htm |
|||
|first=Hermann |
|||
|last=Jacobi |
|||
|year=1884 |
|||
|ref=harv}} |
|||
*{{citation |
|||
|last1=Jain |
|||
|first1=Jyotindra |
|||
|last2=Fischer |
|||
|first2=Eberhard |
|||
|title=Jaina Iconography |
|||
|url=http://books.google.com/books?id=mbXwopoqITIC |
|||
|year=1978 |
|||
|publisher=Brill Publishers |
|||
|isbn=978-90-04-05259-8}} |
|||
*{{citation |
|||
|last=Jain |
|||
|first=Kailash Chand |
|||
|title=Lord Mahāvīra and His Times |
|||
|url=http://books.google.com/books?id=8-TxcO9dfrcC&pg=PA17 |
|||
|accessdate=28 June 2013 |
|||
|year=1991 |
|||
|publisher=Motilal Banarsidass |
|||
|isbn=978-81-208-0805-8 |
|||
|page=17}} |
|||
*{{citation |
|||
| last =Jain, Mahavir Saran | title =The Doctrine of Karma in Jain Philosophy |url=http://www.herenow4u.net/index.php?id=98353}} |
|||
*{{citation | last =Jain, Mahavir Saran | title =The Path to Attain Liberation in Jain Philosophy | url =http://www.scribd.com/doc/219047226/The-Path-to-Attain-Liberation-in-Jain-Philosophy | সংগ্রহের-তারিখ =৯ জুলাই ২০১৫ | আর্কাইভের-তারিখ =৩১ মে ২০১৫ | আর্কাইভের-ইউআরএল =https://web.archive.org/web/20150531013119/https://www.scribd.com/doc/219047226/The-Path-to-Attain-Liberation-in-Jain-Philosophy | ইউআরএল-অবস্থা =অকার্যকর }} |
|||
*{{citation |
|||
| last =Jain, Mahavir Saran | title = Bhagwaan Mahaveer Evam Jain Darshan |
|||
|url=http://www.herenow4u.net/index.php?id=98353}} |
|||
*{{citation |
|||
|last=Jaini |
|||
|first=Padmanabh S. |
|||
|title=Gender and Salvation: Jaina Debates on the Spiritual Liberation of Women |
|||
|url=http://books.google.com/books?id=GRA-uoUFz3MC |
|||
|accessdate=10 January 2013 |
|||
|year=1991 |
|||
|publisher=University of California |
|||
|isbn=978-0-520-06820-9 |
|||
|ref=harv}} |
|||
*{{citation |
|||
|last=Jaini |
|||
|first=Padmanabh S. |
|||
|title=The Jaina Path Of Purification |
|||
|url=http://books.google.com/books?id=wE6v6ahxHi8C |
|||
|accessdate=10 January 2013 |
|||
|year=1998 |
|||
|publisher=Motilal Banarsidass |
|||
|isbn=978-81-208-1578-0 |
|||
|ref=harv}} |
|||
*{{citation |
|||
|last=Jaini |
|||
|first=Padmanabh S. |
|||
|title=Collected Papers On Jaina Studies |
|||
|url=http://books.google.com/books?id=HPggiM7y1aYC |
|||
|accessdate=10 January 2013 |
|||
|year=2000 |
|||
|publisher=Motilal Banarsidass |
|||
|isbn=978-81-208-1691-6 |
|||
|ref=harv}} |
|||
*{{Citation |
|||
|last=Koller |
|||
|first=John M. |
|||
|title=Syādvadā as the Epistemological Key to the Jaina Middle Way Metaphysics of Anekāntavāda |
|||
|journal=Philosophy East and West |
|||
|volume=50 |
|||
|issue=3 |
|||
|location=Honululu |
|||
|issn=00318221 |
|||
|date=July 2000 |
|||
|doi=10.1353/pew.2000.0009 |
|||
|jstor=1400182 |
|||
|page=628}} |
|||
*{{citation |
|||
|last=Rankin |
|||
|first=Aidan |
|||
|title=Many-Sided Wisdom: A New Politics of the Spirit |
|||
|url=http://books.google.com/books?id=zoxR-LdZy0MC |
|||
|year=2010 |
|||
|publisher=John Hunt Publishing |
|||
|isbn=978-1-84694-277-8}} |
|||
*{{citation |
|||
|last=Sangave |
|||
|first=Vilas Adinath |
|||
|title=Jaina Community |
|||
|url=http://books.google.com/books?id=FWdWrRGV_t8C |
|||
|year=1980 |
|||
|publisher=Popular Prakashan |
|||
|location=Bombay |
|||
|edition=2nd |
|||
|isbn=978-0-317-12346-3}} |
|||
*{{citation |
|||
|last=Sangave |
|||
|first=Vilas Adinath |
|||
|title=Facets of Jainology: Selected Research Papers on Jain Society, Religion, and Culture |
|||
|url=http://books.google.com/books?id=QzEQJHWUwXQC |
|||
|year=2001 |
|||
|publisher=Popular Prakashan |
|||
|location=Mumbai |
|||
|isbn=978-81-7154-839-2}} |
|||
*{{citation |
|||
|last=Sangave |
|||
|first=Vilas Adinath |
|||
|title=Aspects of Jaina religion |
|||
|url=http://books.google.com/books?id=8UhvGRoyAqMC |
|||
|edition=5 |
|||
|year=2006 |
|||
|publisher=Bharatiya Jnanpith |
|||
|isbn=978-81-263-1273-3}} |
|||
*{{citation |
|||
|last=Shah |
|||
|first=Natubhai |
|||
|title=Jainism: The World of Conquerors |
|||
|url=http://books.google.com/books?id=EmVzvUzbwegC |
|||
|volume=1 |
|||
|year=1998a |
|||
|publisher=Sussex Academic Press |
|||
|isbn=978-1-898723-30-1}} |
|||
*{{citation |
|||
|last=Shah |
|||
|first=Natubhai |
|||
|title=Jainism: The World of Conquerors |
|||
|url=http://books.google.com/books?id=g120RG8GkHAC |
|||
|volume=2 |
|||
|year=1998b |
|||
|publisher=Sussex Academic Press |
|||
|isbn=978-1-898723-31-8}} |
|||
*{{citation |
|||
|last=Shah |
|||
|first=Umakant P. |
|||
|title=Jaina-Rupa-Mandana |
|||
|url=http://books.google.com/books?id=m_y_P4duSXsC |
|||
|year=1987 |
|||
|publisher=Abhinav Publications |
|||
|isbn=978-81-7017-208-6}} |
|||
*{{citation |
|||
|last=Sethia |
|||
|first=Tara |
|||
|title=Ahiṃsā, Anekānta and Jainism |
|||
|url=http://books.google.com/books?id=QYdlKv8wBiYC |
|||
|year=2004 |
|||
|publisher=Motilal Banarsidass |
|||
|isbn=978-81-208-2036-4}} |
|||
*{{citation |
|||
|last=Tobias |
|||
|first=Michael |
|||
|title=Life Force: The World of Jainism |
|||
|url=http://books.google.com/books?id=ybQB6yyw-tgC |
|||
|year=1991 |
|||
|publisher=Jain Publishing Company |
|||
|isbn=978-0-87573-080-6}} |
|||
*{{Citation |
|||
|title=Mahavira and His Teachings |
|||
|first=A. N. |
|||
|last=Upadhye |
|||
|editor-first=Richard J. |
|||
|editor-last=Cohen |
|||
|journal=Journal of the American Oriental Society |
|||
|volume=102 |
|||
|year=1982 |
|||
|doi=10.2307/601199 |
|||
|jstor=601199 |
|||
|issue=1 |
|||
|pages=231 |
|||
|publisher=American Oriental Society}} |
|||
*{{citation |
|||
|last=Vallely |
|||
|first=Anne |
|||
|title=Guardians of the Transcendent: An Ethnology of a Jain Ascetic Community |
|||
|url=http://books.google.com/books?id=eI4PAY9rDmQC |
|||
|year=2002 |
|||
|publisher=University of Toronto Press |
|||
|isbn=978-0-8020-8415-6}} |
|||
*{{citation |
|||
|last=Vyas |
|||
|first=R.T. |
|||
|title=Studies in Jaina art and iconography and allied subjects |
|||
|url=http://books.google.com/books?id=fETebHcHKogC |
|||
|year=1995 |
|||
|publisher=Abhinav Publications |
|||
|isbn=978-81-7017-316-8}} |
|||
*{{citation |
|||
|last=Sastri |
|||
|first=S. Srikanta |
|||
|title=The Original Home of Jainism |
|||
|url=http://www.srikanta-sastri.org/the-original-home-of-jainism/4584892825 |
|||
|year=1949 |
|||
|publisher=The Jaina Antiquary}} |
|||
*{{citation |
|||
|first=Kristi L. |
|||
|last=Wiley |
|||
|title=The A to Z of Jainism |
|||
|url=http://books.google.com/books?id=kUz9o-EKTpwC |
|||
|year=2009 |
|||
|publisher=Scarecrow Press |
|||
|isbn=978-0-8108-6821-2}} |
|||
*{{citation |
|||
|last=Widengren |
|||
|first=G. |
|||
|title=Historia Religionum, Volume 2 Religions of the Present |
|||
|url=http://books.google.com/books?id=3rrQY1tzLQUC |
|||
|year=1971 |
|||
|publisher=BRILL |
|||
|isbn=978-90-04-02598-1}} |
|||
*{{citation |
|||
|last=Williams |
|||
|first=Robert |
|||
|title=Jaina Yoga: A Survey of the Mediaeval Śrāvakācāras |
|||
|url=http://books.google.com/books?id=LLKcrIJ6oscC |
|||
|year=1991 |
|||
|publisher=Motilal Banarsidass |
|||
|isbn=978-81-208-0775-4}} |
|||
*{{citation |
|||
|last =Tatia |
|||
| first = Nathmal (tr.) |
|||
| title =Tattvārtha Sūtra: That which Is of Vācaka Umāsvāti |
|||
| publisher =Rowman Altamira |
|||
| year =1994 |
|||
| location =Lanham, MD |
|||
| language =Sanskrit - English |
|||
| isbn =0-7619-8993-5 }} |
|||
*{{citation |
|||
| last =Nayanar |
|||
| first =Prof. A. Chakravarti |
|||
| title =Samayasāra of Ācārya Kundakunda |
|||
| publisher =Today & Tomorrows Printer and Publisher |
|||
| year =2005 |
|||
| location =New Delhi |
|||
| isbn =81-7019-364-8 }} |
|||
*{{citation |
|||
|last1=Jain |
|||
|first1=Vijay K. |
|||
|title=Tattvârthsûtra |
|||
|year=2011 |
|||
|publisher=Vikalp Printers |
|||
|location=(Uttarakhand) India |
|||
|isbn=81-903639-2-1 |
|||
|edition=1st |
|||
|url=https://archive.org/details/AcharyaUmasvamisTattvarthsutra |
|||
|quote=Non-Copyright}} |
|||
*{{Citation |
|||
|last1=Jain |
|||
|first1=Hiralal |
|||
|last2=Upadhye |
|||
|first2=Adinath Neminath |
|||
|title=Mahavira his Times and his Philosophy of Life |
|||
|url=http://books.google.com/books?id=GHfzERhGUjQC&pg=PA18 |
|||
|accessdate=28 June 2013 |
|||
|year=2000 |
|||
|publisher=Bharatiya Jnanpith |
|||
|page=18}} |
|||
*{{বই উদ্ধৃতি |
|||
|শিরোনাম=Risabha Deva - The Founder of Jainism |
|||
|শেষাংশ=Jain |
|||
|প্রথমাংশ=Champat Rai |
|||
|প্রকাশক=Bhagwan Rishabhdeo Granth Mala |
|||
|বছর=2008 |
|||
|আইএসবিএন= 978-8177720228 |
|||
}} |
}} |
||
জৈনধর্ম হল একটি প্রাচীন [[ভারতীয় ধর্ম]]। এই ধর্মের উৎস অস্পষ্ট।{{sfn|স্যানগেভ|২০০১|p=১৮৫}}{{sfn|র্যানকিন|মারডিয়া|২০১৩|p=৯৭৫}}{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|p=১৩}} জৈনরা দাবি করেন যে, এটি একটি সনাতন ধর্ম এবং প্রথম তীর্থংকর [[ঋষভনাথ]] এই ধর্মের প্রথম পার্থিব প্রতিষ্ঠাতা।{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|p=১৬}} গবেষকেরা অনুমান করেন যে, [[সিন্ধু সভ্যতা|সিন্ধু সভ্যতার]] সিলমোহরে দৃষ্ট বৃষের চিত্রগুলি জৈনধর্মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।{{sfn|লং|২০১৩|pp=৫৩–৫৪}} এটি প্রাচীন ভারতের [[বেদ]]-বিরোধী অন্যতম "[[শ্রমণ]]" ধর্মবিশ্বাস।{{sfn|লকটেফোল্ড|২০০২|p=৬৩৯}}{{sfn|বিলিমোরিয়া|১৯৮৮|pp=১–৩০}} দার্শনিক [[সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ|সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের]] মতে এই ধর্মমতের অস্তিত্ব বেদসমূহের পূর্বেও ছিল।{{sfn|জম্বুবিজয়|২০০২|p=১১৪}}{{sfn|পান্ডে|১৯৫৭|p=৩৫৩}} |
|||
*{{citation |
|||
|last1=Balcerowicz |
|||
প্রথম বাইশ জন তীর্থংকরের অস্তিত্ব এখনও প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি।{{sfn|স্যানগেভ|২০০১|pp=১০৪, ১২৯}}{{sfn|সরস্বতী|১৯০৮|p=৪৪৪}} ত্রয়োবিংশ তীর্থংকর [[পার্শ্বনাথ]] ছিলেন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব।{{sfn|জিমার|১৯৫৩|p=১৮৩}}{{sfn|জৈনি|১৯৯৮|p=১০}}তাঁর সময়কাল সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী।{{sfn|বার্নেট|১৯৫৭|p=৭}} মহাবীরকে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে [[গৌতম বুদ্ধ|গৌতম বুদ্ধের]] সমসাময়িক মনে করা হয়।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০৩এ|p=৩৮৩}}{{sfn|কেওন|প্রেবিশ|২০১৩|pp=১২৭–১৩০}} জৈন ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও বুদ্ধের সমসাময়িক কালেই শুরু হয়েছিল।{{sfn|স্যানগেভ|২০০১|p=১০৫}} পরবর্তীকালে অনুগামী এবং যে বাণিজ্য প্রক্রিয়া দুই ধর্মকে পুষ্ট করত তা নিয়ে দুই ধর্মের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়।{{sfn|হিরাকাওয়া|১৯৯৩|pp=৪–৭}}{{sfn|নিলিস|২০১০|pp=৭২–৭৬}} বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থগুলির শিরোনাম কয়েকটি ক্ষেত্রে একই বা একই প্রকারের, কিন্তু এগুলিতে পৃথক মতবাদ ব্যক্ত হয়েছে।{{sfn|কিউভার্নস্টর্ম|২০০৩|pp=নয়–এগারো, ১৫১–১৬২}} |
|||
|first1=Piotr |
|||
|title=Jainism and the definition of religion |
|||
জৈনরা মনে করেন যে [[হর্যঙ্ক রাজবংশ|হর্যঙ্ক রাজবংশের]] রাজা [[বিম্বিসার]] (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৫৫৮-৪৯১ অব্দ), [[অজাতশত্রু]] (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৪৯২-৪৬০ অব্দ) ও [[উদয়ন]] (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৪৬০-৪৪০ অব্দ) ছিলেন জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষক।{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|p=৪১}} জৈন বিশ্বাসে [[মৌর্য সাম্রাজ্য|মৌর্য সাম্রাজ্যের]] প্রতিষ্ঠাতা তথা [[মহামতি অশোক|মহামতি অশোকের]] পিতামহ [[চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য]] (খ্রিস্টপূর্ব ৩২২-২৯৮) শেষ জীবনে জৈন সাধু [[ভদ্রবাহু|ভদ্রবাহুর]] শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সাধু হয়ে যান।{{sfn|কুলকে|রদারমান্ড|২০০৪|pp=৬৩–৬৫}}{{sfn|বোয়েশে|২০০৩|pp=৭–১৮}} জৈন ধর্মগ্রন্থগুলিতে বলা হয়েছে যে, শ্রবণবেলগোলায় স্বেচ্ছায় অনশন ব্রত করে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।{{sfn|মুখোপাধ্যায়|১৯৯৮|pp=৩৯–৪৬, ২৩৪–২৩৬}}{{sfn|কুলকে|রদারমান্ড|২০০৪|pp=৬৩–৬৫}} বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলিতে চন্দ্রগুপ্তের কাহিনিটির বিভিন্ন পাঠান্তর পাওয়া যায়।{{sfn|মুখোপাধ্যায়|১৯৮৮|pp=৪–২১, ২৩২–২৩৭}}{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|p=৪২}} |
|||
|date=2009 |
|||
|publisher=Hindi Granth Karyalay |
|||
খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে সম্রাট [[মহামতি অশোক|অশোক]] তাঁর স্তম্ভলিপিতে ''নিগন্থ'' অর্থাৎ জৈনদের কথা উল্লেখ করেছিলেন।{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|p=৪৩}} খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে নির্মিত জৈন মূর্তিও পাওয়া গিয়েছে।{{sfn|উপিন্দর সিং|২০১৬|p=৪৪৪}} প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ এমনই ইঙ্গিত করে যে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর পর থেকে মথুরা একটি গুরুত্বপূর্ণ জৈন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।{{sfn|জৈন|ফিশার|১৯৭৮|pp=৯–১০}} অন্ততপক্ষে খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর অভিলিখনগুলি থেকে বোঝা যায় ততদিনের মধ্যে জৈনরা দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল।{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|p=৪৯}} অভিলিখনের প্রমাণ থেকে জানা যায় যে, খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় বা প্রথম শতাব্দীতেও দক্ষিণ ভারতে জৈন সাধুরা বাস করতেন এবং প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ থেকে বোঝা যায় খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে [[গুজরাত|গুজরাতের]] [[সৌরাষ্ট্র]] অঞ্চলে জৈন সাধুরা থাকতেন।{{sfn|কর্ট|২০১০|p=২০২}} |
|||
|location=Mumbai |
|||
|isbn=978-81-887-69292 |
|||
রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা জৈনধর্মের বিকাশ ও পতনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।{{sfn|নাথুভাই শাহ|২০০৪|pp=৬৯–৭০}} খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে [[রাষ্ট্রকূট রাজবংশ|রাষ্ট্রকূট রাজবংশের]] হিন্দু রাজারা প্রধান প্রধান জৈন গুহামন্দিরগুলির পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন।{{sfn|পেরেইরা|১৯৭৭|pp=২১–২৪}} সপ্তম শতাব্দীতে রাজা [[হর্ষবর্ধন]] জৈনধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্মের সকল সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন।{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|p=৫২}} পল্লব রাজা [[প্রথম মহেন্দ্রবর্মণ]] (৬০০-৬৩০ খ্রিস্টাব্দ) জৈনধর্ম ত্যাগ করে শৈবধর্ম গ্রহণ করেন।{{sfn|লকটেফেল্ড|২০০২|p=৪০৯}} তাঁর লেখা ''[[মত্তবিলাস প্রহসন]]''-এ কয়েকটি শৈব সম্প্রদায় ও বৌদ্ধদের উপহাস করা হয়েছে এবং জৈন সাধুদের ঘৃণ্য আখ্যা দেওয়া হয়েছে।{{sfn|অরুণাচলম|১৯৮১|p=১৭০}} ৭০০ থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দে [[সেউন (যাদব) রাজবংশ|যাদব রাজবংশ]] [[ইলোরা গুহাসমূহ|ইলোরা গুহাসমূহে]] অনেকগুলি মন্দির নির্মাণ করেছিল।<ref name=asiintro>[http://asi.nic.in/asi_monu_whs_ellora.asp বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান – ইলোরা গুহাসমূহ] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20151007002950/http://asi.nic.in/asi_monu_whs_ellora.asp |date=7 October 2015 }}, ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (২০১১), ভারত সরকার</ref>{{sfn|গোপাল|১৯৯০|p=১৭৮}}{{sfn|ওয়েন|২০১২বি|pp=১–১০}} |
|||
|edition=1st |
|||
অষ্টম শতাব্দীতে রাজা [[আম (রাজা)|আম]] জৈনধর্মে ধর্মান্তরিত হন। এই যুগেই জৈন তীর্থযাত্রার প্রথাটি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|pp=৫২–৫৪}} খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীতে [[চালুক্য রাজবংশ|চালুক্য রাজবংশের]] প্রতিষ্ঠাতা [[মূলরাজ]] নিজে জৈন না হলেও একটি জৈন মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|p=৫৬}} একাদশ শতাব্দীতে [[কল্যাণীর কলচুরি|কলচুরির]] রাজা [[দ্বিতীয় বিজল|দ্বিতীয় বিজলের]] মন্ত্রী [[বসব]] অনেক জৈনকে [[লিঙ্গায়েত ধর্ম|লিঙ্গায়েত]] শৈব সম্প্রদায়ে ধর্মান্তরিত করেন। লিঙ্গায়েতরা অনেক জৈন মন্দির ধ্বংস করে এবং সেগুলিকে নিজেদের উপাসনালয়ে পরিণত করে।{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|pp=৭৫–৭৭}} [[হোয়সল রাজবংশ|হোয়সল]] রাজা [[বিষ্ণুবর্ধন]] (আনুমানিক ১১০৮-১১৫২ খ্রিস্টাব্দ) [[রামানুজ|রামানুজের]] প্রভাবে [[বৈষ্ণবধর্ম]] গ্রহণ করেন এবং অধুনা [[কর্ণাটক]] ভূখণ্ডে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে।{{sfn|দাস|২০০৫|p=১৬১}} |
|||
=== মধ্যযুগ === |
|||
[[File:Gori Mandar.jpg|alt=Jain monuments in Nagarparkar, Pakistan|thumb|upright|[[পাকিস্তান|পাকিস্তানের]] [[নগরপকর|নগরপকরে]] [[গোরি মন্দির, নগরপকর|গোরি জৈন মন্দিরের]] ধ্বংসাবশেষ। ১৯৪৭ সালের আগে একটি তীর্থক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হত।<ref name=":0">{{cite web|url=https://whc.unesco.org/en/tentativelists/6111/|title=নগরপকর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র – ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী কেন্দ্র |last=কেন্দ্র |first=ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী |website=whc.unesco.org|language=en|access-date=2017-04-14|archive-url=https://web.archive.org/web/20170510093259/https://whc.unesco.org/en/tentativelists/6111/|archive-date=10 May 2017|url-status=live|df=dmy-all}}</ref>]] |
|||
[[ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমান বিজয়|ভারতীয় উপমহাদেশ মুসলমান বিজয়ের]] পরে জৈনরা মুসলমান শাসকদের নিপীড়নের শিকার হন।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=১৪৫–১৪৬, ১২৪}} [[মাহমুদ গজনি]] (১০০১), [[মহম্মদ ঘোরি]] (১১৭৫) ও [[আলাউদ্দিন খিলজি]] (১২৯৮) প্রমুখ মুসলমান শাসকেরা জৈন সম্প্রদায়ের উপর আরও অত্যাচার চালায়।{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|pp=৭৪–৭৫}} তারা জৈনদের মূর্তিগুলি ধ্বংস করে এবং জৈন মন্দিরগুলিকে হয় ধ্বংস করে বা সেগুলিকে মসজিদে রূপান্তরিত করেছিল। তবে মুসলমান শাসকদের মধ্যে কয়েকজন ব্যতিক্রমীও ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, সম্রাট [[আকবর]] (১৫৪২{{nsndns}}১৬০৫) তাঁর কিংবদন্তি ধর্মীয় সহিষ্ণুতার কারণে জৈনদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে জৈনদের পর্যুষন উৎসবে খাঁচাবন্দী পাখিদের মুক্তি দেওয়ার ও প্রাণীহত্যা বন্ধ রাখার নির্দেশ দিতেন।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|p=১৪৬}} আকবরের রাজত্বকাল সমাপ্ত হওয়ার পর সপ্তদশ শতাব্দীতে জৈনরা আবার প্রবল মুসলমান নিপীড়নের সম্মুখীন হন।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=২২০–২২১}}{{sfn|ট্রুশকে|২০১৫|pp=১৩১১–১৩৪৪}} ঐতিহ্যগতভাবে জৈন সম্প্রদায় ছিল ব্যাংকার ও ধনিক শ্রেণি এবং তা মুসলমান শাসকদের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। যদিও ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমান শাসনকালে তাঁরা কদাচিৎই রাজনৈতিক ক্ষমতার অংশ হয়েছিলেন।{{sfn|কর্ট|১৯৯৮|pp=৮৫–৮৬}} |
|||
===ঔপনিবেশিক যুগ=== |
|||
{{Multiple images |
|||
| image1 = Virchand Gandhi poster.jpg |
|||
| caption1 = ১৮৯৩ সালে [[শিকাগো|শিকাগোতে]] আয়োজিত বিশ্ব ধর্ম মহাসভায় জৈনধর্মের প্রতিনিধিত্বকারী [[বীরচন্দ গান্ধী|বীরচন্দ গান্ধীর]] একটি পোস্টার। |
|||
| width1 = 160 |
|||
| image2 = Srimad Rajcandra.jpg |
|||
| caption2 = শ্রদ্ধেয় জৈন সন্ত, কবি ও সংস্কারক [[শ্রীমদ্ রাজচন্দ্র|শ্রীমদ্ রাজচন্দ্রের]] একটি তৈলচিত্র। |
|||
| width2 = 160 |
|||
}} |
}} |
||
১৮৯৩ সালে প্রথম [[বিশ্ব ধর্ম মহাসভা|বিশ্ব ধর্ম মহাসভায়]] জৈনধর্মের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন [[বীরচন্দ গান্ধী]] নামে এক বিশিষ্ট গুজরাতি জৈন পণ্ডিত। তিনি জৈনদের অধিকার রক্ষার জন্য আন্দোলন করেছিলেন এবং জৈনধর্ম সম্পর্কে বহু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন এবং বক্তৃতা দিয়েছিলেন। <ref name=it>{{cite web|last=ট্রাইবিউন |first=ইন্ডিয়া |title=বীরচন্দ গান্ধী – আ গান্ধী বিফোর গান্ধী অ্যান আনসাং গান্ধী হু সেট কোর্স অফ হিজ নেমসেক |url=http://www.indiatribune.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9374:virchand-gandhi--a-gandhi-before-gandhi-an-unsung-gandhi-who-set-course-for-his-namesake-&catid=25:community&Itemid=457|publisher=ইন্ডিয়া ট্রাইবিউন |accessdate=17 August 2012}}</ref><ref name=OpenCourt>{{cite book|last=হাওয়ার্ড |first=শ্রীমতী চার্লস |title=দি ওপেন কোর্ট, খণ্ড ১৬, এনআর. ৪ "দ্য ডেথ অফ মি. বীরচন্দ আর. গান্ধী"|date=April 1902|publisher=দি ওপেন কোর্ট পাবলিশিং কোম্পানি |location=Chicago|url=https://books.google.com/books?id=i-IeAQAAIAAJ&dq=The%20Open%20court&pg=PA51#q=gandh}}</ref> |
|||
*{{citation |
|||
|last1=Zimmer |
|||
|first1=Heinrich |
|||
|title=Philosophies Of India |
|||
|year=1952 |
|||
|editor=Joseph Campbell |
|||
|publisher=Routledge & Kegan Paul Ltd |
|||
|location=London, E.C. 4 |
|||
|url=https://archive.org/details/Philosophy.of.India.by.Heinrich.Zimmer |
|||
|isbn=978-8120807396}} |
|||
*{{citation |
|||
|last1=Jain |
|||
|first1=Shanti Lal |
|||
|title=ABC of Jainism |
|||
|year=1998 |
|||
|publisher=Jnanodaya Vidyapeeth |
|||
|location=Bhopal (M.P.) |
|||
|isbn=81-7628-0003}} |
|||
*{{citation |
|||
|last=Rankin |
|||
|first=Aidan |
|||
|title=Living Jainism: An Ethical Science |
|||
|url=https://books.google.co.in/books?id=bQxZAQAAQBAJ |
|||
|year=2013 |
|||
|publisher=John Hunt Publishing |
|||
|isbn=978-1780999111}} |
|||
*{{citation |
|||
|last1=Jain |
|||
|first1=Vijay K. |
|||
|title=Acharya Amritchandra's Purushartha Siddhyupaya |
|||
|year=2012 |
|||
|publisher=Vikalp Printers |
|||
|isbn=81-903639-4-8 |
|||
|url=https://books.google.co.in/books?isbn=8190363948 |
|||
|archiveurl=https://archive.org/details/AcharyaAmritchandrasPurusharthaSiddhyupaya |
|||
|archivedate=2012 |
|||
|quote=Non-Copyright}} |
|||
[[গুজরাত]] অঞ্চলে জৈনধর্মের পুনঃপ্রচলনের পুরোভাগে ছিলেন [[শ্রীমদ্ রাজচন্দ্র]] নামে এক অতীন্দ্রিয়বাদী, কবি ও দার্শনিক। ১৮৮৭ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি তিনি স্যার ফ্রামজি কোয়াসজি ইনস্টিটিউটে ''শতাবধান'' (১০০ ''অবধান'') সম্পূর্ণ করেছিলেন। এর ফলে তিনি প্রশংসা ও জনপ্রিয়তা দুইই অর্জন করেছিলেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও জনসাধারণ কর্তৃক তিনি একাধিক স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সেই সঙ্গে কৈশোরেই তিনি "সাক্ষাৎ সরস্বতী" উপাধি অর্জন করেছিলেন।<ref name="CSCSU">{{cite web | website=কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগ, কলোরাডো রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় | url=http://www.cs.colostate.edu/~malaiya/rajchandra.html |title=লাইফ অফ শ্রীমদ্ রাজচন্দ্র |accessdate=8 January 2017}}</ref>{{snf|স্যালটার|২০০২|p=১৩২}} জাতীয় সংবাদপত্রগুলিতে তাঁর কাজকর্ম বহুল প্রচার লাভ করেছিল।{{snf|স্যালটার|২০০২|p=১৩৩}} বিশ্ব ধর্ম মহাসভায় বীরচন্দ গান্ধী শ্রীমদ্ রাজচন্দ্রের কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করেছিলেন।<ref name="KarbhariGāndhī1911">{{cite book|author1=বাঘু এফ. কারভারি |author2=বীরচন্দ রাঘবজী গান্ধী |title=দ্য জৈন ফিলোজফি: কালেক্টেড অ্যান্ড এডিটেড বাই বাঘু এফ. কারবারি |url=https://books.google.com/books?id=L5kWQQAACAAJ|year=1911|publisher=এন. এম. ত্রিপাঠী অ্যান্ড কোম্পানি |pages=১১৬–১২০}}</ref> |
|||
{{refend}} |
|||
তিনি মহাত্মা গান্ধীর অন্যতম আধ্যাত্মিক গুরু হিসেবেও সুপরিচিত ছিলেন।{{snf|স্যালটার|২০০২|p=১৪৫}} ১৮৯১ সালে [[মুম্বই|বোম্বাই]] (অধুনা [[মুম্বই]]) শহরে তাঁদের সাক্ষাৎ হয় এবং গান্ধী যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় ছিলেন তখন পত্রবিনিময়ের মাধ্যমে তাঁদের অনেক কথোপকথন হয়েছিল। নিজের আত্মজীবনী ''[[দ্য স্টোরি অফ মাই এক্সপেরিমেন্টস উইথ ট্রুথ]]'' গ্রন্থে শ্রীমদ্ রাজচন্দ্রের প্রতি নিজের মনোভাব প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী তাঁকে নিজের "গুরু ও সহায়ক" এবং তাঁর "আধ্যাত্মিক সংকটকালের মুহুর্তে আশ্রয়" বলে উল্লেখ করেন। শ্রীমদ্ রাজচন্দ্রের উপদেশাবলি প্রত্যক্ষভাবে গান্ধীর অহিংস নীতিকে প্রভাবিত করেছিল।<ref name="Jainpedia">{{cite web | title=রাজচন্দ্র | website=জৈনপেডিয়া |first=জেরোম |last=পেতিত | date=2016 | url=http://www.jainpedia.org/themes/people/studying-jainism/rajacandra.html | accessdate=9 January 2017}}</ref><ref name="Weber2004">{{cite book|url=https://archive.org/details/gandhiasdisciple0000webe|url-access=registration|title=গান্ধী অ্যাজ ডিসাইপল অ্যান্ড মেন্টর |author=টমাস ওয়েবার |date=2 December 2004|publisher=কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস |isbn=978-1-139-45657-9|pages=[https://archive.org/details/gandhiasdisciple0000webe/page/34 ৩৪]–৩৬}}</ref>{{snf|স্যালটার|২০০২|p=১৪৫}} |
|||
== আরও পড়ুন == |
|||
* Alsdorf, Ludwig. ''Jaina Studies: Their Present State and Future Tasks.'' Eng. tr. Bal Patil. Edited by Willem Bollée. Pandit Nathuram Premi Research Series Volume 1. Mumbai: Hindi Granth Karyalay, 2006. |
|||
* Amiel,Pierre. ''Les Jaïns aujourd'hui dans le monde'' Ed. L'Harmattan, Paris, 2003 translated in English and printed under the title "Jains today in the world" by Parshwanath Vidyapeeth, Varanasi,India, 2008 |
|||
* Amiel,Pierre.''B.A.-BA du Jaïnisme'' Editions Pardès,Grez sur Loing,2008 |
|||
* Balbir, Nalini (Ed.) ''Catalogue of the Jain Manuscripts of the British Library''. Set of 3 books. London: Institute of Jainology, 2006. |
|||
* Bollée, Willem. ''The Story of Paesi'' Pandit Nathuram Premi Research Series Volume 2. Mumbai: Hindi Granth Karyalay, 2005. |
|||
* Bollée, Willem. ''Vyavahara Bhasya Pithika.'' Prakrit text with English translation, annotations and exhaustive Index by Willem Bollée. Pandit Nathuram Premi Research Series Volume 4. Mumbai: Hindi Granth Karyalay, 2006. |
|||
* [[Colette Caillat|Caillat, Colette]] "La cosmologie jaïna" Ed. du Chêne, Paris 1981. |
|||
* Chand, Bool. "Mahavira-Le Grand héros des Jaïns" Maisonneuve et Larose, Paris 1998. |
|||
* Hynson, Colin.'' Discover Jainism.'' Ed. Mehool Sanghrajka. London: Institute of Jainology, 2007. |
|||
* Jain, DuliChand. ''English version of "Baghawan Mahavir ki Vani" - Thus Spake Lord Mahavir''. Chennai, Sri Ramakrishna Math, 1998. |
|||
* Jain, Duli Chandra (Ed.) ''Studies in Jainism''. Set of 3 books. New York: Jain Stucy Circle, 2004. |
|||
* Jalaj, Jaykumar. ''The Basic Thought of Bhagavan Mahavir''. Ed. Elinor Velázquez. (5th edition) Jaipur: Prakrit Bharati Academy, 2007. |
|||
* Joindu. ''Paramatmaprakasha.'' Apabhramsha text with Hindi tr. by Jaykumar Jalaj. Ed. Manish Modi. Pandit Nathuram Premi Research Series Volume 9. Mumbai: Hindi Granth Karyalay, 2007. |
|||
* Joindu. ''Yogasara.'' Apabhramsha text with Hindi tr. by Jaykumar Jalaj. Ed. Satyanarayana Hegde. Pandit Nathuram Premi Research Series Volume 10. Mumbai: Hindi Granth Karyalay, 2008. |
|||
* Kapashi, Vinod. ''Nava Smarana: Nine Sacred Recitations of Jainism.'' Ed. Signe Kirde. Mumbai: Hindi Granth Karyalay, 2007. |
|||
* Kundakunda. ''Atthapahuda'' Prakrit text with Hindi tr. by Jaykumar Jalaj. Ed. Manish Modi. Pandit Nathuram Premi Research Series Volume 6. Mumbai: Hindi Granth Karyalay, 2006. |
|||
* Mardia, K.V. ''The Scientific Foundations of Jainism.'' Motilal Banarsidass, New Delhi, latest edition 2007. {{আইএসবিএন|81-208-0659-X}} (''Jain Dharma ki Vigyanik Adharshila''. Parsvanath Vidhyapitha, Varanasi. 2004. {{আইএসবিএন|81-86715-71-1}}). |
|||
* Mehta, T.U. ''Path of Arhat - A Religious Democracy'', Volume 63, Faridabad: Pujya Sohanalala Smaraka Parsvanatha Sodhapitha, 1993. |
|||
* Nagendra Kr Singh, Indo-European Jain Research Foundation, Encyclopaedia of Jainism {{আইএসবিএন|81-261-0691-3}}, {{আইএসবিএন|978-81-261-0691-2}} |
|||
* Natubhai Shah, Jainism: The World of Conquerors, Published by Sussex Academic Press, 1998, {{আইএসবিএন|1-898723-97-4}}, {{আইএসবিএন|978-1-898723-97-4}} |
|||
* Patil, Bal. ''Jaya Gommatesha.'' Foreword by [[Colette Caillat]]. Mumbai: Hindi Granth Karyalay, 2006. |
|||
* Prabhacandra. ''Tattvarthasutra.'' Sanskrit text with Hindi tr. by Jaykumar Jalaj. Preface by Nalini Balbir. Ed. Manish Modi. Pandit Nathuram Premi Research Series Volume 7. Mumbai: Hindi Granth Karyalay, 2008. |
|||
* Pujyapada. ''Samadhitantra.'' Sanskrit text with Hindi tr. by Jaykumar Jalaj. Pandit Nathuram Premi Research Series Volume 5. Mumbai: Hindi Granth Karyalay, 2006. |
|||
* Pujyapada. ''Istopadesha.'' Sanskrit text with Hindi tr. by Jaykumar Jalaj. Ed. Manish Modi. Pandit Nathuram Premi Research Series Volume 14. Mumbai: Hindi Granth Karyalay, 2007. |
|||
* Rankin, Aidan. 'The Jain Path: Ancient Wisdom for the West.' Winchester/Washington DC: O Books, 2006. |
|||
* Reymond Jean-Pierre "L'Inde des Jaïns" Ed. Atlas 1991. |
|||
* Roy, Ashim Kumar. ''A history of the Jains'', New Delhi: Gitanjali Publishing House, 1984. |
|||
* Samantabhadra. ''Ratnakaranda Sravakacara.'' Sanskrit text with Hindi tr. by Jaykumar Jalaj. Preface by Paul Dundas. Pandit Nathuram Premi Research Series Volume 3. Mumbai: Hindi Granth Karyalay, 2006. |
|||
* Sangave Vilas. 'Le Jaïnisme-Philosophie et Religion de l'Inde" Editions Trédaniel Paris 1999. |
|||
* Todarmal. ''Moksamarga Prakashaka.'' Jaipur: Todarmal Smarak Trust, 1992. |
|||
* Vijayashri. ''Sachitra Pacchis Bol.'' Agra: Mahasati Kaushalya Devi Prakashan Trust, 2005. |
|||
ঔপনিবেশ যুগের প্রতিবেদনে ও খ্রিস্টীয় মিশনারিদের চোখে জৈনধর্মকে নানা চোখে দেখা হয়েছিল। কেউ এই ধর্মকে হিন্দুধর্মের, কেউ বা বৌদ্ধধর্মের একটি সম্প্রদায় মনে করেছিলেন; আবার কেউ বা এটিকে আলাদা একটি ধর্ম মনে করেছিলেন।<ref>{{cite book |title=ভেরিয়াস সেন্সাস অফ ইন্ডিয়া: ১৮৭১–১৮৭২ |url={{Google books|4AEJAAAAQAAJ |plainurl=yes}} |year=1867 |publisher=ভারত সরকার |page=৩১ টীকা ১৪০}}</ref>{{sfn|হপকিনস|১৯০২|p=২৮৩}}{{sfn|সুনবল|১৯৩৪|pp=৯১–৯৩}} পৌত্তলিক সৃষ্টিকর্তা দেবদেবীতে অবিশ্বাসী জৈনরা খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হতে অস্বীকার করায় খ্রিস্টীয় ধর্মপ্রচারকেরা বিফল মনোরথ হয়েছিলেন। সেই সঙ্গে [[চম্পৎ রাই জৈন]] প্রমুখ ঔপনিবেশিক যুগের জৈন পণ্ডিতেরা জৈনধর্মের বিরুদ্ধ সমালোচনা এবং খ্রিস্টীয় ধর্মপ্রচারকদের ভ্রান্ত ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন।{{sfn|জৈনি|২০০০|p=৩৩}} খ্রিস্টীয় ও ইসলামীয় ধর্মপ্রচারকেরা জৈন প্রথা ও রীতিনীতিগুলিকে পৌত্তলিক ও কুসংস্কারমূলক মনে করতেন।{{sfn|হ্যাকেট|২০০৮|pp=৬৩–৬৮}} [[জন ই. কর্ট]] বলেছেন যে, এই জাতীয় সমালোচনাগুলি ত্রুটিযুক্ত এবং খ্রিস্টানদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একই ধরণের রীতিনীতিগুলিকে উপেক্ষা করেই করা হয়েছিল।{{sfn|কর্ট|২০১০|pp=১২–১৬, ২০০–২০৭, ২০৮–২১৯, ২৫১ সঙ্গে টীকা ১০}} |
|||
== বহিঃসংযোগ == |
|||
{{কমন্স বিষয়শ্রেণী|Jainism|জৈনধর্ম}} |
|||
<!-- NOTE: Any external links in nature of advertisement for matrimonial or groups or lists or commercial advertisements will be immediately deleted --> |
|||
* [http://www.census.india.gov.in Census of India 2001. Office of the Registrar General, India.]{{অকার্যকর সংযোগ|তারিখ=ফেব্রুয়ারি ২০১৯ |bot=InternetArchiveBot |ঠিক করার প্রচেষ্টা=yes }} |
|||
* [http://www.herenow4u.net/index.php?id=68030 Concept of Physical Substance (Pudgala) in Jain Philosophy: Professor Mahavir Saran Jain] |
|||
* [http://www.herenow4u.net/index.php?id=67938 The Concept Of Embodied Soul And Liberated Soul In Jain Philosophy: Professor Mahavir Saran Jain] |
|||
* [http://www.kamit.jp/03_jaina/jain_eng.htm Jaina Architecture in India] |
|||
* [http://www.jainreligion.in About Jain Religion, Teerth, 24 Tirthankaras] |
|||
ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার ও বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য আইন প্রণয়ন করে নগ্ন অবস্থায় ঘুরে বেড়ানোকে গ্রেফতারিযোগ্য অপরাধ আখ্যা দেয়। এই আইনের ফলে বিশেষ প্রভাব পড়েছিল জৈন দিগম্বর সাধুদের উপর।{{sfn|ফ্লুগেল|২০০৬|pp=৩৪৮–৩৪৯}} অখিল ভারতীয় জৈন সমাজ এই আইনের বিরোধিতা করে বলে যে এতে জৈনদের ধর্মীয় অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। আচার্য [[শান্তিসাগর]] ১৯২৭ সালে বোম্বাই শহরে প্রবেশ করেন; কিন্তু তাঁকে দেহ বস্ত্রাচ্ছাদিত করতে বাধ্য করা হয়। তারপর তিনি নিজের অনুগামী নিয়ে নগ্ন হয়ে ভারতব্যাপী দিগম্বর তীর্থযাত্রায় বের হন। মহারাষ্ট্র অঞ্চলের দেশীয় রাজারা তাঁকে স্বাগত জানান।{{sfn|ফ্লুগেল|২০০৬|pp=৩৪৮–৩৪৯}} [[ব্রিটিশ রাজ|ব্রিটিশ রাজত্বে]] দিগম্বর সাধুদের উপর এই নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে এবং এই আইন প্রত্যাহারের জন্য শান্তিসাগর অনশন করেছিলেন।{{sfn|নাথুভাই শাহ|২০০৪|p=৫৬}} স্বাধীনতা লাভের পর ভারতে আইনগুলি প্রত্যাহৃত হয়।{{sfn|ফ্লুগেল|২০০৬|pp=৩৫৯–৩৬০}} |
|||
{{Sister project links|v=no|n=no|s=no|b=no}} |
|||
==আধুনিক যুগ== |
|||
{{Jain Agamas}} |
|||
{{Main|জৈন সম্প্রদায়}} |
|||
{{Religion topics}} |
|||
[[আচার্য]] সম্মানে বিভূষিতা প্রথম নারী ছিলেন [[আচার্য চন্দনা|চন্দনাজি]]। ১৯৮৭ সালে তিনি এই সম্মান অর্জন করেন।<ref name="MillerLong2019">{{cite book|author1=ক্রিস্টোফার প্যাট্রিক মিলার |author2=জেফরি ডি. লং |author3=মাইকেল রিডিং |title=বিকনস অফ ধর্ম: স্পিরিচুয়াল এক্সঅ্যাম্পলারস ফর দ্য মডার্ন এজ |url=https://books.google.com/books?id=_9i_DwAAQBAJ&pg=PA10 |date=15 December 2019|publisher=রোওম্যান অ্যান্ড লিটলফিল্ড |isbn=978-1-4985-6485-4|pages=৭, ১০–}}</ref> |
|||
জৈনধর্মের অনুগামীদের বলা হয় "জৈন"। এই শব্দটি উৎসারিত হয়েছে সংস্কৃত ''জিন'' (বিজয়ী) শব্দটি থেকে। ''জিন'' বলতে সেই সব সর্বজ্ঞ ব্যক্তিদের বোঝায় যাঁরা মোক্ষের পথ প্রদর্শন করান।{{sfn|স্যানগেভ|২০০৬|p=১৫}}{{sfn|উপিন্দর সিং|২০১৬|p=৩১৩}} জৈনদের অধিকাংশই বর্তমানে ভারতে বসবাস করেন। সমগ্র বিশ্বে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ জৈনধর্মের অনুগামী।{{Sfn|ভুর্স্ট|২০১৪|p=৯৬}}{{sfn|মেল্টন|বাউমান|২০১০|p=উনষাট, ১৩৯৫}} সেই হিসেবে [[প্রধান ধর্মসমূহ|জগতের প্রধান ধর্মসমূহের]] তুলনায় জৈনধর্ম ক্ষুদ্র একটি ধর্মবিশ্বাস। সমগ্র [[ভারতে জৈনধর্ম|ভারতের]] জনসংখ্যার ০.৩৭ শতাংশ জৈন ধর্মাবলম্বী। এঁদের অধিকাংশই বসবাস করেন [[মহারাষ্ট্রে জৈনধর্ম|মহারাষ্ট্র]] (২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী ১৪ লক্ষ,<ref name=jaindemographics/> ভারতীয় জৈনদের ৩১.৪৬ শতাংশ), [[রাজস্থানে জৈনধর্ম|রাজস্থান]] (১৩.৯৭ শতাংশ), [[গুজরাতে জৈনধর্ম|গুজরাত]] (১৩.০২ শতাংশ) ও [[মধ্যপ্রদেশ]] (১২.৭৪ শতাংশ) রাজ্যে। এছাড়া [[কর্ণাটকে জৈনধর্ম|কর্ণাটক]] (৯.৮৯ শতাংশ), [[উত্তরপ্রদেশে জৈনধর্ম|উত্তরপ্রদেশ]] (৪.৭৯ শতাংশ), [[দিল্লিতে জৈনধর্ম|দিল্লি]] (৩.৭৩ শতাংশ) ও [[তামিলনাড়ু|তামিলনাড়ুতেও]] (২.০১ শতাংশ) জৈনদের উপস্থিতি উল্লেখনীয়।<ref name=jaindemographics>{{citation |url=http://www.censusindia.gov.in/2011census/c-01.html |title=সি-১ পপুলেশন বাই রিলিজিয়াস কমিউনিটি |publisher=স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, ভারত সরকার |last=রেজিস্টার জেনারেল ও জনগণনা কমিশনারের কার্যালয় |date=2011 |access-date=9 September 2015|archive-url=https://web.archive.org/web/20150913045700/http://www.censusindia.gov.in/2011census/C-01.html |archive-date=13 September 2015 |url-status=live |df=dmy-all }}</ref> ভারতের বাইরে জৈনরা বাস করেন [[ইউরোপে জৈনধর্ম|ইউরোপ]], [[যুক্তরাজ্যে জৈনধর্ম|যুক্তরাজ্য]], [[মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জৈনধর্ম|মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র]], [[কানাডায় জৈনধর্ম|কানাডা]],{{sfn|উইলি|২০০৯|p=৪৩}} [[অস্ট্রেলিয়া]] ও [[আফ্রিকায় জৈনধর্ম|কেনিয়ায়]]।{{sfn|মুগাম্বি|২০১০|p=১০৮}} এছাড়া [[জাপানে জৈনধর্ম|জাপানেও]] দ্রুত হারে জৈনধর্ম প্রসার লাভ করছে; সে-দেশে পাঁচ হাজারেরও বেশি পরিবার জৈনধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে।<ref>{{cite web |url=https://m.timesofindia.com/india/thousands-of-japanese-making-a-smooth-transition-from-zen-to-jain/amp_articleshow/74262195.cms |title=থাউসেন্ডস অফ জাপানিজ মেকিং আ স্মুথ ট্রানজিশন ফ্রম জেন টু জৈন |date=23 February 2020 |website=হিন্দুস্তান টাইমস}}</ref> |
|||
{{কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রণ}} |
|||
২০১৫-১৬ সালে গৃহীত জাতীয় পরিবার ও স্বাস্থ্য সমীক্ষা (এনএফএইচএস-৪) অনুযায়ী, জৈনরা ভারতের ধনীতম সম্প্রদায়।<ref>{{cite web |url=https://www.hindustantimes.com/india-news/delhi-and-punjab-richest-states-jain-wealthiest-community-national-survey/story-sakdd3MBOfKhU2p5LrNVUM.html |title=দিল্লি অ্যান্ড পাঞ্জাব রিচেস্ট স্টেটস, জৈন ওয়েদিয়েস্ট কমিউনিটি: ন্যাশনাল সার্ভে |date=13 January 2018 |website=হিন্দুস্তান টাইমস}}</ref> ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী, ভারতে বয়সের দিক থেকে সাত বছর থেকে বরিষ্ঠতম ব্যক্তিদের মধ্যে জৈন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই সাক্ষরতার হার সবচেয়ে বেশি (৮৭ শতাংশ) এবং অধিকাংশই স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।<ref>{{citation |url=http://timesofindia.indiatimes.com/india/Jains-have-highest-percentage-of-literates-Census-data/articleshow/53942863.cms |title=জৈনস হ্যাভ হাইয়েস্ট পারসেন্টেজ অফ লিটারেটস: সেনসাস ২০১১ |publisher=দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া |date=31 August 2016 |access-date=19 May 2017 |archive-url=https://web.archive.org/web/20170129153443/http://timesofindia.indiatimes.com/india/Jains-have-highest-percentage-of-literates-Census-data/articleshow/53942863.cms |archive-date=29 January 2017 |url-status=live |df=dmy-all }}</ref> অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের বাদ দিলে ভারতে জৈনদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ৯৭ শতাংশ। ভারতে জৈনদের মধ্যে লিঙ্গানুপাত ৯৪০; অবশ্য ০-৬ বছর বয়সীদের মধ্যে এই লিঙ্গানুপাতের ক্ষেত্রে জৈনরা দ্বিতীয় নিম্নতম (প্রতি ১০০০ বালকে ৮৭০ জন বালিকা)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্বদেশে এই স্থানে নিম্নতম স্থানের অধিকারী [[শিখ|শিখরা]]।<ref>{{citation| url=http://censusindia.gov.in/Ad_Campaign/drop_in_articles/04-Distribution_by_Religion.pdf| title=ডিস্ট্রিবিউশন অফ পপুলেশন বাই রিলিজিয়নস | author=ভারতের জনগণনা | publisher=ভারত সরকার | year=2011| access-date=19 May 2017| archive-url=https://web.archive.org/web/20160304191803/http://censusindia.gov.in/Ad_Campaign/drop_in_articles/04-Distribution_by_Religion.pdf| archive-date=4 March 2016| url-status=live| df=dmy-all}}</ref> |
|||
[[বিষয়শ্রেণী:ধর্ম]] |
|||
[[বিষয়শ্রেণী:জৈন ধর্ম|*]] |
|||
কয়েকটি প্রথা ও মতবাদের জন্য জৈনধর্ম বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রণী নেতা [[মহাত্মা গান্ধী]] জৈনধর্মের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে বলেছিলেন:{{sfn|রুডলফ|রুডলফ|১৯৮৪|p=১৭১}} |
|||
{{quote|বিশ্বে আর কোনও ধর্মই অহিংসার নীতিটিকে এত গভীর ও প্রণালীবদ্ধভাবে ব্যাখ্যা করেনি, যেমনটি জৈনধর্মে প্রতিটি মানুষের জীবনে এটির প্রয়োগযোগ্যতার সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। অহিংসার মঙ্গলময় নীতিটি যখনই বিশ্ববাসীর দেহান্ত ও পরকালেও [কিছু] অর্জনের জন্য আরোপিত হবে, তখন নিশ্চিতভাবেই জৈনধর্ম সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করবে এবং মহাবীর নিশ্চয়ই অহিংসার শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা হিসেবে সম্মানীত হবেন।{{sfn|জনার্দন পান্ডে|১৯৯৮|p=৫০}}}}<ref>মূল উদ্ধৃতি: No religion in the World has explained the principle of ''Ahiṃsā'' so deeply and systematically as is discussed with its applicability in every human life in Jainism. As and when the benevolent principle of ''Ahiṃsā'' or non-violence will be ascribed for practice by the people of the world to achieve their end of life in this world and beyond, Jainism is sure to have the uppermost status and Mahāvīra is sure to be respected as the greatest authority on ''Ahiṃsā''.</ref> |
|||
==আরও দেখুন== |
|||
{{commonscat}} |
|||
* [[জৈনধর্মের সমালোচনা]] |
|||
* [[জৈন আইন]] |
|||
* [[জৈন সৃষ্টিতত্ত্ব]] |
|||
* [[জৈনদের তালিকা]] |
|||
* [[অহিংসা]] |
|||
{{Portal bar|ভারত|দর্শন|মনস্তত্ত্ব|ধর্ম}} |
|||
==পাদটীকা== |
|||
{{notelist}} |
|||
==তথ্যসূত্র== |
|||
{{সূত্র তালিকা|৩}} |
|||
===উল্লেখপঞ্জি=== |
|||
{{refbegin|30em}} |
|||
* {{citation |last=আগরওয়াল |first=এম. কে. |title=ফ্রম ভারত টু ইন্ডিয়া |edition=খণ্ড ১: ক্রাইসি দ্য গোল্ডেন |url={{Google books|ROePWIBgyv8C|plainurl=yes}} |publisher=আইইউনিভার্স|date=2012|isbn=978-1-4759-0766-7}} |
|||
* {{citation |last=আগরওয়াল |first=এম. কে. |title=দ্য বেদিক কোর অফ হিউম্যান হিস্ট্রি: অ্যান্ড ট্রুথ উইল বি দ্য সেভিয়র |url={{Google books|zObPAwAAQBAJ|plainurl=yes}} |publisher=আইইউনিভার্স |date=2013|isbn=978-1-4917-1595-6}} |
|||
* {{citation |last=অ্যালবার্টস |first=ওয়ান্ডা |title=ইন্টিগ্রেটিভ রিলিজিয়াস এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া: আ স্টাডি-অফ-রিলিজিয়াস অ্যাপ্রোচ |url={{Google books|xvwKWS3VKfcC|plainurl=yes}} |year=2007|publisher=ওয়াল্টার ডে গ্রুইটার |isbn=978-3-11-097134-7 }} |
|||
* {{citation |last=অ্যাপেলটন |first=নাওমি |title=শেয়ার্ড ক্যারেকটারস ইন জৈন, বুদ্ধিস্ট অ্যান্ড হিন্দু ন্যারাটিভ: গডস, কিংস অ্যান্ড আদার হিরোজ |url={{Google books|3QWcDQAAQBAJ|plainurl=yes}} |year=2016|publisher=টেলর অ্যান্ড ফ্রান্সিস |isbn=978-1-317-05574-7 }} |
|||
* {{citation |last=আরোরা |first=উদয় প্রকাশ |author-link=উদয় প্রকাশ আরোরা |title=উদয়ন |url={{Google books|d4VeYJdww2YC|plainurl=yes}} |year=2007 }} |
|||
* {{citation |editor-last=অরুণাচলম |editor-first=এম. |editor-link=এম. অরুণাচলম |title=ঐন্তাম উলকত তামিল মানাটু-কারুট্টারাণকু আয়বুক কট্টুরৈকল |url={{Google books|3WFDAAAAYAAJ|plainurl=yes}} |date=1981 |publisher=ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোশিয়েসন অফ তামিল রিসার্চ}} |
|||
* {{citation |last=বাব |first=লরেন্স এ. |title=অ্যাবসেন্ট লর্ড: এস্থেটিকস অ্যান্ড কিংস ইন আ জৈন রিচুয়াল কালচার |url={{Google books|C8HcBvE8XJ4C|plainurl=yes}} |year=1996 |publisher=ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস |isbn=978-0-520-91708-8 }} |
|||
* {{citation |last=বেইলি |first=উইলিয়াম |title=দ্য থিওলজিক্যাল ইউনিভার্স |url={{Google books|G7_GBgAAQBAJ|plainurl=yes}} |publisher=বেইলি পাবলিশিং, পিএ |date=2012 |isbn=978-1-312-23861-9 }} |
|||
* {{citation |last=বালসারোউকজ |first=পিওট্র |authorlink=পিওট্র বালসারোউকজ |title=এসেজ ইন জৈন ফিলোফফি অ্যান্ড রিলিজিয়ন |url={{Google books|NcRpfZcIhLoC|plainurl=yes}} |year=2003 |publisher=[[মোতিলাল বনারসিদাস]] |isbn=978-81-208-1977-1 }} |
|||
* {{citation |last=বালসারোউকজ |first=পিওট্র |title=জৈনিজম অ্যান্ড দ্য ডেফিনেশন অফ রিলিজিয়ন |date=2009 |publisher=[[হিন্দি গ্রন্থ কার্যালয়]] |location=মুম্বই |isbn=978-81-88769-29-2 |edition=১ম}} |
|||
* {{citation |last=বালসারোউকজ |first=পিওট্র |title=আর্লি অ্যাসেটিজম ইন ইন্ডিয়া: আজীবিকিজম অ্যান্ড জৈনিজম|url={{Google books|nfOPCgAAQBAJ|plainurl=yes}} |year=2015 |publisher=রটলেজ |isbn=978-1-317-53853-0 }} |
|||
* {{citation |last=বার্নেট |first=লিঙ্কন |authorlink=লিঙ্কন বার্নেট| display-authors=এবং অন্যান্য| editor1-last=ওয়েলস |editor1-first=স্যাম |title=দ্য ওয়ার্ল্ড’স গ্রেট রিলিজিয়নস |year=1957 |publisher=[[টাইম ইনকর্পোরেটেড]] |location=নিউ ইয়র্ক |edition=1st |ref=harv}} |
|||
* {{citation |last=বার্টলি |first=সি. জে. |title=দ্য থিওলজি অফ রামানুজ: রিয়ালিজম অ্যান্ড রিলিজিয়ন |url={{Google books|9SpTAQAAQBAJ|plainurl=yes}}| year=2013| publisher=রটলেজ|isbn=978-1-136-85306-7 }} |
|||
* {{citation |last=বার্গার |first=পিটার |authorlink=পিটার এল. বার্গার |title=দি অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল ভ্যালুজ: এসেজ ইন অনরিং অফ জর্জ পেফার |url={{Google books|qSt8YyRKr0wC|plainurl=yes}} |date=2010 |publisher=[[পিয়ারসন এডুকেশন]] |location=India |isbn=978-81-317-2820-8 }} |
|||
* {{citation |last=বিলিমোরিয়া |first=পি. |title =শব্দপ্রমাণ: ওয়ার্ড অ্যান্ড নলেজ, স্টাডিজ অফ ক্ল্যাসিকাল ইন্ডিয়া |year=1988 |volume=১০, স্প্রিংগার |isbn=978-94-010-7810-8 }} |
|||
* {{citation |last=বোয়েশে |first=রজার |author-link=রজার বোয়েশে |title=দ্য ফার্স্ট গ্রেট পলিটিক্যাল রিয়ালিস্ট: কৌটিল্য অ্যান্ড হিজ অর্থশাস্ত্র |url={{Google books|K85NA7Rg67wC|plainurl=yes}} |year=2003 |publisher=লেক্সিংটন বুকস |isbn=978-0-7391-0607-5 }} |
|||
* {{citation |editor-last=বুটালিয়া |editor-first=তরুণজিৎ সিং |editor-last2=স্মল |editor-first2=ডায়ন পি. |title=রিলিজিয়ন ইন ওহিও: প্রোফাইলস অফ ফেইথ কমিউনিটিজ |url={{Google books|LRFePtMXjT8C|plainurl=yes}} |publisher=ওহিও ইউনিভার্সিটি প্রেস |date=2004 |isbn=978-0-8214-1551-1 }} |
|||
* {{citation |last=কালিয়াট |first=কোলেট |date=২০০৩এ |title=গ্লিনিংস ফ্রম আ কমপেয়ার্যাটিভ স্টাডি অফ আর্লি ক্যাননিক্যাল বুদ্ধিস্ট অ্যান্ড জৈন টেক্সটস |publisher=জার্নাল অফ দি ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোশিয়েশন অফ অফ বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ |volume=২৬ |issue=১}} |
|||
* {{citation |url=https://books.google.com/books?id=EscwAQAAMAAJ |title=দ্য প্র্যাকটিক্যাল পাথ|author=চম্পৎ রাই জৈন|authorlink=চম্পৎ রাই জৈন |year=1917 |publisher=দ্য সেন্ট্রাল জৈন পাবলিশিং হাউজ}} |
|||
* {{citation |last=চরিত্রপ্রজ্ঞা |first=সমানি |editor-last=শেঠিয়া |editor-first=তারা |title=অহিংসা, অনেকান্ত, অ্যান্ড জৈনিজম|url={{Google books|QYdlKv8wBiYC|plainurl=yes}} |year=2004 |publisher=মোতিলাল বনারসিদাস |isbn=978-81-208-2036-4 }} |
|||
* {{citation |last=চট্টোপাধ্যায় |first=অসীম কুমার |title=আ কমপ্রিহেনসিভ হিস্ট্রি অফ জৈনিজম: ফ্রম দি আর্লিয়েস্ট বিগিনিংস টু এডি ১০০০ |url={{Google books|IH7XAAAAMAAJ|plainurl=yes}}|year=2000|publisher=মুন্সিরাম মনোহরলাল|isbn=978-81-215-0931-2 }} |
|||
* {{citation |last1=ক্লার্ক |first1=পিটার |authorlink=পিটার বি. ক্লার্ক |last2=বেয়ার |first2=পিটার |authorlink2=পিটার বেয়ার |title=দ্য ওয়ার্ল্ড’স রিলিজিয়নস: কমিউনিটিজ অ্যান্ড ট্রান্সফর্মেশনস |url={{Google books|rBgn3xB75ZcC|plainurl=yes}} |date=2009 |publisher=রটলেজ |isbn=978-0-203-87212-3 }} |
|||
* {{citation |last=কর্ট | first=জন ই. |authorlink=জন ই. কর্ট |title=মিডিয়াভাল জৈন গডেস ট্র্যাডিশন| journal=নুমেন | volume=৩৪ | issue=২ | pages=২৩৫–২৫৫ | year=1987 | doi=10.1163/156852787x00047 }} |
|||
* {{citation |last=কর্ট | first=জন ই. |title=দ্য জৈন নলেজ ওয়্যারহাউসেজ: ট্র্যাডিশনাল লাইব্রেরিজ ইন ইন্ডিয়া |journal=জার্নাল অফ দি আমেরিকান ওরিয়েন্টাল সোসাইটি |volume=১১৫ |issue=১ |pages=৭৭–৮৭ |date=1995 |doi=10.2307/605310 |jstor=605310}} |
|||
* {{citation |editor-last=কর্ট |editor-first=জন ই. |title=ওপেন বাউন্ডারিজ: জৈন কমিউনিটিজ অ্যান্ড কালচারাল ইন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি |url={{Google books|yoHfm7BgqTgC|plainurl=yes}} |publisher=সানি প্রেস |date=1998 |isbn=978-0-7914-3785-8 }} |
|||
* {{citation |last=কর্ট |first=জন ই. |title=জৈনস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড: রিলিজিয়াস ভ্যালুজ অ্যান্ড আইডিওলজি ইন ইন্ডিয়া |url={{Google books|PZk-4HOMzsoC|plainurl=yes}} |publisher=অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস |date=2001a |isbn=978-0-19-513234-2 }} |
|||
* {{citation |last=কর্ট |first=জন ই. |editor-last=হোয়াইট |editor-first=ডেভিড গর্ডন |title=তন্ত্র ইন প্র্যাকটিস |url={{Google books|hayV4o50eUEC|plainurl=yes}} |year=২০০১বি| publisher=[[মোতিলাল বনারসিদাস]] |isbn=978-81-208-1778-4 }} |
|||
* {{citation |last=কর্ট |first=জন ই. |title=ফ্রেমিং দ্য জিনাস: ন্যারেটিভস অফ আইকনস অ্যান্ড আইডলস ইন জৈন হিস্ট্রি |url={{Google books|MDBpq23-0QoC|plainurl=yes}} |publisher=অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস |year=2010 |isbn=978-0-19-538502-1 }} |
|||
* {{citation |last=দালাল |first=রোশেন |authorlink=রোশেন দালাল |title=দ্য রিলিজিয়নস অফ ইন্ডিয়া: আ কনসাইস গাইড টু নাইন মেজর ফেইথস |url={{Google books|pNmfdAKFpkQC|plainurl=yes}} |date=২০১০এ|origyear=2006 |publisher=পেঙ্গুইন বুকস|isbn=978-0-14-341517-6 }} |
|||
* {{citation |last=দালাল |first=রোশেন |title=হিন্দুইজম: অ্যান অ্যালফাবেটিক্যাল গাইড |url={{Google books|DH0vmD8ghdMC|plainurl=yes}} |year=২০১০বি |publisher=পেঙ্গুইন বুকস |isbn=978-0-14-341421-6 }} |
|||
* {{citation |last=দাশ |first=শিশির কুমার |authorlink=শিশির কুমার দাশ |title=আ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান লিটারেচার, ৫০০–১৩৯৯: ফ্রম কোর্টলি টু দ্য পপুলার |url={{Google books|BC3l1AbPM8sC|plainurl=yes}} |date=2005 |publisher=[[সাহিত্য অকাদেমি]] |isbn=978-81-260-2171-0 }} |
|||
* {{citation |editor-last=ডনিগার |editor-first=ওয়েন্ডি |editor-link=ওয়েন্ডি ডনিগার |title=এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়নস |url={{Google books|ZP_f9icf2roC|plainurl=yes}} |date=1999 |publisher=মেরিয়াম-ওয়েবস্টার|isbn=978-0-87779-044-0 }} |
|||
* {{citation |last=ডুন্ডাস |first=পল |authorlink=পল ডুন্ডাস |title=দ্য জৈনস |url={{Google books|X8iAAgAAQBAJ|plainurl=yes}} |edition=২য় |date=2002 |orig-year=1992 |publisher=রটলেজ |isbn=978-0-415-26605-5 |location=লন্ডন ও নিউ ইয়র্ক}} |
|||
* {{citation |last=ডুন্ডাস |first=পল |title=এনসাইক্লোপেডিয়া অফ বুদ্ধিজম |editor-last=বাসওয়েল |editor-first=রবার্ট ই. |chapter=জৈনিজম অ্যান্ড বুদ্ধিজম |location=নিউ ইয়র্ক|publisher=ম্যাকমিলান রেফারেন্স লাইব্রেরি |year=২০০৩এ |isbn=978-0-02-865718-9 }} |
|||
* {{citation |last=ডুন্ডাস |first=পল |editor-last=অলিভেল এ. |editor-first=প্যাট্রিক |title=বিটুইন দি এম্পায়ারস: সোসাইটি ইন ইন্ডিয়া ৩০০ বিসিই টু ৪০০ সিই |url={{Google books|efaOR_-YsIcC|plainurl=yes}} |year=2006 |publisher=অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস |isbn=978-0-19-977507-1 }} |
|||
* {{citation |last=ফার্গুসন |first=জেমস |title=আ হিস্ট্রি অফ আর্কিটেকচার ইন অল কান্ট্রিজ: ফ্রম দি আর্লিয়েস্ট টাইমস টু দ্য প্রেজেন্ট ডেজ |url={{Google books|JXZAAAAAYAAJ|plainurl=yes}} |volume=৩ |publisher=জন মারি |date=1876 }} |
|||
* {{citation |last=ফিনেগান |first=জ্যাক |title=অ্যান আর্কিওলজিক্যাল হিস্ট্রি অফ রিলিজিয়নস অফ ইন্ডিয়ান এশিয়া |url={{Google books|BrDXAAAAMAAJ|plainurl=yes}}|year=1989|publisher=প্যারাগন হাউজ |isbn=978-0-913729-43-4 }} |
|||
* {{citation |last=ফ্লোরিডা |first=রবার্ট ই. |title=হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড’স মেজর রিলিজিয়নস: দ্য বুদ্ধিস্ট ট্র্যাডিশনস|url={{Google books|IlfuAAAAMAAJ|plainurl=yes}} |year=2005|publisher=এবিসি-ক্লিও|isbn=978-0-313-31318-9 }} |
|||
* {{citation |last=ফ্লুগেল|first=পিটার |authorlink=পিটার ফ্লুগেল |year=2002 |chapter=তেরাপন্থ শ্বেতাম্বর জৈন ট্র্যাডিশন |editor-last=মেল্টন |editor-first=জে. জি. |editor-last2=বাউম্যান |editor-first2=জি. |title=রিলিজিয়নস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড: আ কমপ্রিহেনসিভ এনসাইক্লোপিডিয়া অফ বিলিফস অ্যান্ড প্র্যাকটিশেস |publisher=এবিসি-ক্লিও |isbn=978-1-57607-223-3}} |
|||
* {{citation |last=ফ্লুগেল|first=পিটার |editor-last=কিং |editor-first=আনা এস. |editor-last2=ব্রোকিংটন |editor-first2=জৈন |editor-link2=জন ব্রোকিংটন |title=প্রেজেন্ট লর্ড: সীমান্ধর স্বামী অ্যান্ড দি অক্রম বিজ্ঞান মুভমেন্ট |url=http://eprints.soas.ac.uk/7438/1/Present_Lord_2003.pdf |work=দি ইন্টিমেন্ট আদার: লভ ডিভাইন ইন দি ইন্ডিক রিলিজিয়নস |publisher=[[ওরিয়েন্ট লংম্যান]] |year=2005 |isbn=978-81-250-2801-7 |location=নতুন দিল্লি}} |
|||
* {{citation |last=ফ্লুগেল|first=পিটার |title=স্টাডিজ ইন জৈন হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার: ডিসপিউটস অ্যান্ড ডায়ালগস |url={{Google books|CIgqBgAAQBAJ|plainurl=yes}} |year=2006 |publisher=রটলেজ |isbn=978-1-134-23552-0 }} |
|||
* {{citation |last=ফোর |first=শেরি |title=জৈনিজম: আ গাইড ফর দ্য পারপ্লেক্সড |url={{Google books|iAXsBQAAQBAJ|plainurl=yes}} |year=2015 |publisher=ব্লুমসবেরি পাবলিশিং |isbn=978-1-4742-2756-8 }} |
|||
* {{citation |last=ফোর |first=শেরি |title=জৈনিজম: আ গাইড ফর ফ্য পারপ্লেক্সড |url={{Google books|HMXuBQAAQBAJ|plainurl=yes}} |year=2015 |publisher=ব্লুমসবেরি অ্যাকাডেমিক |isbn=978-1-4742-2755-1 }} |
|||
* {{citation |last=গোমব্রিক |first=রিচার্ড |title=বুদ্ধিস্ট প্রিসেপ্ট অ্যান্ড প্র্যাকটিশ |url={{Google books|lqp4LuZQnHsC|plainurl=yes}} |year=2012|publisher=রটলেজ |isbn=978-1-136-15623-6 }} |
|||
* {{citation |last=গোপাল |first=মদন |editor-last=গৌতম |editor-first=কে. এস. |title=ইন্ডিয়া থ্রু দি এজেস |year=1990 |publisher=প্রকাশনা বিভাগ, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক, ভারত সরকার}} |
|||
* {{citation |last=গঘ |first=এলান |title=শেডস অফ এনলাইটেনমেন্ট: আ জৈন তান্ত্রিক ডায়াগ্রাম অ্যান্ড দ্য কালার্স অফ দ্য তীর্থংকরস, ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ জৈন স্টাডিজ |year=2012 |volume=৮ |number=১ |url=http://gsas.yale.edu/news/studying-jainism-and-its-tantric-ritual-diagrams-india }} |
|||
* {{citation |last=গ্র্যানোফ |first=ফিলিস |title=দ্য ভায়োলেন্স অফ নন-ভায়োলেন্স: আ স্টাডি অফ সাম জৈন রেসপন্সেস টু নন-জৈন রিলিজিয়াস প্র্যাকটিসেস |journal=দ্য জার্নাল অফ দি ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোশিয়েশন অফ বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ |volume=১৫ |year=1992 |number=১ |url=https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/jiabs/article/viewFile/8791/2698 }} |
|||
* {{citation |last=গ্রিমস |first=জন |title=আ কনসাইস ডিকশনারি অফ ইন্ডিয়ান ফিলোজফি: সংস্কৃত টার্মস ডিফাইন্ড ইন ইংলিশ | publisher=সানি প্রেস | year=1996 |location=New York |isbn=0-7914-3068-5 }} |
|||
* {{citation |last=হ্যাকেট |first=রোজালিন্ড আই. জে. |title=প্রসেলিটাইজেশন রিভিজিটেড: রাইটস টক, ফ্রি মার্কেটস অ্যান্ড কালচার ওয়ার্স |url={{Google books|ZHHXAAAAMAAJ|plainurl=yes}} |year=2008 |publisher=ইকুইনক্স অ্যাকাডেমিকস|isbn=978-1-84553-227-7 }} |
|||
* {{citation |last=হার্ভে |first=গ্রাহাম |title=রিলিজিয়নস ইন ফোকাস: নিউ অ্যাপ্রোচেস টু ট্র্যাডিশনস অ্যান্ড কনটেম্পোরারি প্র্যাকটিশেস |url={{Google books|wrTsCwAAQBAJ|plainurl=yes}} |year=2016 |publisher=রটলেজ |isbn=978-1-134-93690-8 }} |
|||
* {{citation |last=জেকবি |first=হার্মান | title=জৈন সূত্রজ (অনুবাদ) |editor =ম্যাক্সকুমার (সি সেক্রেড বুকস অফ দি ইস্ট সিরিজ, দ্বাবিংশ খণ্ড) |url=https://archive.org/stream/jainasūtrasparti029233mbp#page/n333/mode/2up |year=1964 | publisher =মোতিলাল বনারসিদাস (আদি প্রকাশক: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস)}} |
|||
* {{citation |last=হিরাকাওয়া |first=আকিরা |title=আ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান বুদ্ধিজম: ফ্রম শাক্যমুণি টু আর্লি মহাযান |url={{Google books|XjjwjC7rcOYC|plainurl=yes}} |year=1993|publisher=মোতিলাল বনারসিদাস |isbn=978-81-208-0955-0 }} |
|||
* {{citation |last=হিরিয়ান্না |first=এম. |title= আউটলাইনস অফ ইন্ডিয়ান ফিলোজফি |url={{Google books|9xGyRAjftrwC|plainurl=yes}} |year=1993|publisher=মোতিলাল বনারসিদাস|isbn=978-81-208-1086-0 }} |
|||
* {{citation |last=হপকিনস |first=এডওয়ার্ড ওয়াশবার্ন |title=দ্য রিলিজিয়নস অফ ইন্ডিয়া |url={{Google books|O0IvAAAAYAAJ|page=PA283|keywords=|text=|plainurl=yes}} |year=1902 |publisher=জিন অ্যান্ড কোম্পানি}} |
|||
* {{citation |last=ইজাওয়া |first=এ. |title=এমপ্যাথি ফর পেইন ইন বেদিক রিচুয়াল |publisher=জার্নাল অফ দি ইন্টারন্যাশনাল কলেজ ফর অ্যাডভান্সড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ, কোকুসাই বুককযোগকু দইগকুইন দাইগাকু |year=2008 |volume=১২}} |
|||
* {{citation |last=জৈন |first=চম্পৎ রাই |title=দ্য প্র্যাকটিক্যাল ধর্ম |url=https://archive.org/details/ThePracticalDharma |year=1929 |publisher=দি ইন্ডিয়ান প্রেস |quote={{PD-notice}} |ref={{sfnref|চম্পৎ রাই জৈন|১৯২৯বি}} }} |
|||
* {{citation |last1=জৈন |first1=জ্যোতীন্দ্র |authorlink=জ্যোতীন্দ্র জৈন |last2=ফিশার |first2=এবারহার্ড |authorlink2=এবারহার্ড ফিশার |title=জৈন আইকনোগ্রাফি |url={{Google books|gFZ7vQ2jwlEC|plainurl=yes}} |date=1978 |publisher=ব্রিল |volume=১২ |isbn=978-90-04-05259-8 }} |
|||
* {{citation |last=জৈন |first=কৈলাশ চন্দ|title=লর্ড মহাবীর অ্যান্ড হিজ টাইমস |url={{Google books|8-TxcO9dfrcC|plainurl=yes}} |date=1991 |publisher=মোতিলাল বনারসিদাস|isbn=978-81-208-0805-8 |ref={{sfnref|কৈলাস চন্দ জৈন|১৯৯১}} }} |
|||
* {{citation |last=জৈন |first=এস. এ. |title=রিয়ালিটি (শ্রীমৎ পূজ্যপাদাচার্যের সর্বার্থসিদ্ধির ইংরেজি অনুবাদ) |date=1992 |origyear=১ম সংস্করণ ১৯৬০ |publisher=জ্বালামালিনী ট্রাস্ট |url=https://archive.org/details/Reality_JMT |edition=২য় |quote={{PD-notice}} |ref={{sfnref|এস. এ. জৈন|১৯৯২}} }} |
|||
* {{citation |last=জৈন |first=শান্তি লাল |title=এবিসি অফ জৈনিজম |url=https://archive.org/details/abcofjainismcomp0000jain/page/51 |year=1998 |publisher=জ্ঞানোদয় বিদ্যাপীঠ|isbn=978-81-7628-000-6 |ref={{sfnref|শান্তি লাল জৈন|১৯৯৮}} }} |
|||
* {{citation |last=জৈন |first=বিজয় কে. |title=আচার্য উমাস্বামী’জ তত্ত্বার্থসূত্র |date=2011 |publisher=বিকল্প প্রিন্টার্স |isbn=978-81-903639-2-1 |edition=1st |url={{Google books|zLmx9bvtglkC|plainurl=yes}} |quote={{PD-notice}} |ref={{sfnref|বিজয় কে. জৈন|২০১১}}}} |
|||
* {{citation |last=জৈন |first=বিজয় কে. |title=আচার্য অমৃতচন্দ্র’জ পুরুষার্থ সিদ্ধ্যুপায়: রিয়েলাইজেশন অফ দ্য পিয়র সেলফ, উইথ হিন্দি অ্যান্ড ইংলিশ ট্রান্সলেশন |url={{Google books|4iyUu4Fc2-YC|plainurl=yes}} |date=2012 |publisher=বিকল্প প্রিন্টার্স |isbn=978-81-903639-4-5 |quote={{PD-notice}} |ref={{sfnref|বিজয় কে. জৈন|২০১২}} }} |
|||
* {{citation |last=জৈন |first=বিজয় কে. |title= আচার্য অমৃতচন্দ্র’জ দ্রব্যসংগ্রহ |url={{Google books|g9CJ3jZpcqYC|plainurl=yes}} |date=2013 |quote={{PD-notice}} |publisher= বিকল্প প্রিন্টার্স |isbn=978-81-903639-5-2 |ref={{sfnref|বিজয় কে. জৈন|২০১৩}} }} |
|||
* {{citation |last=জৈন |first=বিজয় কে. |title=আচার্য সামন্তভদ্র’জ রত্নকরন্দক-শ্রাবকাচার: দ্য জুয়েল-ক্যাসকেট অফ হাউজহোল্ডার’স কনডাক্ট |date=2016 |publisher=বিকল্প প্রিন্টার্স |isbn=978-81-903639-9-0 |url={{Google books|87AnDAAAQBAJ|plainurl=yes}} |quote={{PD-notice}} |ref={{sfnref|বিজয় কে. জৈন|২০১৬}} }} |
|||
* {{citation |last=জৈনি |first=পদ্মনাভ |editor-last=ডনিগার |editor-first=ওয়েন্ডি |title=কর্ম অ্যান্ড রিবার্থ ইন ক্ল্যাসিক্যাল ইন্ডিয়ান ট্র্যাডিশনস |url={{Google books|4WZTj3M71y0C|plainurl=yes}} |year=1980 |publisher=ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস|isbn=978-0-520-03923-0 }} |
|||
* {{citation |last=Jaini |first=Padmanabh S. |authorlink=Padmanabh Jaini |title=Gender and Salvation: Jaina Debates on the Spiritual Liberation of Women |url={{Google books|GRA-uoUFz3MC|plainurl=yes}} |date=1991 |isbn=978-0-520-06820-9 |publisher=University of California Press }} |
|||
* {{citation |last=জৈনি |first=পদ্মনাভ এস. |title=দ্য জৈন পাথ অফ পিউরিফিকেশন |url={{Google books|wE6v6ahxHi8C|plainurl=yes}} |date=1998 |origyear=1979 |publisher=[[মোতিলাল বনারসিদাস]] |location=Delhi |isbn=978-81-208-1578-0 }} |
|||
* {{citation |editor-last=জৈনি |editor-first=পদ্মনাভ এস. |title=কালেক্টেড পেপারস অন জৈন স্টাডিজ |url={{Google books|HPggiM7y1aYC|plainurl=yes}} |date=2000 |publisher=[[মোতিলাল বনারসিদাস]] |location=দিল্লি |edition=১ম |isbn=978-81-208-1691-6 }} |
|||
* {{citation |last=জম্বুবিজয় |first=মুনি |year=2002|title=এসেজ ইন জৈন ফিলোজফি অ্যান্ড রিলিজিয়ন |editor=পিয়ত্র বালসারোউইকজ ও মারেক মেজর | publisher=মোতিলাল বনারসিদাস|isbn=978-81-208-1977-1 }} |
|||
* {{citation |last1=জান্সমা |first1=রুডি |last2=জৈন |first2=স্নেহ রানি |title=ইন্ট্রোডাকশন টু জৈনিজম |date=2006 |publisher=প্রাকৃত ভারতী অ্যাকাডেমি |location=জয়পুর |url={{Google books|lYLXAAAAMAAJ|plainurl=yes}} |isbn=978-81-89698-09-6 }} |
|||
* {{citation |last=জনসন |first=ডব্লিউ. জে. |title=হার্মলেস সোলস: কার্মিক বন্ডেজ অ্যান্ড রিলিজিয়াস চেঞ্জ ইন আর্লি জৈনিজম উইথ স্পেশাল রেফারেন্স টু উমাস্বাতী অ্যান্ড কুন্দকুন্দ |url={{Google books|vw8OUSfQbV4C|plainurl=yes}}|year=1995 |publisher=মোতিলাল বনারসিদাস|isbn=978-81-208-1309-0 }} |
|||
* {{citation |last=জনস্টন |first=উইলিয়াম এম. |title=এনসাইক্লোপিডিয়া অফ মনাস্টিসিজিম: এ–এল |url={{Google books|GfC0TDkJJNgC|plainurl=yes}} |year=2000|publisher=রটলেজ |isbn=978-1-57958-090-2 }} |
|||
* {{citation |last1=জোনস |first1=কনস্ট্যান্স |last2=রায়ান |first2=জেমস ডি. |title=এনসাইক্লোপিডিয়া অফ হিন্দুইজম |url={{Google books|OgMmceadQ3gC|plainurl=yes}} |year=2007 |publisher=ইনফোবেস পাবলিশিং |isbn=978-0-8160-5458-9 }} |
|||
* {{citation |last=জোনস |first=লিন্ডসে |title=এনসাইক্লোপিডিয়া অফ রিলিজিয়ন |date=2005 |publisher=ম্যাকমিলান রেফারেন্স|isbn=978-0-02-865733-2 |url={{Google books|0jMOAQAAMAAJ|plainurl=yes}} |ref={{sfnref|লিন্ডসে জোনস|২০০৫}} }} |
|||
* {{citation |last=জুয়েরগেনসমেয়ার |first=মার্ক |title=দি অক্সফোর্ড হ্যান্ডবুক অফ গ্লোবাল রিলিজিয়ন |url={{Google books|EsMVDAAAQBAJ|plainurl=yes}} |year=2011|publisher=অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস|isbn=978-0-19-976764-9 }} |
|||
* {{citation |last=কেল্টিং |first=এম. হুইটনি |title=হিরোইক ওয়াভস রিচুয়ালস, স্টোরিজ অ্যান্ড দ্য ভার্চুজ অফ জৈন ওয়াইফহুড |url={{Google books|-txAd-dK0tEC|plainurl=yes}} |year=2009 |publisher=অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস |isbn=978-0-19-973679-9 }} |
|||
* {{citation |last1=কেওন |first1=দামিয়েন |last2=প্রেবিশ |first2=চার্লস এস. |title=এনসাইক্লোপিডিয়া অফ বুদ্ধিজম |url={{Google books|NFpcAgAAQBAJ|page=PA127|keywords=|text=|plainurl=yes}} |year=2013 |publisher=রটলেজ |isbn=978-1-136-98588-1 }} |
|||
* {{citation |editor-first=ট্রুডি |editor-last=রিং |editor-last2=ওয়াটসন |editor-first2=নোয়েল |editor-last3=শেলিংগার |editor-first3=পল |title=এশিয়া অ্যান্ড ওশিয়ানিয়া: ইন্টারন্যাশনাল ডিকশনারি অফ হিস্টোরিক প্লেসেস |year=1996 |publisher=রটলেজ |isbn=978-1-884964-04-6}} |
|||
* {{citation |last=কিশোর |first=কণিকা |date=2015-06-16 |title=সিম্বল অ্যান্ড ইমেজ ওয়ারশিপ ইন জৈনিজম |journal=ইন্ডিয়ান হিস্টোরিক্যাল রিভিউ |language=en |volume=৪২ |issue=১ |pages=১৭–৪৩ |doi=10.1177/0376983615569814 |s2cid=151841865 |df=dmy-all}} |
|||
* {{citation |last1=কুলকে |first1=হারমান |last2=রদারমান্ড |first2=ডায়েটমার |title=আ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া |url={{Google books|RoW9GuFJ9GIC|plainurl=yes}} |year=2004 |publisher=রটলেজ |isbn=978-0-415-32920-0 }} |
|||
* {{citation |last=কুমার |first=সহদেব |title=আ থাউজ্যান্ড পেটালড লোটাস: জৈন টেম্পলস অফ রাজস্থান: আর্কিটেকচার অ্যান্ড আইকনোগ্রাফি |url={{Google books|nSDACkmA_ukC|plainurl=yes}} |publisher=অভিনব পাবলিকেশনস |date=2001 |isbn=978-81-7017-348-9 |ref={{sfnref|সহদেব কুমার|২০০১}} }} |
|||
* {{citation |last=লকটেফেল্ড |first=জেমস জি. |title=দি ইলাস্ট্রেটেড এনসাইক্লোপিডিয়া অফ হিন্দুইজম: এ–এম |url={{Google books|5kl0DYIjUPgC|plainurl=yes}} |date=2002 |publisher=দ্য রসেন পাবলিশিং গ্রুপ |volume=১ |isbn=978-0-8239-3179-8 }} |
|||
* {{citation |last=লকটেফেল্ড |first=জেমস জি. |title=দি ইলাস্ট্রেটেড এনসাইক্লোপিডিয়া অফ হিন্দুইজম: এন–জেড |volume=২ |year=2002|publisher= দ্য রসেন পাবলিশিং গ্রুপ |isbn=978-0-8239-2287-1|url={{Google books|g6FsB3psOTIC|plainurl=yes}} }} |
|||
* {{citation |last=লং |first=জেফরি ডি. |authorlink=জেফরি ডি. লং |title=জৈনিজম: অ্যান ইন্ট্রোডাকশন |url={{Google books|ajAEBAAAQBAJ|plainurl=yes}} |year=2009 |publisher=আই. বি. টরিস |isbn=978-0-85773-656-7}} |
|||
* {{citation |last=লং |first=জেফরি ডি. |title=জৈনিজম: অ্যান ইন্ট্রোডাকশন |year=2013 |publisher=আই. বি. টরিস |isbn=978-0-85771-392-6}} |
|||
* {{citation |last=লরেনজেন | first=ডেভিড এন. | title=ওয়ারিয়র এসেটিকস ইন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি | journal=জার্নাল অফ দি আমেরিকান ওরিয়েন্টাল সোসাইটি | volume=৯৮ | issue=১ | pages=৬১–৭৫ | year=1978 | doi=10.2307/600151 | jstor=600151 }} |
|||
* {{citation |last1=মার্কহ্যাম |first1=ইয়ান এস. |last2=লোর |first2=ক্রিস্টি |title=আ ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়নস রিডার |url={{Google books|JdNNz1jcN9cC|plainurl=yes}} |year=2009|publisher=জন উইলি অ্যান্ড সনস |isbn=978-1-4051-7109-0 }} |
|||
* {{citation |last=মতিলাল |first=বিমল কৃষ্ণ |title=লজিক, ল্যাংগুয়েজ অ্যান্ড রিয়েলিটি: ইন্ডিয়ান ফিলোজফি অ্যান্ড কনটেম্পোরারি ইস্যুজ |url={{Google books|V8SLH7ogB9oC|plainurl=yes}} |year=1990|publisher=মোতিলাল বনারসিদাস |isbn=978-81-208-0717-4 }} |
|||
* {{citation |last=মতিলাল |first=বিমল কৃষ্ণ |editor-last=গনেরি |editor-first=জোনার্ডন |editor-last2=তিওয়ারি |editor-first2=হিরামন |title=দ্য ক্যারেক্টার অফ লজিক ইন ইন্ডিয়া |url={{Google books|NzZRu12ngLAC|plainurl=yes}} |year=1998 |publisher=স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ইয়র্ক প্রেস |isbn=978-0-7914-3739-1 }} |
|||
* {{citation |last=ম্যাকফাউল |first=টমাস আর. |title=দ্য ফিউচার অফ পিস অ্যান্ড জাস্টিস ইন দ্য গ্লোবাল ভিলেজ: দ্য রোল অফ দ্য ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়নস ইন দ্য টোয়েন্টি-ফার্স্ট সেঞ্চুরি |url={{Google books|V_XCDYzE8qsC|plainurl=yes}} |year=2006 |publisher=গ্রিনউড পাবলিশিং |isbn=978-0-275-99313-9 }} |
|||
* {{citation |editor-last=মেল্টন |editor-first=জে. গর্ডন |editorlink=জে. গর্ডন মেল্টন |title=রিলিজিয়াস সেলিব্রেশনস: অ্যান এনসাইক্লোপিডিয়া অফ হলিডেজ, ফেস্টিভ্যালস, সলেম অবজার্ভেন্স, অ্যান্ড স্পিরিচুয়াল কোমেমোরেশন |volume=১ |url={{Google books|KDU30Ae4S4cC|plainurl=yes}} |publisher=এবিসি-ক্লিও |date=2011 |isbn=978-1-59884-206-7 }} |
|||
* {{citation |editor-last=মেল্টন |editor-first=জে. গর্ডন |editor-last2=বাউমান |editor-first2=মার্টিন |title=রিলিজিয়নস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড: আ কমপ্রিহেনসিভ এনসাইক্লোপিডিয়া অফ বিলিফস অ্যান্ড প্র্যাকটিশেস |url={{Google books|v2yiyLLOj88C|plainurl=yes}} |edition=২য় |volume=এক: এ–বি |publisher=এবিসি-ক্লিও |date=2010 |isbn=978-1-59884-204-3 }} |
|||
* {{citation |last=মিশেল |first=জর্জ আই |title=টেম্পল আর্কিটেকচার অ্যান্ড আর্ট অফ দি আর্লি চালুক্যজ: বাদামি, মহাকূট, আইহোল, পাট্টাডাকাল |url={{Google books|-1TroAEACAAJ|plainurl=yes}} |year=2014 |publisher=নিয়োগি বুকস |isbn=978-93-83098-33-0 }} |
|||
* {{citation |last1=মিশ্র |first1=সুসান বর্মা |first2=হিমাংশু প্রভা |last2=রায় |title=দি আর্কিওলজি অফ সেক্রেড স্পেসেজ: দ্য টেম্পলস ইন ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়ান, ২এন্ড সেঞ্চুরি বিসিই–৮থ সেঞ্চুরি সিই |url={{Google books|CtDLDAAAQBAJ|plainurl=yes}}|year=2016|publisher=রটলেজ |isbn=978-1-317-19374-6 }} |
|||
* {{citation |last=মুখোপাধ্যায় |first=রাধাকুমুদ |authorlink=রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় |title=চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য অ্যান্ড হিজ টাইমস |url={{Google books|i-y6ZUheQH8C|plainurl=yes}} |edition=৪র্থ |year=1988 |origyear=first published in 1966 |publisher=[[মোতিলাল বনারসিদাস]] |isbn=978-81-208-0433-3 }} |
|||
* {{citation |editor-last=মুগাম্বি |editor-first=জে. এন. কে. |editor-link=জেসি মুগাম্বি |title=আ কমপেয়ারেটিভ স্টাডি অফ রিলিজিয়নস |edition=২য় |url={{Google books|cx8ACQAAQBAJ|plainurl=yes}} |publisher=ইউনিভার্সিটি অফ নাইরোবি প্রেস |date=2010 |orig-year=1990 |isbn=978-9966-846-89-1 }} |
|||
* {{citation |last=নায়ানার |title=গাথা ১.২৯|year=২০০৫}} |
|||
* {{citation |last=নিলিস |first=জেসন |title=আর্লি বুদ্ধিস্ট ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ট্রেড নেটওয়ার্কস: মোবিলিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ উইথইন অ্যান্ড বিয়ন্ড দ্য নর্থওয়েস্টার্ন বর্ডারল্যান্ডস অফ সাউথ এশিয়া |url={{Google books|GB-JV2eOr2UC|plainurl=yes}} |year=2010 |publisher=ব্রিল অ্যাকাডেমিক |isbn=978-90-04-18159-5 }} |
|||
* {{citation | last1=নেমিচন্দ্র |first1=আচার্য |last2=বলবীর |first2=নলিনী | title=দ্রব্যসংগ্রহ: এক্সপোজিশন অফ দ্য সিক্স সাবস্টেন্সেস |publisher =[[হিন্দি গ্রন্থ কার্যালয়]] | year=2010 | location=মুম্বই | version=(প্রাকৃত ও সংস্কৃত) পণ্ডিত নাথুরাম প্রেমী রিসার্চ সিরিজ (খণ্ড ১৯) | isbn=978-81-88769-30-8 }} |
|||
* {{citation |last=নেসফিল্ড |first=জন কলিনসন |title=ব্রিফ ভিউ অফ দ্য কাস্ট সিস্টেম অফ দ্য নর্থ-ওয়েস্টার্ন প্রভিন্সেস অ্যান্ড অবধ |url={{Google books|nuU-AAAAYAAJ|plainurl=yes}} |year=1885|publisher=উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অবধ সরকার প্রেস}} |
|||
* {{citation |last=ওলসন |first=কার্ল | title=দ্য কনফ্লিক্টিং থিমস অফ ননভায়োলেন্স অ্যান্ড ভায়োলেন্স ইন এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়ান এসেটিজম অ্যাজ এভিডেন্ট ইন দ্য প্র্যাকটিশ অফ ফাস্টিং | journal=ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ ধর্ম স্টাডিজ | volume=১ | issue=২ | pages=১ | year=2014 | doi=10.1186/2196-8802-2-1 | doi-access=free }} |
|||
* {{citation |last=ওয়েন |first=লিসা |author-link=লিসা ওয়েন |title=কার্ভিং ডিভোশন ইন দ্য জৈন কেভস অ্যাট ইলোরা |url={{Google books|MUszAQAAQBAJ|plainurl=yes}} |publisher=ব্রিল |date=২০১২এ |isbn=978-90-04-20629-8 }} |
|||
* {{citation |last=ওয়েন |first=লিসা |author-link=লিসা ওয়েন |title=কার্ভিং ডিভোশন অফ দ্য জৈন কেভস অ্যাট ইলোরা |url={{Google books|vHK2WE8xAzYC|plainurl=yes}} |year=২০১২বি |publisher=ব্রিল Academic |isbn=978-90-04-20629-8 }} |
|||
* {{citation |last=পাল |first=প্রতাপাদিত্য |authorlink=প্রতাপাদিত্য পাল |title=ইন্ডিয়ান স্কাল্পচার: সিরকা ৫০০ বি.সি.–এ.ডি. ৭০০|url={{Google books|clUmKaWRFTkC|plainurl=yes}} |publisher=লস এঞ্জেলেস কান্ট্রি মিউজিয়াম অফ আর্ট, [[ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস]] |date=1986 |volume=1 |isbn=978-0-87587-129-5 |ref={{sfnref|প্রতাপাদিত্য পাল|১৯৮৬}} }} |
|||
* {{citation |last=পান্ডে |first=গোবিন্দ |title=স্টাডিজ ইন দি অরিজিনস অফ বুদ্ধিজম |url={{Google books|__1kiAonBzIC|plainurl=yes}} | year=1957| publisher=মোতিলাল বনারসিদাস (পুনর্মুদ্রণ: ১৯৯৫) |isbn=978-81-208-1016-7 }} |
|||
* {{citation |last=পাণ্ডে |first=জনার্দন |url={{Google books|lmJnWrjnfjMC|plainurl=yes}} |date=1998 |title=গান্ধী অ্যান্ড ২১র্স্ট সেঞ্চুরি |isbn=978-81-7022-672-7 |ref={{sfnref|জনার্দন পাণ্ডে|১৯৯৮}} }} |
|||
* {{citation|url={{Google books|bBd_BAAAQBAJ|plainurl=yes}}|title=ইন্ডিয়ান ফিলাটেলি ডাইজেস্ট |first=প্রশান্ত এইচ. |last=পাণ্ড্য |date=2014}} |
|||
* {{citation |editor-last=পেশিলিস |editor-first=কারেন |editor-last2=রাজ |editor-first2=সেলভা জে. |title=সাউথ এশিয়ান রিলিজিয়নস: ট্র্যাডিশনস অ্যান্ড টুডে |url={{Google books|kaubzRxh-U0C|plainurl=yes}} |publisher=রটলেজ |date=2013 |isbn=978-0-203-07993-5 }} |
|||
* {{citation |last=পেরেইয়া |first=জোস |title=মনোলিথিক জিনাস |url={{Google books|LMTgiygj4-oC|page=PA24|keywords=|text=|plainurl=yes}} |year=1977 |publisher=মোতিলাল বনারসিদাস|isbn=978-81-208-2397-6 }} |
|||
* {{citation |last=পেরেট |first=রয় ডব্লিউ. |title=ফিলোজফি অফ রিলিজিয়ন: ইন্ডিয়ান ফিলোজফি| url={{Google books|edhYAQAAQBAJ|plainurl=yes}}| year=2013| publisher=রটলেজ | isbn=978-1-135-70322-6 }} |
|||
* {{citation |last=পোপ |first=জর্জ উগ্লো |title=আ টেক্সট-বুক অফ ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি |url={{Google books|xpABAAAAQAAJ|plainurl=yes}} |year=1880|publisher=ডব্লিউ. এইচ. অ্যালেন অ্যান্ড কোম্পানি}} |
|||
* {{citation |last=প্রাইস |first=জোয়ান |title=সেক্রেড স্ক্রিপচার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়ন: অ্যান ইন্ট্রোডাকশন|url={{Google books|J0eycqQq9U4C|plainurl=yes}} |year=2010|publisher=ব্লুমসবেরি অ্যাকাডেমিকস|isbn=978-0-8264-2354-2 }} |
|||
* {{citation |editor-last=কিউভার্রস্টর্ম |editor-first=ওলি |title=জৈনিজম অ্যান্ড আর্লি বুদ্ধিজম: এসেজ ইন অনর অফ পদ্মনাভ এস. জৈনি |url={{Google books|5_EdL2FtIqQC|plainurl=yes}} |year=2003 |publisher=জৈন পাবলিশিং কোম্পানি|isbn=978-0-89581-956-7 }} |
|||
* {{citation |last1=র্যানকিং |first1=আইড্যান ডি. |last2=মারদিয়া |first2=কান্তিলাল|authorlink2=কান্তিলাল মারদিয়া |title=লিভিং জৈনিজম: অ্যান এথিক্যাল সায়েন্স |url={{Google books|bQxZAQAAQBAJ|plainurl=yes}} |date=2013 |publisher=জন হান্ট পাবলিশিং |isbn=978-1-78099-911-1 }} |
|||
* {{citation |last=রবিনসন |first=টমাস আর্থার |title=ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়নস |url={{Google books|20DBvovDC0QC|plainurl=yes}} |publisher=[[হিমস এনশিয়েন্ট অ্যান্ড মডার্ন| হিমস এনশিয়েন্ট অ্যান্ড মডার্ন লিমিটেড]]|date=2006|isbn=978-0-334-04014-9}} |
|||
* {{citation |last1=রুডলফ |first1=লয়েড আই. |last2=রুডলফ |first2=সুসান হোয়েবার |title=দ্য মডার্নিটি অফ ট্র্যাডিশন: পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট ইন ইন্ডিয়া |url={{Google books|7guY1ut-0lwC|plainurl=yes}} |date=1984 |publisher=ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগো প্রেস |isbn=978-0-226-73137-7 }} |
|||
* {{cite thesis |last=সল্টার |first=এমা |url=http://eprints.hud.ac.uk/id/eprint/9211/|title=রাজ ভক্ত মার্গ: দ্য পাথ অফ ডিভোশন টু শ্রীমদ রাজচন্দ্র। আ জৈন কমিউনিটি অফ দ্য টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি |date=September 2002 |type= Doctoral thesis |chapter= |institution= ইউনিভার্সিটি অফ ওয়েলস |docket= |oclc= |access-date=2018-09-21|via=ইউনিভার্সিটি অফ হাডারসফিল্ড রেপোসিটরি |pages=১২৫–১৫০}} |
|||
* {{citation |last=সালভাডোরি |first=সিন্থিয়া |title=থ্রু ওপেন ডোরস |url={{Google books|4xIRAQAAIAAJ|plainurl=yes}}|year=1989|publisher=কেনওয়ে |isbn=978-9966-848-05-5 }} |
|||
* {{citation |last=সাংগাভে |first=বিলাস আদিনাথ |authorlink=বিলাস আদিনাথ সাংগাভে |title=জৈন কমিউনিটি: আ সোশ্যাল সার্ভে |url={{Google books|FWdWrRGV_t8C|plainurl=yes}} |date=1980 |publisher=[[পপুলার প্রকাশন]] |location=বোম্বে |edition=২য় |isbn=978-0-317-12346-3 }} |
|||
* {{citation |last=সাংগাভে |first=বিলাস আদিনাথ |title=ফ্যাসেটস অফ জৈনোলজি: সিলেক্টেড রিসার্চ পেপার্স অন জৈন সোসাইটি, রিলিজিয়ন, অ্যান্ড কালচার |url={{Google books|QzEQJHWUwXQC|plainurl=yes}} |date=2001 |publisher=[[পপুলার প্রকাশন]] |location=মুম্বই |isbn=978-81-7154-839-2 }} |
|||
* {{citation |last=সাংগাভে |first=বিলাস আদিনাথ |title=অ্যাসপেক্টস অফ জৈন রিলিজিয়ন |url={{Google books|8UhvGRoyAqMC|plainurl=yes}} |edition=৫ |date=2006 |origyear=1990 |publisher=[[ভারতীয় জ্ঞানপীঠ]] |isbn=978-81-263-1273-3 }} |
|||
* {{citation |last=সরস্বতী |first=দয়ানন্দ |author-link=দয়ানন্দ সরস্বতী |title=অ্যান ইংলিশ ট্র্যানসলেশন অফ সত্যার্থ প্রকাশ (১৯৭০ সালে পুনর্মুদ্রিত)|year=1908| url=https://archive.org/stream/satyarthprakashl00dayauoft#page/n467/mode/2up|publisher=লাহোর : বীরগণান্দ প্রেস}} |
|||
* {{citation |last=শেঠিয়া |first=তারা |title=অহিংসা, অনেকান্ত অ্যান্ড জৈনিজম |url={{Google books|QYdlKv8wBiYC|plainurl=yes}} |date=2004 |publisher=[[মোতিলাল বনারসিদাস]] |isbn=978-81-208-2036-4 }} |
|||
* {{citation |last=সেট্টার |first=এস. |editor-last=ঈশ্বরন |editor-first=কে. |title=ইনভাইটিং ডেথ: ইন্ডিয়ান অ্যাটিচিউড টুওয়ার্ডস রিচুয়াল ডেথ |url={{Google books|vmc3vs5Ija0C|plainurl=yes}} |date=1989 |publisher=ই. জে. ব্রিল |isbn=90-04-08790-7 }} |
|||
* {{citation |last=সিং |first=রাম ভূষণ প্রসাদ |title=জৈনিজম ইন আর্লি মিডিয়াভাল কর্ণাটক |url={{Google books|JtWGm4E4qZIC|plainurl=yes}} |date=2008 |origyear=1975 |publisher=[[মোতিলাল বনারসিদাস]] |isbn=978-81-208-3323-4 |ref={{sfnref|রাম ভূষণ প্রসাদ সিং|২০০৮}} }} |
|||
* {{citation |last=সিং |first=উপিন্দর |author-link=উপিন্দর সিং |title=আ হিস্ট্রি অফ এনশিয়েন্ট অ্যান্ড আর্লি মিডিয়াভাল ইন্ডিয়া: ফ্রম দ্য স্টোন এজ টু দ্য ১২থ সেঞ্চুরি |url={{Google books|Pq2iCwAAQBAJ|plainurl=yes}} |publisher=[[পিয়ারসন এডুকেশন]] |date=2016 |isbn=978-93-325-6996-6 |ref={{sfnref|উপিন্দর সিং|২০১৬}} }} |
|||
* {{citation |last=শাহ |first=নাথুভাই |title=জৈনিজম: দ্য ওয়ার্ল্ড অফ কনকারার্স |url={{Google books|g120RG8GkHAC|plainurl=yes}} |volume=২ |year=1998 |publisher=সাসেক্স অ্যাকাডেমিক প্রেস |isbn=978-1-898723-31-8 |ref={{sfnref|নাথুভাই শাহ|১৯৯৮}} }} |
|||
* {{citation |last=শাহ |first=নাথুভাই |title=জৈনিজম: দ্য ওয়ার্ল্ড অফ কনকারার্স |url={{Google books|qLNQKGcDIhsC|plainurl=yes}} |volume=এক |date=2004 |origyear=১৯৯৮ সালে প্রথম প্রকাশিত |publisher=[[মোতিলাল বনারসিদাস]] |isbn=978-81-208-1938-2 |ref={{sfnref|নাথুভাই শাহ|২০০৪}} }} |
|||
* {{citation |last=শাহ |first=উমাকান্ত প্রেমানন্দ |author-link=উমাকান্ত প্রেমানন্দ শাহ |title=জৈন-রূপ-মণ্ডন: জৈন আইকনোগ্রাফি |url={{Google books|m_y_P4duSXsC|plainurl=yes}} |date=1987 |publisher=অভিনব পাবলিকেশনস |isbn=978-81-7017-208-6 |ref={{sfnref|উমাকান্ত পি. শাহ|১৯৮৭}} }} |
|||
* {{citation |last1=শর্মা |first1=রমেশ চন্দ্র |last2=ঘোষাল |first2=প্রণতি |title=জৈন কনট্রিবিউশন টু বারাণসী |url={{Google books|YoLXAAAAMAAJ|plainurl=yes}} |year=2006 |publisher=জ্ঞানপ্রবাহ |isbn=978-81-246-0341-3 }} |
|||
* {{citation |last1=শ |first1=জেফরি এম. |last2=ডেমি |first2=টিমোথি জে. |title=ওয়ার অ্যান্ড রিলিজিয়ন: অ্যান এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ফেইথ অ্যান্ড কনফ্লিক্ট |url={{Google books|KDlFDgAAQBAJ|plainurl=yes}} |year=2017 |publisher=এবিসি-ক্লিও |isbn=978-1-61069-517-6 }} |
|||
* {{citation |last=সিনহা |first=যদুনাথ |title=ইন্ডিয়ান সাইকোলজি |url=https://www.google.com/books/edition/Indian_Psychology/VCwmmWXJBqEC |year=1944 }} |
|||
* {{citation |last1=সলোমন |first1=রবার্ট সি. |last2=হিগিনস |first2=ক্যাথলিন এম. |title=আ প্যাশন ফর উইসডম: আ ভেরি ব্রিফ হিস্ট্রি অফ ফিলোজফি |url={{Google books|btIm8_a8Ol8C|plainurl=yes}} |year=1998 |publisher=অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস |isbn=978-0-19-511209-2 }} |
|||
* {{citation |last=সোনি |first=জয়ন্দ্র |title=বেসিক জৈন এপিস্টেমোলজি |journal=ফিলোজফি ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট |volume=৫০ |issue=৩ |pages=৩৬৭–৩৭৭ |year=2000 |jstor=1400179}} |
|||
* {{citation |last=সুনবল |first=এ. জে. |title=আদর্শ সাধু: অ্যান আইডিয়াল মংক |url={{Google books|oUU4AAAAIAAJ|page=PA91|keywords=|text=|plainurl=yes}} |year=1934 |publisher=কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস|isbn=978-1-001-40429-5 }} |
|||
* {{citation |editor-last=সুন্দররাজন |editor-first=কে. আর. |editor-last2=মুখোপাধ্যায় |editor-first2=বীথিকা |title=হিন্দু স্পিরিচুয়ালিটি: পোস্টক্ল্যাসিকাল অ্যান্ড মডার্ন |url=https://books.google.com/books?id=UUWIEfAY-mMC |year=1997 |publisher=[[মোতিলাল বনারসিদাস]] |isbn=978-81-208-1937-5 |chapter=২০ }} |
|||
* {{citation |last=শোয়ার্ৎজ |first=উইলিয়াম অ্যান্ড্রিউ |title=দ্য মেটাফিজিক্স অফ প্যারাডক্স: জৈনিজম, অ্যাবসোলিউট রিলেটিভিটি, অ্যান্ড রিলিজিয়াস প্লুরালিজম |date=2018 |publisher=লেক্সিংটন বুকস |isbn=978-1-4985-6392-5 |url=https://rowman.com/ISBN/9781498563925/The-Metaphysics-of-Paradox-Jainism-Absolute-Relativity-and-Religious-Pluralism |access-date=23 August 2018 |archive-url=https://web.archive.org/web/20180824002257/https://rowman.com/ISBN/9781498563925/The-Metaphysics-of-Paradox-Jainism-Absolute-Relativity-and-Religious-Pluralism |archive-date=24 August 2018 |url-status=live |df=dmy-all }} |
|||
* {{citation |last=টেলর |first=ব্রোন |author-link=ব্রোন টেলর |title=এনসাইক্লোপিডিয়া অফ রিলিজিয়ন অ্যান্ড নেচার |url={{Google books|i4mvAwAAQBAJ|plainurl=yes}} |year=2008 |publisher=ব্লুমসবেরি অ্যাকাডেমিক |isbn=978-1-4411-2278-0}} |
|||
* {{citation |last=টিৎজে |first=কার্ট |title=জৈনিজম: আ পিক্টোরিয়াল গাইড টু দ্য রিলিজিয়ন অফ নন-ভায়োলেন্স |url={{Google books|loQkEIf8z5wC|plainurl=yes}} |publisher=[[মোতিলাল বনারসিদাস]] |edition=২ |date=1998 |isbn=978-81-208-1534-6 }} |
|||
* {{citation |last=ট্রাশকে |first=অড্রে |date=2015-09-01 |title=ডেঞ্চারাস ডিবেটস: জৈন রেসপন্স টু থিওলজিক্যাল চ্যালেঞ্জেস অ্যাট দ্য মুঘল কোর্ট |journal=মডার্ন এশিয়া স্টাডিজ |volume=৪৯ |issue=৫ |pages=১৩১১–১৩৪৪ |doi=10.1017/S0026749X14000055 |s2cid=146540567 |issn=0026-749X |df=dmy-all |url=https://semanticscholar.org/paper/6fd3bf9e1dbf7a4bbe281695dc8cc75aaaada336 }} |
|||
* {{citation |last=টু্কোল |first=বিচারপতি টি. কে. |authorlink=টি. কে. টুকোল|title=সল্লেখনা ইজ নট সুইসাইড |date=1976 |publisher=এল. ডি. ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডোলজি |location=[[আহমেদাবাদ]] |edition=১ম |url=https://archive.org/details/SallekhanaIsNotSuicide |quote={{PD-notice}} }} |
|||
* {{citation |last=উমাস্বাতী |first=উমাস্বামী |title=দ্যাট হুইচ ইজ (অনুবাদ: নাথুমল তাতিয়া) |url={{Google books|0Rw4RwN9Q1kC|plainurl=yes}} |year=1994 |publisher=রোওম্যান অ্যান্ড লিটলফিল্ড |isbn=978-0-06-068985-8 }} |
|||
* {{citation |last=ভ্যালেলি |first=অ্যানি |title=গার্ডিয়ানস অফ দ্য ট্র্যানসেডেন্ট: অ্যান এথনোলজি অফ আ জৈন এসেটিক কমিউনিটি |url={{Google books|eI4PAY9rDmQC|plainurl=yes}} |date=2002 |publisher=ইউনিভার্সিটি অফ টরেন্টো প্রেস |isbn=978-0-8020-8415-6 }} |
|||
* {{citation |last=ভ্যালেলি |first=অ্যানি |editor-last=বুলিভ্যান্ট |editor-first=স্টিফেন |editor-last2=রুস |editor-first2=মাইকেল |title=দি অক্সফোর্ড হ্যান্ডবুক অফ এথেইজম |url={{Google books|93VoAgAAQBAJ|plainurl=yes}} |year=2013 |publisher=অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস |isbn=978-0-19-166739-8 }} |
|||
* {{citation |last=ফন গ্লাসেনাপ |first=হেলমুথ |author-link=হেলমুথ ফন গ্লাসেনাপ |others=শ্রীধর বি. শ্রোত্রী (অনুবাদ) |title=জৈনিজম: অ্যান ইন্ডিয়ান রিলিজিয়ন অফ স্যালভেশন |trans-title=Der Jainismus: Eine Indische Erlosungsreligion |url={{Google books|WzEzXDk0v6sC|plainurl=yes}} |publisher=[[মোতিলাল বনারসিদাস]] (পুনর্মুদ্রণ: ১৯৯৯) |year=1925| location=Delhi |isbn=978-81-208-1376-2 }} |
|||
* {{citation |last=ভুর্স্ট |first=রবার্ট ই. ভ্যান |author-link=রবার্ট ই. ভ্যান ভুর্স্ট |url={{Google books|mD8aCgAAQBAJ|plainurl=yes}} |title=আরইএলজি: ওয়ার্ল্ড |edition=২ |publisher=[[সেনগেজ লার্নিং]] |date=2014|isbn=978-1-285-43468-1}} |
|||
* {{citation |last=ভুর্স্ট |first=রবার্ট ই. ভ্যান |author-link=রবার্ট ই. ভ্যান ভুর্স্ট |title=আরইএলজি: ওয়ার্ল্ড |url={{Google books|37TcBAAAQBAJ|plainurl=yes}} |publisher= সেনগেজ লার্নিং |year=2015 |edition=২য় |isbn=978-1-285-43468-1 }} |
|||
* {{citation |last=উইলি |first=ক্রিস্টি এল. |title=হিস্টোরিক্যাল ডিকশনারি অফ জৈনিজম |url={{Google books|QCT-CQAAQBAJ|plainurl=yes}}|year=2004| publisher=স্কেয়ারক্রো |isbn=978-0-8108-6558-7}} |
|||
* {{citation |last=উইলি |first=ক্রিস্টি এল. |title=দি এ টু জেড অফ জৈনিজম |url={{Google books|cIhCCwAAQBAJ|plainurl=yes}} |year=2009 | volume=৩৮ |publisher=স্কেয়ারক্রো |isbn=978-0-8108-6337-8 }} |
|||
* {{citation |last=উইলিয়ামস |first=রবার্ট |title=জৈন যোগ: আ সার্ভে অফ দ্য মিডিয়াভাল শ্রাবকাচারস |url={{Google books|LLKcrIJ6oscC|plainurl=yes}} |year=1991 |publisher=[[মোতিলাল বনারসিদাস]] |isbn=978-81-208-0775-4 }} |
|||
* {{citation| last=উইন্টারনিৎজ |first=মরিজ |author-link=মরিজ উইন্টারনিৎজ |title=হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান লিটারেচার: বুদ্ধিস্ট অ্যান্ড জৈন লিটারেচার | url={{Google books|Lgz1eMhu0JsC|plainurl=yes}}| year=1993 | publisher=মোতিলাল বনারসিদাস| isbn=978-81-208-0265-0}} |
|||
* {{citation |last=ইয়ান্ডেল |first=কেইথ ই. |title=ফিলোজফি অফ রিলিজিয়ন আ কনটেম্পোরারি ইন্ট্রোডাকশন |url=https://www.google.com/books/edition/Philosophy_of_Religion/c6aHAgAAQBAJ |year=1999 }} |
|||
* {{citation |last=জিমার |first=হেইনরিখ |author-link=হেইনরিখ জিমার |editor-last=ক্যাম্পবেল |editor-first=জোসেফ |editorlink=জোসেফ ক্যাম্পবেল |title=ফিলোজফিজ অফ ইন্ডিয়া |year=1953 |orig-year=1952 |publisher=রটলেজ অ্যান্ড কেগান পল লিমিটেড |location=লন্ডন |url=https://archive.org/details/Philosophy.of.India.by.Heinrich.Zimmer |isbn=978-81-208-0739-6 }} |
|||
{{refend}} |
|||
{{Z148}} |
|||
{{Jainism topics}} |
|||
{{Religion topics}} |
|||
{{Vegetarianism}} |
|||
{{Authority control}} |
|||
[[বিষয়শ্রেণী:জৈনধর্ম| ]] |
|||
[[বিষয়শ্রেণী:দ্বৈতবাদ]] |
|||
[[বিষয়শ্রেণী:ভারতীয় ধর্ম]] |
[[বিষয়শ্রেণী:ভারতীয় ধর্ম]] |
||
[[বিষয়শ্রেণী: |
[[বিষয়শ্রেণী:মোক্ষে বিশ্বাসী ধর্ম]] |
||
[[বিষয়শ্রেণী: |
[[বিষয়শ্রেণী:নাস্তিকতাবাদ]] |
||
[[বিষয়শ্রেণী: |
[[বিষয়শ্রেণী:নিরামিশাষী ধর্ম]] |
||
[[বিষয়শ্রেণী: |
[[বিষয়শ্রেণী:ঈশ্বর-নিরপেক্ষতাবাদী ধর্ম]] |
||
১৪:০৭, ৭ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে সংশোধিত সংস্করণ

| জৈনধর্ম |
|---|
 |
|
|
জৈনধর্ম (/ˈdʒeɪnɪzəm/),[১] হল একটি প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম। ধর্মটির আধ্যাত্মিক ধ্যানধারণা ও ইতিহাসের সূত্রপাত ঘটেছিল এই ধর্মের আদি প্রবর্তক হিসেবে কথিত চব্বিশ জন তীর্থংকরের এক পরম্পরার মাধ্যমে।[২] প্রথম তীর্থংকরের নাম ঋষভনাথ। বর্তমানে তিনি "আদিনাথ ভগবান" নামেও পরিচিত। জৈনরা বিশ্বাস করেন, ঋষভনাথ জন্মগ্রহণ করেছিলেন বহু লক্ষ বছর আগে। ত্রয়োবিংশ তীর্থংকর পার্শ্বনাথ খ্রিস্টপূর্ব ৯০০ অব্দ এবং চতুর্বিংশ তীর্থংকর মহাবীর খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ অব্দ নাগাদ জন্মগ্রহণ করেন। জৈন ধর্মবিশ্বাসে এই ধর্ম হল এক চিরন্তন ধর্ম এবং তীর্থংকরগণ মহাবিশ্বের প্রতিটি চক্রে মানবসমাজকে পথ প্রদর্শন করার জন্য আবির্ভূত হয়ে থাকেন।
জৈনদের প্রধান ধর্মীয় নীতিগুলি হল অহিংসা, অনেকান্তবাদ (বহুত্ববাদ), অপরিগ্রহ (অনাসক্তি) ও সন্ন্যাস (ইন্দ্রিয় সংযম)। ধর্মপ্রাণ জৈনেরা পাঁচটি প্রধান প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন: অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (চুরি না করা), ব্রহ্মচর্য (যৌন-সংযম) ও অপরিগ্রহ। জৈন সংস্কৃতির উপর এই নীতিগুলির প্রভাব ব্যাপক। যেমন, এই নীতির ফলেই জৈনরা প্রধানত নিরামিশাষী। এই ধর্মের আদর্শবাক্য হল পরস্পরোপগ্রহো জীবনাম (আত্মার কার্য পরস্পরকে সহায়তা করা) এবং ণমোকার মন্ত্র হল জৈনদের সর্বাপেক্ষা অধিক পরিচিত ও মৌলিক প্রার্থনামন্ত্র।
জৈনধর্ম বিশ্বের প্রাচীনতম ধর্মগুলির অন্যতম। এই ধর্ম দু’টি প্রধান প্রাচীন সম্প্রদায়ে বিভক্ত: দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর। কৃচ্ছসাধনের নিয়ম, স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক এবং কোন ধর্মগ্রন্থগুলি প্রামাণ্য সেই নিয়ে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু মতভেদ রয়েছে। তবে দুই সম্প্রদায়েই ভিক্ষু সাধু ও সাধ্বীদের (সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী) ভার শ্রাবক ও শ্রাবিকারাই (গৃহী পুরুষ ও নারী) বহন করেন। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ জৈনধর্মের অনুগামী। এঁদের অধিকাংশই ভারতে বসবাস করেন। ভারতের বাইরে কানাডা, ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বহুসংখ্যক জৈন বাস করেন। জাপানেও জৈনদের জনসংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেদেশে পাঁচ হাজারেরও বেশি জাপানি পরিবার জৈনধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে। জৈনদের প্রধান উৎসবগুলির অন্যতম হল পর্যুষণ, দশলক্ষণ, অষ্টনিকা, মহাবীর জন্ম কল্যাণক ও দীপাবলি।
ধর্মবিশ্বাস ও দর্শন
জৈনধর্ম হল একটি ঈশ্বর-নিরপেক্ষতাবাদী ধর্ম। এই ধর্মের পূর্বাভাস অনুযায়ী, মহাবিশ্ব বস্তু দ্বৈতবাদের নীতিকে লঙ্ঘন না করেই বিবর্তিত হচ্ছে[৩] এবং সমান্তরালতা ও মিথষ্ক্রিয়তাবাদের মূলসূত্রের মধ্যবর্তী ভূমিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্বাহিত হচ্ছে।[৪]
দ্রব্য (বস্তু)
সংস্কৃত ভাষায় "দ্রব্য" শব্দটির অর্থ সারবস্তু বা সত্ত্বা।[৫] জৈন দর্শন অনুযায়ী, মহাবিশ্ব ছয়টি চিরন্তন দ্রব্য দ্বারা গঠিত: চেতন সত্ত্বা বা আত্মা ("জীব"), অচেতন বস্তু বা পদার্থ ("পুদ্গল"), গতির মূলসূত্র ("ধর্ম"), বিরামের মূলসূত্র ("অধর্ম"), মহাশূন্য ("আকাশ") ও সময় ("কাল")।[৬][৫] শেষোক্ত পাঁচটি দ্রব্যকে একত্রে "অজীব" (জড় পদার্থ) নামে অভিহিত করা হয়।[৫] জৈন দার্শনিকগণ একটি দ্রব্যকে একটি দেহ বা সত্ত্বার থেকে স্বতন্ত্র জ্ঞান করেন এবং দ্রব্যকে এক সাধারণ অবিনশ্বর উপাদান বলে ঘোষণা করে দেহ বা সত্ত্বাকে এক বা একাধিক দ্রব্য দ্বারা নির্মিত তথা নশ্বর যৌগ বলে উল্লেখ করেন।[৭]
তত্ত্ব (সত্য)
জৈন দর্শনে "তত্ত্ব" বলতে সত্যকে বোঝায়। এটিই মুক্তিলাভের প্রধান অবলম্বন। দিগম্বর জৈনদের মতে তত্ত্বের সংখ্যা সাত: চেতন ("জীব"), অচেতন ("অজীব"); আত্মার কর্ম-সংক্রান্ত অভ্যন্তরমুখী প্রবাহ ("আস্রব"); আত্মার কর্ম-সংক্রান্ত কণাগুলির বন্ধন ("বন্ধ");[৮][৯] কর্ম-সংক্রান্ত কণাগুলির গতিরোধ ("সম্বর"); অতীতের কর্ম-সংক্রান্ত কণাগুলির নির্মূলীকরণ ("নির্জরা") এবং মুক্তি ("মোক্ষ")। শ্বেতাম্বর জৈনরা এগুলির সঙ্গে আরও দু’টি তত্ত্বকে যোগ করেন। এগুলি হল: সৎকর্ম ("পুণ্য") ও অসৎকর্ম ("পাপ")।[১০][১১][১২] জৈন দর্শনে "তত্ত্বসমূহে বিশ্বাস"-কেই প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টি মনে করা হয়।[১১] সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে জৈনধর্মের আধ্যাত্মিক লক্ষ্য হল মোক্ষে উত্তীর্ণ হওয়া। কিন্তু অধিকাংশ জৈন গৃহীর কাছে এই লক্ষ্যটি হল সৎকর্মের মাধ্যমে উৎকৃষ্টতর পুনর্জন্ম লাভ এবং মোক্ষের পথে এক ধাপ অগ্রসর হওয়া।[১৩][১৪]
আত্মা ও কর্ম
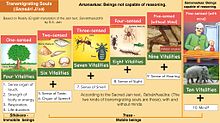
জৈনরা বিশ্বাস করেন, "প্রাচুর্যপূর্ণ ও চির-পরিবর্তনশীল আত্মা"-র অস্তিত্ব একটি স্বতঃপ্রমাণিত সত্য এবং স্বতঃসিদ্ধ বলেই এই ধারণাটির প্রমাণের কোনও প্রয়োজন নেই।[১৫] জৈন মতে, অসংখ্য আত্মার অস্তিত্ব রয়েছে; কিন্তু প্রতি আত্মারই তিনটি করে গুণ: "চৈতন্য" (চেতনা; সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ গুণ এটি), "সুখ" (পরম সুখ) ও "বীর্য" (স্পন্দনশীল শক্তি)।[১৬] তাঁরা আরও মনে করেন যে, এই বীর্যই কর্ম-সংক্রান্ত কণাগুলিকে আত্মার কাছে টেনে আনে এবং বন্ধন সৃষ্টি করে; আবার এই বীর্যই আত্মার উৎকর্ষ-সাধন করে অথবা আত্মাকে দোষযুক্ত করে।[১৬] জৈন ধর্মগ্রন্থগুলিতে বলা হয়েছে যে, আত্মা "পার্থিব শরীরের দ্বারা আবৃত" হয়ে অস্তিত্বমান থাকে এবং আত্মাও সম্পূর্ণভাবে শরীরকে পরিপূর্ণ করে রাখে।[১৭] অন্যান্য সকল ভারতীয় ধর্মের মতোই জৈনধর্মেও কর্মকে বিধানের বিশ্বজনীন কারণ ও কার্য মনে করা হয়। যদিও এই ধর্মে কর্মকে একটিকে পার্থিব বস্তু (সূক্ষ্ম পদার্থ) হিসেবেও দেখা হয়, যা আত্মাকে বদ্ধ করতে পারে, আত্মার সঙ্গে আবদ্ধ অবস্থায় জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে যাত্রা করতে পারে এবং লোকসমূহে জীবগণের দুঃখ ও সুখকে প্রভাবিত করতে পারে।[১৮] কর্মকে অস্পষ্ট এবং আত্মার সহজাত প্রকৃতি ও সংগ্রামের বস্তু মনে করা হয়। সেই সঙ্গে এটিকে পরবর্তী জন্মের একটি আধ্যাত্মিক অনুদ্ভূত শক্তিও জ্ঞান করা হয়।[১৯]
সংসার
সংসারের নির্মাণ-কাঠামো সম্পর্কে ধারণা বিষয়ে জৈনধর্ম ও অন্যান্য ভারতীয় ধর্মগুলির মধ্যে মতদ্বৈধ আছে। জৈনধর্মে আত্মা ("জীব") হিন্দুধর্মের ন্যায় সত্য হিসেবে স্বীকৃত হলেও বৌদ্ধধর্মের অনুরূপ বিবেচিত হয়নি। পুনর্জন্মের চক্রটিরও জৈনধর্মে একটি সুস্পষ্ট সূত্রপাত ও সমাপ্তি রয়েছে।[২০] জৈন থিওজফি অনুযায়ী, প্রত্যেক আত্মা চুরাশি লক্ষ জন্মাবস্থা পার হয় এই সংসারে আসে,[২১][২২] যাতে তারা পাঁচ ধরনের শরীরের মধ্যে দিয়ে যায়: স্থলচর শরীর, জলচর শরীর, অগ্নিময় শরীর, বায়ুচর শরীর ও উদ্ভিজ্জ শরীর, যা আবার বৃষ্টিপাত থেকে শ্বাসপ্রশ্বাস পর্যন্ত ক্রমাগত সকল মানব ও অ-মানবীয় ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হয়।[২৩] জৈনধর্মে জীবনের কোনও রূপকেই আঘাত করা পাপ, তাতে নেতিবাচক কর্মের প্রভাব পড়ে বলে মনে করা হয়।[২৪][২৫] জৈনধর্ম মতে আত্মার সূচনা হয় এক আদ্যকালীন অবস্থায় এবং কর্মানুসারে হয় তা উচ্চতর অবস্থায় বিবর্তিত হয় অথবা নিম্নতর অবস্থায় ফিরে যায়।[২৬] জৈনধর্ম আরও বলে যে, "অভব্য" (অক্ষম) আত্মারা কখনই মোক্ষ লাভ করতে পারে না।[২০][২৭] এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, কোনও ইচ্ছাকৃত ও জঘন্য অশুভ কর্মের পরে আত্মা "অভব্য" অবস্থায় প্রবেশ করে।[২৮] হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শনের কোনও কোনও শাখার অদ্বৈত মতবাদের বিরুদ্ধে গিয়ে জৈনধর্ম বলে আত্মা ভালো বা মন্দ দুইই হতে পারে।[২৭] জৈনধর্ম মতে, একজন "সিদ্ধ" (মোক্ষপ্রাপ্ত আত্মা) সংসারের উর্ধ্বে চলে যান এবং তিনিই সর্বোচ্চ লোকে ("সিদ্ধশীল") সর্বজ্ঞ হয়ে চিরকাল সেখানেই বাস করেন।[২৯]
বিশ্বতত্ত্ব
জৈন ধর্মগ্রন্থগুলিতে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মাণ্ড অনেক চিরন্তন "লোক" (অস্তিত্বের জগৎ) দ্বারা গঠিত। হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মে কাল ও ব্রহ্মাণ্ডকে চিরন্তন মনে করা হয়, কিন্তু জৈনধর্মে ব্রহ্মাণ্ডকে মনে করা হয় ক্ষণস্থায়ী।[৩১][৩২] ব্রহ্মাণ্ড, দেহ, বস্তু ও কালকে আত্মা অর্থাৎ জীবের থেকে পৃথক জ্ঞান করা হয়। জৈন দর্শনে এদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে জীবন, জীবনযাপন, মৃত্যু ও পুনর্জন্ম ব্যাখ্যাত হয়েছে।[৩২] জৈন ব্রহ্মাণ্ডের তিনটি লোক বিদ্যমান: উর্ধ্বলোক, মধ্যলোক ও অধোলোক।[৩৩] জৈনধর্মে বলা হয় যে, কালের আদি নেই এবং তা চিরন্তন;[৩৪] "কালচক্র" অর্থাৎ কালের মহাজাগতিক চক্রটি অনিবার পাক খাচ্ছে। ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মাণ্ডের এই অংশে দুই "অর"-এর (অপরিমেয় কাল) মধ্যে ছয়টি পর্যায় রয়েছে এবং প্রথম অরে ব্রহ্মাণ্ড উৎপাদিত হয় এবং পরবর্তী অরে ব্রহ্মাণ্ড বিনষ্ট হয়।[৩৫] এইভাবেই এটি বিশ্বের কালচক্রকে দুই চক্রার্ধে বিভক্ত করে: "উৎসর্পিণী" (আরোহণকারী, ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধি ও আনন্দের সময়) ও "অবসর্পিণী" (অবরোহণকারী, ক্রমবর্ধমান দুঃখ ও পাপাচারের সময়)।[৩৪][৩৬][৩৭] এখানে বলা হয়েছে যে বর্তমানে বিশ্ব অবসর্পিণীর পঞ্চম অরে অবস্থিত, যা দুঃখ ও ধর্মীয় অধঃপতনে পরিপূর্ণ এবং যেখানে জীবিত সত্ত্বাদের উচ্চতা হ্রাস পায়। জৈনধর্ম মতে ষষ্ঠ অরের পর ব্রহ্মাণ্ড এক নতুন চক্রে পুনঃজাগরিত হবে।[৩৮][৩৯][৪০]
ঈশ্বর

জৈনধর্ম ঈশ্বর-নিরপেক্ষতাবাদী ধর্ম।[৪১] জৈন বিশ্বাসে ব্রহ্মাণ্ড অসৃষ্ট ও চিরবিরাজমান;[৪২] এই কারণেই তা স্বাধীন এবং তার কোনও স্রষ্টা, শাসক, বিচারক বা ধ্বংসকর্তা নেই।[৩২][৪৩] এই-জাতীয় মত হিন্দুধর্ম ও আব্রাহামীয় ধর্মগুলির বিপরীত হলেও বৌদ্ধধর্মের অনুরূপ।[৪৪] অবশ্য জৈনরা দেবতা ও নারকীয় সত্ত্বাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। তাঁরা মনে করেন যে, এই দেবতা ও নারকীয় সত্ত্বারাও পার্থিব সত্ত্বাদের মতো জন্মগ্রহণ করেন, মারা যান এবং পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন।[৪৫][৪৬] জৈন ধর্মগ্রন্থগুলিতে বলা হয়েছে যে, কোনও দেবতার শরীরে সানন্দে বাস করার সৌভাগ্য কোনও আত্মা লাভ করতে পারেন তাঁর ইতিবাচক কর্মের জন্য[৪৭] এবং তাঁরা ঐহিক বিষয়ে অধিকতর অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের অধিকারী হন এবং মানবজগতে কী ঘটতে চলেছে তা পূর্বেই বুঝতে পারেন।[৪৭] অবশ্য তাঁদের অতীতের কর্ম-সঞ্জাত গুণাবলি ব্যয়িত হলে এই আত্মারা কীভাবে আবার মানুষ, পশুপাখি বা অন্য সত্ত্বা রূপে জন্মগ্রহণ করেন, তার ব্যাখ্যাও জৈনদের ধর্মগ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়।[৪৭][৪৮] জৈনধর্মে স-শরীরী উৎকৃষ্টতম আত্মাকে বলা হয় 'অরিহন্ত (বিজয়ী) ও শরীর-বিহীন উৎকৃষ্টতম আত্মাকে বলা হয় সিদ্ধ (মুক্ত আত্মা)।[২৯][৪৯][৪১]
জ্ঞানতত্ত্ব
জৈন দর্শনে তিনটি "প্রমাণ" (জ্ঞানের নির্ভরযোগ্য উপায়) স্বীকৃত। জৈন দর্শন মতে, জ্ঞানের ভিত্তি "প্রত্যক্ষ" (ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে উপলব্ধি), "অনুমান" ও "শব্দ" (শাস্ত্রবাক্য অর্থাৎ প্রামাণিক সাক্ষ্য)।[৫০][৫১] "তত্ত্বার্থসূত্র", "পর্বাচরণসার", "নান্দী" ও "অনুযোগদ্বারিণী" প্রভৃতি গ্রন্থে এই ধারণাগুলি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।[৫২][৫১] কোনও কোনও জৈন ধর্মগ্রন্থে "উপমান"-কে (আংশিক সাদৃশ্য বর্ণনা) একটি চতুর্থ নির্ভরযোগ্য উপায় বলে উল্লেখ করা হয়েছে, ঠিক যেভাবে অন্যান্য ভারতীয় ধর্মে জ্ঞানতত্ত্ব-সংক্রান্ত মতগুলি পাওয়া যায় সেইভাবেই।[৫৩] জৈনধর্মে বলা হয় "জ্ঞান" পাঁচ প্রকারের –"কেবলজ্ঞান" (সর্বজ্ঞতা), "শ্রুতজ্ঞান" (শাস্ত্রজ্ঞান), "মতিজ্ঞান" (ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান), "অবধিজ্ঞান" (অন্তর্দৃষ্টি-সংক্রান্ত জ্ঞান) ও "মনঃপ্রয়ায়জ্ঞান" (টেলিপ্যাথি)।[৫৪] জৈন ধর্মগ্রন্থ "তত্ত্বার্থসূত্র" অনুযায়ী, প্রথম দু’টি অপ্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং অবশিষ্ট তিনটি প্রত্যক্ষ জ্ঞান।[৫৫]
মোক্ষ

জৈনধর্ম অনুযায়ী, আত্মার পরিশুদ্ধিকরণ এবং মোক্ষ লাভ করা সম্ভব তিন রত্নের পথ অবলম্বন করে:[৫৫][৫৬][৫৭] "সম্যক দর্শন" (সঠিক দৃষ্টিকোণ; অর্থাৎ জীব বা আত্মার সত্যে বিশ্বাস ও গ্রহণ);[৫৮] "সম্যক জ্ঞান" (সঠিক জ্ঞান, অর্থাৎ তত্ত্বসমূহের সংশয়হীন জ্ঞান);[৫৯] ও "সম্যক চরিত্র" (সঠিক আচরণ, অর্থাৎ পঞ্চপ্রতিজ্ঞার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ আচরণ)।[৫৯] জৈন ধর্মগ্রন্থগুলিতে মোক্ষের সহায়ক সন্ন্যাসপ্রথার উপর গুরুত্ব আরোপ করার জন্য একটি চতুর্থ রত্ন হিসেবে প্রায়শই "সম্যক তপ" (সঠিক তপস্যা) যোগ করে থাকে।[৬০] এই চার রত্নকে বলা হয় "মোক্ষমার্গ" (মোক্ষের পথ)।[৫৬]
প্রধান নীতিসমূহ
অহিংসা

জৈনধর্মে অহিংসা একটি মৌলিক মতবাদ।[৬১] জৈন মতে, ব্যক্তিকে সকল সহিংস ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করতে হবে এবং অহিংসার প্রতি এমন এক অঙ্গীকার না করলে সকল ধর্মাচরণই বৃথা যাবে।[৬১] জৈন ধর্মতত্ত্ব অনুযায়ী, হিংসা যতই সঠিক বা আত্মরক্ষামূলক হোক না কেন, ব্যক্তির উচিত কোনও সত্ত্বাকে হত্যা বা কোনও সত্ত্বার কোনও প্রকার ক্ষতি না করা। অহিংসা এই ধর্মে এমনই এক ধর্মীয় কর্তব্য।[৬১][৬২] "আচারাঙ্গসূত্র" ও "তত্ত্বার্থসূত্র" প্রভৃতি জৈন ধর্মগ্রন্থে বলা হয়েছে যে ব্যক্তিকে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ, স্থাণু বা সচল সকল প্রকার জীবিত সত্ত্বার হত্যা থেকে বিরত থাকতে হবে।[৬৩][৬৪] জৈন ধর্মতত্ত্ব এই শিক্ষা দেয় যে, কেউই অপর কোনও জীবিত সত্ত্বাকে হত্যা করবে না, অপরকে হত্যার নিমিত্তও হতে দেবে না, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনও হত্যায় সম্মতিও প্রদান করবে না।[৬৩][৬২] অধিকন্তু জৈনধর্ম শুধুমাত্র কর্মের মাধ্যমেই নয়, বরং বাক্য ও চিন্তার মধ্য দিয়েও সকল জীবের প্রতি অহিংসা নীতি গ্রহণের পক্ষপাতী।[৬৩][৬৪] এই ধর্ম এই শিক্ষা দেয় যে, কাউকে ঘৃণা করা বা কারও প্রতি সহিংস আচরণের পরিবর্তে "সকল জীবিত সত্ত্বার উচিত পরস্পরকে সাহায্য করা।"।[৬৪][ক] জৈনরা বিশ্বাস করেন যে, ব্যক্তির আত্মায় হিংসার এক নেতিবাচক প্রভাব পড়ে এবং হিংসা আত্মাকে ধ্বংসও করে দেয়, বিশেষত যখন হিংসা ইচ্ছাকৃতভাবে, ঘৃণা বা অযত্নের কারণে জন্ম নেয় অথবা যখন একজন পরোক্ষভাবে কোনও মানুষ বা মানবেতর জীবিত সত্ত্বাকে হত্যার কারণ হয় বা তাকে হত্যায় সম্মতি দেয়।[৬৬]
অহিংসার মতবাদটি হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মেও আছে, কিন্তু এটির সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটেছিল জৈনধর্মে।[৬১][৬৭][৬৮][৬৯][৭০] কোনও কোনও জৈন পণ্ডিতের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, সর্বোচ্চ ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে অহিংসার ধর্মতাত্ত্বিক এই ভিত্তিটি অন্য জীবের প্রতি দান বা দয়াপ্রদর্শনের গুণ থেকে বা সকল জীবকে উদ্ধার করার একটি কর্তব্যবোধ থেকে উৎসারিত হয়নি, বরং এটি হয়েছে একটি অবিরাম আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ফল হিসেবে। এর ফলে আত্মা শুদ্ধ হয় এবং তা থেকে ব্যক্তির নিজস্ব আধ্যাত্মিক বিকাশ সুসম্পন্ন হয়, যা শেষ পর্যন্ত ব্যক্তির মোক্ষলাভের পথ উন্মুক্ত করে দেয় এবং তাকে পুনর্জন্মের চক্র থেকে মুক্ত করে।[৭১] জৈনরা বিশ্বাস করেন যে, কোনও সত্ত্বাকে আঘাত করলে অসৎকর্মের উদ্ভব ঘটে, যা ব্যক্তির পুনর্জন্মের কারণ হয় এবং ভবিষতে তার ভালো থাকাকে বিঘ্নিত করে দুঃখেরও উৎপত্তি ঘটায়।[৭২][৭৩]
পরবর্তীকালীন মধ্যযুগীয় জৈন পণ্ডিতেরা বহিঃশত্রুর ভীতিপ্রদর্শন বা হিংসার সম্মুখীন হয়ে অহিংসার নীতিটি পুনঃসমীক্ষা করে দেখেন। উদাহরণস্বরূপ, সাধ্বীদের রক্ষা করার জন্য সাধুদের সহিংস আচরণের তাঁরা যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেছিলেন।[৭৪][৭৫] পল ডুন্ডাসের মতে, জৈন পণ্ডিত জিনদত্তসুরি মুসলমানদের দ্বারা মন্দির ধ্বংস ও জৈন নিপীড়নের সময়ই লিখেছিলেন যে, "ধর্মকর্মে আত্মনিয়োগকারী এমন কোনও ব্যক্তিকে যদি যুদ্ধ করতে বা হত্যা করতে বাধ্য করা হয়, তবে তিনি আধ্যাত্মিক গুণাবলির কিছুই হারাবেন না, বরং মুক্তিলাভ করবেন"।[৭৬][৭৭] যদিও জৈন ধর্মগ্রন্থগুলিকে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে যুদ্ধ ও হত্যা ক্ষমা করার উদাহরণ অপেক্ষাকৃত হারে দুর্লভ।[৭৪][খ]
অনেকান্তবাদ (বহুমুখী সত্য)

জৈনধর্মের দ্বিতীয় প্রধান নীতিটি হল "অনেকান্তবাদ"।।[৭৯][৮০] শব্দটি এসেছে "অনেকান্ত" অর্থাৎ "বহুমুখী" এবং "বাদ" অর্থাৎ "মতবাদ শব্দ দু’টির মিলনে।[৭৯][৮০] এই মতবাদ অনুযায়ী, সত্য ও বাস্তবতা জটিল এবং সবসময়ই তার বহু-অংশবিশিষ্ট দিক থাকে। এই মতবাদে আরও বলা হয়েছে যে, বাস্তবতার অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায়, কিন্তু তা ভাষা দ্বারা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করা যায় না। অনেকান্তবাদ বলে, মানুষের পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগের প্রয়াসটি আসলে "নয়" অর্থাৎ "সত্যের আংশিক প্রকাশ"।[৭৯] বলা হয় যে, মানুষ সত্যের অভিজ্ঞতার আস্বাদ পেতে পারে, কিন্তু তা সম্পূর্ণভাবে ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারে না। অনেকান্তবাদ মতে, অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করার প্রয়াসগুলি হল "স্যাৎ" বা "কিয়দংশে" বৈধ, কিন্তু তা "সম্ভবত, শুধুমাত্র একটি দৃষ্টিকোণ থেকে অসম্পূর্ণ" রয়েই যায়।[৮১] অনেকান্তবাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এক অর্থে আধ্যাত্মিক সত্যগুলির অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায়, কিন্তু তা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করা যায় না।[৭৯] এই মতে, "একান্ত"-এ (একমুখিতা) বিশ্বাস এক মহাভ্রান্তি; কারণ সেখানে কিছু কিছু আপেক্ষিক সত্যকে পরম সত্য জ্ঞান করা হয়।[৮২] এই মতবাদটি প্রাচীন। "সামান্নফল সুত্ত"-এর মতো বৌদ্ধ গ্রন্থেও এই মতবাদ পাওয়া যায়। জৈন আগমগুলিতে বলা হয়েছে, সকল প্রকার অধিবিদ্যামূলক প্রশ্নের উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে মহাবীরের উত্তরটি ছিল এক "সীমিত স্তরে হ্যাঁ" ("স্যাৎ")।[৮৩][৮৪] এই গ্রন্থগুলি অনেকান্তবাদকে বুদ্ধের শিক্ষা থেকে একটি প্রধান পার্থক্য হিসেবে চিহ্নিত করে। বুদ্ধ মধ্যপন্থা শিক্ষা দিয়েছিলেন; অধিবিদ্যামূলক প্রশ্নের ক্ষেত্রে তিনি "হ্যাঁ, এটাই" বা "না, এটা নয়" এই জাতীয় চরম উত্তর দিতেন। অপরপক্ষে মহাবীর তাঁর অনুগামীদের পরম বাস্তবতাকে বুঝতে "সম্ভবত" কথাটি যুক্ত করে "হ্যাঁ, এটা" ও "না, এটা নয়" দুইই গ্রহণের শিক্ষা দিয়েছিলেন।[৮৫] জৈনধর্মে এক দ্বৈতবাদী অনেকান্তবাদের নির্মাণ-কাঠামোর মধ্যে স্থায়ী সত্ত্বাকে "জীব" (আত্মা) ও "অজীব" (বস্তু) হিসেবে ধারণা করা হয়।[৮৬]
পল ডুন্ডাসের মতে, সমসাময়িক কালে অনেকান্তবাদ ধারণাটিকে কোনও কোনও জৈন "বিশ্বজনীন ধর্মীয় সহিষ্ণুতার প্রচার", "বহুত্ব"-এর এক শিক্ষা এবং "অন্যান্য [নৈতিক, ধর্মীয়] মতবাদের প্রতি সহৃদয় আচরণ" হিসেবে দেখেন। ডুন্ডাস বলেছেন যে, এটি ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলি ও মহাবীরের উপদেশাবলির ভ্রান্ত ব্যাখ্যা।[৮৭] তাঁর মতে, মহাবীরের শিক্ষায় "বহুমুখিতা, বহুমুখী দৃষ্টিকোণ" হল পরম সত্য ও মানব অস্তিত্ব বিষয়ক।[৮৮] তিনি দাবি করেন যে, খাদ্যের জন্য প্রাণীহত্যা, অবিশ্বাসী বা অন্য কোনও জীবিত সত্ত্বার বিরুদ্ধে হিংসাকে অনেকান্তবাদ মতে "সম্ভবত ঠিক" বলা হয়নি।[৮৭] উদাহরণস্বরূপ, জৈন সাধু ও সাধ্বীদের পঞ্চ মহাব্রত প্রসঙ্গে কঠোর নিয়ম রয়েছে এবং সেগুলির সম্পর্কেও কোনও "সম্ভবত" কথাটি খাটে না।[৮৯] ডুন্ডাস আরও বলেছেন যে, একইভাবে প্রাচীনকাল থেকেই জৈনধর্ম বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্মের সঙ্গে সহাবস্থান করে আসছে; এই সকল ধর্মের জ্ঞানতত্ত্ব ও ধর্মবিশ্বাসের কিছু কিছু ক্ষেত্রে জৈনধর্মের সঙ্গে এগুলির মতভেদ আছে; ঠিক যেমন ওই দুই ধর্মও জৈনধর্মের সকল মতকে গ্রহণ করে না।[৯০]
অপরিগ্রহ (অনাসক্তি)
জৈনধর্মের তৃতীয় প্রধান নীতিটি হল "অপরিগ্রহ", অর্থাৎ কোনও জাগতিক বস্তুর প্রতি অনাসক্তি।[৯১] জৈনধর্মে সাধু ও সাধ্বীদের ক্ষেত্রে কোনও সম্পত্তি, সম্পর্ক ও আবেগের প্রতি সম্পূর্ণ অনাসক্তির প্রয়োজন হয়।[৯২] দিগম্বর সম্প্রদায়ে সাধু-সাধ্বীরা পরিযায়ী এবং শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ে তাঁরা এক স্থানে বাস করেন।[৯২] জৈন গৃহস্থদের ক্ষেত্রে সৎভাবে উপার্জিত স্বল্প সম্পত্তি রক্ষণেরই উপদেশ দেওয়া হয় এবং অতিরিক্ত সম্পত্তি দান করে দিতে বলা হয়।[৯১] নাথুভাই শাহের মতে, অপরিগ্রহ নীতিটি পার্থিব ও মানসিক উভয়ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। পার্থিব সম্পদ বলতে বিভিন্ন ধরনের সম্পত্তিকে বোঝায়। মানসিক সম্পত্তি বলতে বোঝায় আবেগ, পছন্দ ও পছন্দ এবং কোনও ধরনের আসক্তিকে। কথিত হয় যে, সম্পদের প্রতি অপরীক্ষিত আসক্তি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতি করে।[৯৩]
জৈন নীতিবিদ্যা ও পঞ্চ-মহাব্রত

জৈনধর্ম পাঁচটি নৈতিক কর্তব্য শিক্ষা দেয়, যেগুলিকে এই ধর্মে বলা হয় পঞ্চপ্রতিজ্ঞা। গৃহস্থ জৈনরা এগুলিকে বলেন "অনুব্রত" এবং জৈন সাধু-সাধ্বীরা এগুলিকে বলেন "মহাব্রত"।[৯৪] উভয়ের ক্ষেত্রেই এই ধর্মের নৈতিক অনুশাসনের প্রস্তাব করে যে, জৈনরা এক গুরু, দেব (জিন), মতবাদের সঙ্গে পরিচিত হবেন এবং সেই ব্যক্তিকে পাঁচ অপরাধ হতে মুক্ত হতে হবে: ধর্ম সম্পর্কে সংশয়, জৈনধর্মের সত্য সম্পর্কে অস্পষ্টতা, জৈন শিক্ষা সম্পর্কে আন্তরিক আকাঙ্ক্ষাহীনতা, সহধর্মী জৈনদের স্বীকৃতি প্রদান করা থেকে বিরত থাকা এবং তাঁদের আধ্যাত্মিক অনুশীলনের প্রশংসা না করা।[৯৫] এই কারণে জৈনরা পাঁচটি ব্রত বা প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন:
- "অহিংসা", ("ইচ্ছাকৃতভাবে হিংসা থেকে বিরত থাকা" বা "কাউকে আঘাত না করা"):[৯৫] জৈনরা প্রথমেই যে প্রধান ব্রত বা প্রতিজ্ঞাটি পালন করেন সেটি হল অপর কোনও মানুষ এবং সেই সঙ্গে সকল জীবিত সত্ত্বার (নির্দিষ্টভাবে পশুপাখিদের) ক্ষতি না করা।[৯৫] এটিই জৈনধর্মের সর্বোচ্চ নৈতিক কর্তব্য। এটি যে শুধু ব্যক্তির কার্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল, তা-ই নয়, বরং বাক্য ও চিন্তাভাবনার মধ্যেও অহিংসতাকে স্থান দেওয়ার কথা উপদেশ দিত।[৯৬][৯৭]
- "সত্য" ("সত্যবাদিতা"): এই ব্রতটি হল সর্বদা সত্য কথা বলার। মিথ্যা না বলা বা যা অসত্য তা না বলার এবং সেই সঙ্গে অন্যকেও মিথ্যা বলতে উৎসাহিত না করা বা অন্যের অসত্য বচনকে অনুমোদন না করা।[৯৬][৯৪]
- "অস্তেয়" ("চুরি না করা"): জৈন গৃহস্থের স্বেচ্ছাপূর্বক প্রদত্ত কোনও জিনিস গ্রহণ করা কর্তব্য নয়।[৯৫][৯৮] এছাড়াও কোনও জিনিস প্রদত্ত হলেও জৈন সাধু-সাধ্বীদের তা গ্রহণের আগে অনুমতি গ্রহণ করতে হয়।[৯৯]
- "ব্রহ্মচর্য" (ইন্দ্রিয়-সংযম"): জৈন সাধু-সাধ্বীদের পক্ষে যৌনতা ও ইন্দ্রিয়-বিলাসিতা নিষিদ্ধ। গৃহস্থের পক্ষে ব্রহ্মচর্য ব্রতের অর্থ দাম্পত্যসঙ্গীর প্রতি সৎ ও বিশ্বস্ত থাকা।[৯৬][৯৪]
- "অপরিগ্রহ" ("অনাসক্তি"): এই ব্রতটি পার্থিব ও মনস্তাত্ত্বিক সম্পত্তির প্রতি অনাসক্তির এবং চাহিদা ও লোভ এড়িয়ে চলার উপদেশ দেয়।[৯৪] জৈন সাধু ও সাধ্বীরা সম্পত্তি ও সামাজিক সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন, কিছুই নিজেদের সম্পদ হিসেবে সঞ্চয় করে রাখেন না এবং কারও প্রতি আসক্ত থাকেন না।[৯১][১০০]
জৈনধর্ম সাতটি সম্পূরক ব্রত পালনেরও উপদেশ দেয়। এর মধ্যে তিনটিকে বলা হয় "গুণব্রত" ও চারটিকে বলা হয় "শিক্ষাব্রত"।[১০১][১০২] জৈন সাধু ও সাধ্বীরা অতীতকালে জীবনের শেষপর্বে "সল্লেখনা" (বা "সান্থারা") নামে এক "ধর্মীয় মৃত্যুবরণ"-এর ব্রত পালন করতেন। কিন্তু বর্তমানে এই ব্রতপালনের ঘটনা দুর্লভ।[১০৩] এই ব্রতে সাধু-সাধ্বীরা স্বেচ্ছায় ধীরে ধীরে খাদ্যগ্রহণ ও জলপান কমিয়ে দিয়ে অনাসক্তির সঙ্গে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করে নিতেন।[১০৪][১০৫] মনে করা হয় যে, এই ব্রত পালনের মাধ্যমে নেতিবাচক কর্মের প্রভাব কমে যায় এবং তা আত্মার পুনর্জন্মে প্রভাব বিস্তার করে।[১০৬]
ধর্মানুশীলন প্রথা
কৃচ্ছব্রত ও সন্ন্যাস
প্রধান ভারতীয় ধর্মগুলির মধ্যে জৈনধর্মেই কৃচ্ছব্রত সর্বাপেক্ষা কঠোর।[১০৭][১০৮][১০৯] কৃচ্ছব্রতীর জীবনে থাকে নগ্নতা (যা বস্ত্রের প্রতিও অনাসক্তির প্রতীক), উপবাস, শারীরিক কৃচ্ছসাধনা ও তপস্যা। এগুলির উদ্দেশ্য হল অতীত কর্মকে দগ্ধ করা এবং নতুন কর্মের উৎপাদন বন্ধ করা। জৈনধর্মে এই দুইই সিদ্ধ অবস্থায় উপনীত হওয়ার ও মোক্ষলাভের ক্ষেত্রে আবশ্যক মনে করা হয়।[১০৭][১১০][১১১]
"তত্ত্বার্থসূত্র" ও "উত্তরাধ্যয়ন সূত্র" ইত্যাদি জৈন ধর্মগ্রন্থে বিস্তারিতভাবে কৃচ্ছসাধনার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তীকালীন জৈন গ্রন্থগুলিতে ছ’টি বাহ্যিক ও ছ’টি আন্তরিক অনুশীলনের কথা প্রায়শই পুনরুল্লিখিত হয়েছে।[১১২] বাহ্যিক কৃচ্ছসাধনার মধ্যে পড়ে সম্পূর্ণ উপবাস, সীমিত পরিমাণে খাদ্যগ্রহণ, নির্দিষ্ট খাদ্যসামগ্রীই গ্রহণ, সুস্বাদু খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকা, মাংসের কৃচ্ছসাধন এবং মাংসকে রক্ষণ (অর্থাৎ, লোভের উৎপত্তি ঘটাতে পারে এমন কিছু এড়িয়ে চলা)।[১১৩] আন্তরিক কৃচ্ছসাধনার মধ্যে পড়ে অনুতাপ, স্বীকারোক্তি, সাধু-সাধ্বীদের সম্মান প্রদর্শন ও সহায়তা করা, অধ্যয়ন, ধ্যান এবং দেহ পরিত্যাগের জন্য শারীরিক চাহিদাগুলিকে উপেক্ষা করা।[১১৩] বাহ্যিক ও আন্তরিক কৃচ্ছসাধনার তালিকা গ্রন্থ ও পরম্পরাভেদে ভিন্ন ভিন্ন।[১১৪][১১৫] কৃচ্ছসাধনাকে কামনার নিয়ন্ত্রণ এবং জীবের (আত্মা) পরিশুদ্ধিকরণের একটি উপায় হিসেবে দেখা হয়।[১১৬] মহাবীর প্রমুখ তীর্থংকরেরা বারো বছর ধরে কৃচ্ছসাধনা করে এই জাতীয় ব্রতের উদাহরণ স্থাপন করেছিলেন।[১১৭][১১৮][১১৯]
জৈন সন্ন্যাসী সংগঠন বা "সংঘ" চার শ্রেণিতে বিন্যস্ত: "সাধু" (সন্ন্যাসী, "মুনি"), "সাধ্বী" (সন্ন্যাসিনী, "আর্যিকা"), "শ্রাবক" (পুরুষ গৃহস্থ) ও "শ্রাবিকা" (গৃহস্থ নারী)। শেষোক্ত দুই শ্রেণি কৃচ্ছব্রতী ও স্বশাসিত আঞ্চলিক সমাবেশে তাঁদের "গছ" বা "সমুদায়" নামক সন্ন্যাসী সংগঠনগুলির পৃষ্ঠপোষকতা করে।[১২০][১২১][১২২] জৈন সন্ন্যাসপ্রথায় ওষ্ঠাধর ঢেকে রাখাকে উৎসাহিত করা হয়। সেই সঙ্গে "দণ্ডাসন" নামে উলের সুতো সহ এক ধরনের দীর্ঘ দণ্ড ব্যবহার করতে হয়, যাতে পথে এসে পড়া পিঁপড়ে ও কীটপতঙ্গদের আলতো করে সরিয়ে দেওয়া যায়।[১২৩][১২৪][১২৫]
খাদ্য ও উপবাস
সকল জীবিত সত্ত্বার প্রতি অহিংসার নীতিটিই জৈন সংস্কৃতিকে নিরামিশপন্থী করে তুলেছে। ধর্মপ্রাণ জৈনরা দুগ্ধ-নিরামিশাহার অভ্যাস করেন, অর্থাৎ তাঁরা ডিম না খেলেও কোনও দুগ্ধজাত খাদ্যের উৎপাদনের সময় প্রাণীদের প্রতি হিংসাত্মক আচরণ না হলে সেই খাদ্য গ্রহণ করেন। প্রাণীকল্যাণের বিষয়টি গুরুত্ব পেলে অবশ্য খাদ্য বিষয়ে প্রাণীজ পণ্য ব্যবহার থেকে বিরত থাকাই উৎসাহিত করা হয়।[১২৬] জৈন সাধু, সাধ্বী ও কোনও কোনও অনুগামী আলু, পিঁয়াজ ও রসুনের মতো কন্দমূল ব্যবহার থেকে বিরত থাকেন, যাতে এই সব শিকড়গুলি উপড়ানোর সময় ক্ষুদ্র জীব-জীবাণু ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। এছাড়া কন্দ ও অঙ্কুরের উদ্গমকে উচ্চতর জীবন্ত সত্ত্বার একটি বৈশিষ্ট্য বলেও গণ্য করা হয়।[১২৭][গ] জৈন সাধু ও ধর্মপ্রাণ গৃহস্থেরা সূর্যাস্তের পর খাদ্যগ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। এটিকে তাঁরা বলেন "রাত্রি-ভোজন-ত্যাগ-ব্রত"।[১২৮] দিগম্বর সম্প্রদায়ের সাধুরা দিনে একবার মাত্র ভোজন আরও কঠিনতর এক ব্রত পালন করেন।[১২৮]
জৈনরা নির্দিষ্টভাবে উৎসবের সময় উপবাস করেন।[১২৯] "উপবাস" ছাড়াও এটিকে "তপস্যা" বা "ব্রত"-ও বলা হয়।[১৩০] ব্যক্তিবিশেষ নিজের সামর্থ্য অনুযায়ীও উপবাস করতে পারেন।[১৩১] দিগম্বর জৈনেরা "দশ-লক্ষণ-পর্ব" উপলক্ষ্যে উপবাস করেন দিনে একবার বা দুইবার খাদ্য গ্রহণ করে, দশ দিন ধরে উষ্ণ জল পান করে বা উৎসবের প্রথম ও শেষ দিনটিতে সম্পূর্ণ উপবাস করে।[১৩২] এটি কোনও জৈন সাধু-সাধ্বীর এই পর্যায়ের ধর্মানুশীলনের অনুকরণ।[১৩২] শ্বেতাম্বর জৈনরা অনুরূপভাবে আট দিনের "পর্যুষণ" উৎসবে "সম্বৎসরী-প্রতিক্রমণ" সহ একই প্রথা অনুশীলন করেন।[১৩৩] কথিত হয় যে, এই প্রথার মাধ্যমে ব্যক্তির আত্মা থেকে কর্মের প্রভাব মুক্ত হয় এবং ব্যক্তি পূণ্য অর্জন করেন।[১৩৪] "একদিবসীয়" উপবাসের সময়কাল ৩৬ ঘণ্টা, যা শুরু হয় পূর্বদিন সূর্যাস্তের থেকে এবং শেষ হয় মূল উপবাস-দিনের পরদিন সূর্যোদয়ের ৪৮ মিনিট পরে।[১২৯] গৃহস্থদের মধ্যে উপবাস বিশেষভাবে পালন করেন নারীরা। এর মাধ্যমে নারীরা তাঁদের ধর্মানুরাগ ও পবিত্রতা বজায় রাখেন, নিজেদের পরিবারের জন্য পূণ্য অর্জন করেন এবং ভাবীকালের জন্য কল্যাণ সুরক্ষিত করেন। এক-একটি সামাজিক ও সহায়তামূলক নারীগোষ্ঠীর মধ্যেও কিছু কিছু ধর্মীয় উপবাস প্রথা আয়োজিত হয়।[১৩৫]বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে বন্ধুবান্ধব ও পরিবারের মধ্যে দীর্ঘকালীন উপবাস অনুষ্ঠিত হয়।[১৩৫]
ধ্যান
জৈনধর্ম ধ্যানকে ধর্মানুশীলনের একটি আবশ্যিক অঙ্গ মনে করে। কিন্তু এই ধর্মে ধ্যানের উদ্দেশ্যে হিন্দুধর্মে বা বৌদ্ধধর্মে ধ্যানের উদ্দেশ্য থেকে অনেকটাই আলাদা।[১৩৬] অন্যান্য ভারতীয় ধর্মে ধ্যানের উদ্দেশ্য রূপান্তরমূলক অন্তর্দৃষ্টি বা আত্ম-উপলব্ধি হলেও জৈনধর্মে ধ্যানের উদ্দেশ্য হল কর্ম-সংক্রান্ত আসক্তি ও কর্মক্রিয়া বন্ধ করা।[১৩৬] পদ্মনাভ জৈনীর মতে, "সামায়িক" হল জৈনধর্মে "ধ্যানের সংক্ষিপ্ত পর্যায়সমূহ"-এর এক অনুশীলন, যা আবার "শিক্ষাবর্ত" অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক সংযমের অঙ্গ।[১৩৭] সামায়িকের উদ্দেশ্য হল মানসিক প্রশান্তি অর্জন, যা কিনা দ্বিতীয় শিক্ষাবর্ত।[ঘ] সাধু-সাধ্বীরা দিনে অন্তত তিনবার সামায়িক অভ্যাস করেন। কিন্তু একজন গৃহস্থ এটিকে জৈন মন্দিরে পূজা এবং অন্যান্য সেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত করে নেন।[১৩৮][১৩৯][১৪০] জনসন ও জৈনির মতে সামায়িক ধ্যানের থেকে বেশি কিছুর দ্যোতক এবং জৈন গৃহস্থের কাছে এটি "সাময়িকভাবে সন্ন্যাস মর্যাদা অর্জনের" একটি স্বেচ্ছামূলক আচার।[১৪১][ঙ]
আচার-অনুষ্ঠান ও পূজা

জৈনদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ে অনেক আচার-অনুষ্ঠান প্রচলিত রয়েছে। ডুন্ডাসের মতে, শ্বেতাম্বর জৈনদের মধ্যে গৃহস্থদের আচার-অনুষ্ঠানগত পথটি "কৃচ্ছসাধনার মূল্যবোধ দ্বারা অতিমাত্রায় পরিপূরিত"। এখানে অনুষ্ঠানগুলি পালিত হয় তীর্থংকরদের সম্মানে বা তাঁদের কৃচ্ছব্রতী জীবনের ঘটনাবলি উদ্যাপনের উদ্দেশ্যে অথবা কোনও কৃচ্ছব্রতীর মনস্তাত্ত্বিক ও পার্থিব জীবনকে পুরোভাগে রেখে তা অবলম্বন করার জন্য।[১৪৩][১৪৪] এই ধর্মের চরম অনুষ্ঠানটি হল "সল্লেখনা"। এটি হল খাদ্য ও পানীয় ত্যাগ করে এক কৃচ্ছব্রতীর স্বেচ্ছায় ধর্মসম্মত মৃত্যুবরণ।[১৪৩] দিগম্বর জৈনরাও একই ধারণা পোষণ করে। কিন্তু জীবনচক্র ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলি এক প্রকারে হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানেরই অনুরূপ।[১৪৩] এই পারস্পরিক মিলগুলি দেখা যায় প্রধানত জীবনচক্র-সংক্রান্ত (হিন্দু মতে ষোড়শ সংস্কার) আচার-অনুষ্ঠানগুলিতে। সম্ভবত জৈন ও হিন্দু সমাজের মধ্যে সহাবস্থানের কারণেই এই মিল দেখা গিয়েছিল এবং এই অনুষ্ঠানগুলিকে প্রয়োজনীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ বলে জ্ঞান করা হত।[১৪৫][১৪৬]
জৈনরা আনুষ্ঠানিকভাবে অসংখ্য দেবদেবীর পূজা করে।[১৪৪] এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে জিনদের পূজা বিশেষ প্রচলিত। জৈনধর্মে দেবতা হিসেবে জিন কোনও অবতার নন, বরং কোনও কৃচ্ছব্রতী তীর্থংকরের প্রাপ্ত সর্বজ্ঞতার সর্বোচ্চ অবস্থা।[১৪৭] চব্বিশ জন তীর্থংকরের মধ্যে জৈনরা প্রধানত চারজনকে পূজা করেন: মহাবীর, পার্শ্বনাথ, নেমিনাথ ও ঋষভনাথ।[১৪৮] তীর্থংকর ব্যতীত অন্যান্য সন্তদের মধ্যে দিগম্বর সম্প্রদায়ে বাহুবলীর ভক্তিমূলক পূজা বহুল প্রচলিত।[১৪৯] "পঞ্চ কল্যাণক" অনুষ্ঠানগুলি আয়োজিত হয় তীর্থংকরদের জীবনের পাঁচটি ঘটনার স্মরণে। এগুলির মধ্যে রয়েছে: "পঞ্চ কল্যাণক প্রতিষ্ঠা মহোৎসব", "পঞ্চ কল্যাণক পূজা " ও "স্নাত্রপূজা"।[১৫০][১৫১]

জৈনধর্মে মৌলিক অনুষ্ঠানটি হল দেবতার দর্শন। এই দেবতাদের মধ্যে থাকেন জিন,[১৫৩] বা অন্য যক্ষ ও যক্ষিণীগণ, ব্রহ্মাদেব প্রমুখ দেবদেবীগণ, ৫২ জন বীর, পদ্মাবতী, অম্বিকা ও ১৬ জন বিদ্যাদেবী (সরস্বতী ও লক্ষ্মী সহ)।[১৫৪][১৫৫][১৫৬] তেরাপন্থি দিগম্বরেরা তাঁদের আনুষ্ঠানিক পূজা শুধু তীর্থংকরদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন।[১৫৭] পূজানুষ্ঠানকে বলা হয় "দেবপূজা"। জৈনদের সকল উপ-সম্প্রদায়েই এই দেবপূজার চল রয়েছে।[১৫৮] সাধারণত গৃহস্থ জৈন সাদামাটা বস্ত্র পরিধান করে নৈবেদ্যের থালা নিয়ে মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করে হাঁটু গেড়ে বসে নমস্কার করে, তারপর মন্ত্রপাঠ ও প্রার্থনা সম্পূর্ণ করে। ক্ষেত্রবিশেষে মন্দিরের পুরোহিত সেই গৃহস্থকে সাহায্য করেন। তারপর গৃহস্থ নৈবেদ্য রেখে দিয়েই মন্দির ছেড়ে বেরিয়ে যান।[১৫৮]
জৈনদের আচারগুলির মধ্যে "অভিষেক" অর্থাৎ দেবমূর্তির আনুষ্ঠানিক স্নান অন্তর্গত।[১৫৯] কোনও কোনও জৈন সম্প্রদায়ে পূজারি (যাঁকে "উপাধ্যে" বলা হয়) নিয়োগ করা হয় মন্দিরের পূজানুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্য। ক্ষেত্রবিশেষে জৈন মন্দিরে হিন্দু পুরোহিতও পূজার্চনা করেন।[১৬০][১৬১] সাড়ম্বরে পূজায় অন্ন, টাটকা ও শুকনো ফল, ফুল, নারকেল, মিষ্টান্ন ও অর্থ নৈবেদ্য হিসেবে প্রদান করা হয়। কেউ কেউ কর্পূরের দীপ প্রজ্বলিত করে এবং চন্দনের তিলক দেয়। এছাড়াও ভক্তেরা ধর্মগ্রন্থ (বিশেষত তীর্থংকরদের জীবনকাহিনি) পাঠ করেন।[১৬২][১৫২]
হিন্দু ও বৌদ্ধদের মতো ধর্মপ্রাণ জৈনরাও মন্ত্রের কার্যকরিতায় বিশ্বাস করেন এবং নির্দিষ্ট কিছু ধ্বনি ও শব্দকে স্বাভাবিকভাবেই পবিত্র, শক্তিশালী ও আধ্যাত্মিক মনে করেন।[১৬৩][১৬৪] সর্বাধিক বিখ্যাত মন্ত্রগুলির মধ্যে জৈনধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ে যেটি বহুলভাবে স্বীকৃত, সেটি হল "পঞ্চ নমস্কার"। জৈনরা এটিকে চিরন্তন এবং প্রথম তীর্থংকরের যুগ থেকে প্রচলিত মনে করা হয়।[১৬৩][১৬৫] মধ্যযুগীয় পূজানুষ্ঠানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তীর্থংকর-সহ "ঋষিমণ্ডল"-এর তান্ত্রিক রেখাচিত্রগুলি।[১৬৬] জৈনদের তান্ত্রিক প্রথায় মন্ত্র ও আচার-অনুষ্ঠানের ব্যবহার হয় পুনর্জন্মের লোকে পূণ্যার্জনের লক্ষ্যে।[১৬৭]
উৎসব

সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বাৎসরিক জৈন উৎসবটিকে শ্বেতাম্বর জৈনরা বলেন "পর্যুষণ" এবং দিগম্বর জৈনরা বলেন "দশলক্ষণ পর্ব "। ভারতীয় পঞ্জিকার সৌরচান্দ্র ভাদ্রপদ (ভাদ্র) মাসের কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী তিথি থেকে এই উৎসব শুরু হয়। গ্রেগরিয়ান পঞ্জিকা অনুসারে এই সময়টি অগস্ট বা সেপ্টেম্বর মাসে পড়ে।[১৬৮][১৬৯] শ্বেতাম্বর জৈনরা আট দিন এবং দিগম্বর জৈনরা এই উৎসব দশ দিন ধরে পালন করেন।[১৬৮] এই সময়টিতে জৈন শ্রাবক-শ্রাবিকারা উপবাস ও প্রার্থনা করেন। এই উৎসবের সময় পাঁচটি প্রতিজ্ঞার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।[১৬৯] শ্বেতাম্বর জৈনরা এই সময় কল্পসূত্র পাঠ করেন; দিগম্বর জৈনরা পাঠ করেন তাঁদের নিজস্ব ধর্মগ্রন্থগুলি। এই উৎসবটি হল এমন এক সময় যখন জৈনরা সক্রিয়ভাবে জীবহিংসা নিবারণের জন্য প্রযত্ন করেন। এই সময় তাঁরা পশুপাখিদের মুক্তি দেন এবং প্রাণীহত্যার প্রতিরোধ করেন।[১৬৮]
ক্ষমাশীলতা
আমি সকল জীবকে ক্ষমা করছি,
সকল জীব আমাকে ক্ষমা করুক।
জগতে সকলে আমার বন্ধু,
আমার কোনও শত্রু নেই।
— জৈন উৎসবের শেষ দিনের প্রার্থনা[১৭০]
উৎসবের শেষ দিনটির কেন্দ্রে থেকে প্রার্থনা ও ধ্যানসভা। এটি "সম্বৎসরী" নামে পরিচিত। জৈনরা এই দিনটিকে প্রায়শ্চিত্ত, সকলকে ক্ষমা করার, সকল জীবের থেকে ক্ষমা চাওয়ার, শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থনার এবং জগতের সকলকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করার দিন মনে করেন।[১৬৮] অন্যের প্রতি "মিচ্ছামি দুক্কদম" বা "খমাৎ খম্না" বলে ক্ষমাপ্রার্থনা করা হয়। এর অর্থ হল, "যদি আমি জ্ঞানত বা অজ্ঞানত বাক্য বা কর্মের মাধ্যমে তোমার প্রতি কোনও অন্যায় করে থাকি, তবে আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি।" "পর্যুষণ" কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল "বিশ্বস্ত থাকা" বা "একত্রিত হওয়া"।[১৭১]
মহাবীর জন্ম কল্যাণক উৎসবটি আয়োজিত হয় মহাবীরের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে। ভারতীয় পঞ্জিকার চান্দ্রসৌর চৈত্র মাসের ত্রয়োদশী তিথিতে মহাবীর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। গ্রেগরিয়ান পঞ্জিকা অনুসারে এই দিনটি মার্চ বা এপ্রিল মাসে পড়ে।[১৭২][১৭৩] এই উৎসব উপলক্ষ্যে জৈনরা মন্দির, তীর্থ ও পুণ্যস্থানে যাত্রা করেন এবং মহাবীরের শোভাযাত্রা বের করেন। ভারতের বিহার রাজ্যের রাজধানী পটনার উত্তরে মহাবীরের জন্মস্থান বলে কথিত কুন্দগ্রামে জৈনরা বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।[১৭২] দীপাবলির পরের দিনটি জৈনরা মহাবীরের মোক্ষলাভের দিন হিসেবে উদ্যাপন করেন।[১৭৪] হিন্দুদের দীপাবলি উৎসবটিও এই একই দিনেই (কার্তিক অমাবস্যা) উদ্যাপিত হয়। এই দিন জৈন মন্দির, বাড়ি, কার্যালয় ও দোকানগুলি প্রদীপ ও বৈদ্যুতিক বাতি দিয়ে সাজানো হয়। আলো জ্ঞানের এবং অজ্ঞান দূরীকরণের প্রতীক। এই দিন মিষ্টি বিতরণ করা হয়। দীপাবলির সকালে সারা বিশ্বে জৈন মন্দিরগুলিতে মহাবীরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনার পর "নির্বাণ লাড়ু" বিতরিত হয়। জৈন নববর্ষও দীপাবলির পরদিনই শুরু হয়।[১৭৫] হিন্দুদের অক্ষয়তৃতীয়া ও রাখিবন্ধনের মতো উৎসবগুলি জৈনরাও পালন করেন।[১৭৬][১৭৭]
সম্প্রদায় ও প্রথাসমূহ
জৈন সমাজ দু’টি প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত: দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর। দিগম্বর সাধুরা কোনও বস্ত্র পরিধান করেন না; সাধ্বীরা শুধু সেলাই-না-করা অনাড়ম্বর শাড়ি পরেন। দিগম্বর সাধ্বীদের বলা হয় "আর্যিকা"। অন্যদিকে শ্বেতাম্বর সাধু-সাধ্বীরা সবাই সেলাই-না-করা সাদা কাপড় পরেন।[১৭৮]
জৈন বিশ্বাস অনুযায়ী, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনকালে আচার্য ভদ্রবাহু এক দ্বাদশ-বর্ষ-ব্যাপী দুর্ভিক্ষের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং নিজের শিষ্যদের নিয়ে কর্ণাটকে চলে গিয়েছিলেন। কথিত আছে, আচার্য ভদ্রবাহুর শিষ্য স্থুলভদ্র মগধে থেকে যান।[১৭৯] আচার্য ভদ্রবাহু ফেরার পর দেখেন যে, যাঁরা মগধে রয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা শ্বেত বস্ত্র পরিধান করতে শুরু করেছেন। যে জৈনরা নগ্ন থাকতেন তাঁদের কাছে এই রীতিটি গ্রহণযোগ্য হয়নি।[১৮০] জৈনদের প্রথাগত বিশ্বাস অনুযায়ী এইভাবেই দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের বিভাজন শুরু হয়। দিগম্বরেরা নগ্ন থাকেন এবং শ্বেতাম্বরেরা শ্বেত বস্ত্র পরিধান করেন।[১৮১] দিগম্বরেরা এটি জৈনদের "অপরিগ্রহ" নীতির বিরোধী মনে করেছিলেন। কারণ, এই নীতি অনুযায়ী জৈনদের বস্ত্রের প্রতিও অনাসক্ত হয়ে সম্পূর্ণ নগ্নাবস্থায় থাকতে হত। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে শ্বেতাম্বরেরা বলভীর মহাসভা আয়োজন করেন। এই সভায় দিগম্বরেরা যোগ দেননি। এই সভাতেই শ্বেতাম্বর জৈনরা তাঁদের রক্ষিত সেই সব গ্রন্থগুলিকে প্রামাণ্য ধর্মশাস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করেন, যেগুলিকে দিগম্বরেরা বরাবরই প্রত্যাখ্যান করে এসেছিলেন। মনে করা হয় যে, এই ধর্মসভার মাধ্যমেই জৈনদের প্রধান দু’টি সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐতিহাসিক বিভাজনটি দৃঢ় ভিত্তি লাভ করে।[১৮২][১৮৩] দিগম্বর মতবাদের প্রাচীনতম নথিটি কুন্দকুন্দ কর্তৃক প্রাকৃত ভাষায় লেখা সুত্তপহুদ গ্রন্থে পাওয়া যায়।[১৮৪]
দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর জৈনদের পার্থক্য রয়েছে তাদের প্রথা ও রীতিনীতি এবং পোষাক-নীতিতে, [১৮৫][১৮৬][১৮৭] উপদেশাবলির ব্যাখ্যায়টেমপ্লেট:Sfnজৈনি[১৮৬] এবং জৈন ইতিহাস প্রসঙ্গে (বিশেষত তীর্থংকর প্রসঙ্গে)।[১৮৮][১৮৯][১৯০][১৯১][১৯২] তাঁদের সন্ন্যাসের নিয়মের মধ্যেও পার্থক্য আছে,[১৯৩] যেমন আছে দুই সম্প্রদায়ের মূর্তিতত্ত্বে।[১৯৩] শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ে সাধুর তুলনায় সাধ্বী বেশি,[১৯৪] যেখানে দিগম্বর সম্প্রদায় প্রধানত সাধুদের নিয়েই গঠিত[১৯৫] এবং দিগম্বরেরা মনে করেন যে, পুরুষেরা আত্মার মোক্ষলাভের পথে অধিকতর এগিয়ে থাকে।[১৯৬][১৯৭] অন্যদিকে শ্বেতাম্বর জৈনরা মনে করেন যে, নারীরাও কৃচ্ছসাধনের মাধ্যমে মোক্ষলাভ করতে পারেন[১৯৭][১৯৮] এবং বলেন যে, উনবিংশ তীর্থংকর মাল্লীনাথ ছিলেন নারী।[১৯৯] শেষোক্ত মতটি দিগম্বর জৈনেরা প্রত্যাখ্যান করেন।[২০০]
মথুরা অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে কুষাণ সাম্রাজ্যের সমসাময়িক কালের (আনুমানিক খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী) অনেক জৈন মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে।[২০১] সেই সব মূর্তিতে তীর্থংকরদের দেখা গিয়েছে নগ্ন অবস্থায় এবং সাধুদের দেখা গিয়েছে বাঁ-কাঁধে বস্ত্রাবৃত অবস্থায়, যাকে জৈনশাস্ত্রে "অর্ধফলক" (অর্ধ-বস্ত্রাবৃত) বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।[২০১] মনে করা হয় যে, যাপনীয় শাখাটির উৎপত্তি এই "অর্ধফলক" ধারণাটির থেকেই। এই শাখায় দিগম্বরদের নগ্নতা-নীতির সঙ্গে বেশ কয়েকটি শ্বেতাম্বর বিশ্বাসও গৃহীত হয়েছিল।[২০১] ফ্লুগেলের মতে, আধুনিক যুগে নতুন জৈন ধর্মীয় আন্দোলনগুলি হল "প্রাথমিকভাবে জৈনধর্মের ভক্তিবাদী রূপ", যার সঙ্গে "জৈন মহাযান" শৈলীর ভক্তিবাদের একটি সাদৃশ্য রয়েছে।[২০২]
শাস্ত্র ও ধর্মগ্রন্থ
জৈনদের প্রামাণ্য ধর্মশাস্ত্রগুলিকে বলা হয় "আগম"। কথিত আছে, অনেকটা প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলির মতো এগুলিও মৌখিক প্রথার মাধ্যমে প্রচলিত ছিল।[২০৪] মনে করা হয় যে, এগুলির উৎস হল তীর্থংকরদের উপদেশাবলি, যা তাঁদের "গণধর" অর্থাৎ প্রধান শিষ্যগণ "শ্রুত জ্ঞান" হিসেবে পরম্পরাক্রমে ছড়িয়ে দিতেন।[২০৫][২০৬] শ্বেতাম্বর জৈনরা মনে করেন যে, কথ্য শাস্ত্রভাষাটি ছিল অর্ধমাগধী; অন্যদিকে দিগম্বর জৈনরা এই শাস্ত্রভাষাটিকে এক ধরনের ধ্বনি-অনুনাদ মনে করেন।[২০৪]
শ্বেতাম্বরেরা বিশ্বাস করেন যে তাঁরা জৈনদের আদি ৫০টি শাস্ত্রের ৪৫টি সংরক্ষণ করেছেন (হারিয়ে গিয়েছে শুধু একটি অঙ্গ শাস্ত্র ও চারটি পূর্ব শাস্ত্র); কিন্তু দিগম্বরেরা মনে করেন যে সবগুলিই হারিয়ে গিয়েছে[২০৭][২০৮] এবং আচার্য ভূতাবলি ছিলেন শেষ সাধু যাঁর মূল প্রামাণ্য ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে আংশিক জ্ঞান ছিল। তাঁদের মতে, দিগম্বর আচার্যেরা চার "অনুযোগ" সহ আদিতম জ্ঞাত দিগম্বর জৈন ধর্মগ্রন্থগুলি পুনঃসৃজন ঘটিয়েছিলেন।[২০৯][২১০][২১১] দিগম্বর ধর্মগ্রন্থগুলি আংশিকভাবে প্রাচীনতর শ্বেতাম্বর ধর্মগ্রন্থগুলির সঙ্গে সহমত পোষণ করে, কিন্তু সেই সঙ্গে জৈনদের প্রধান দুই সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থের মধ্যে কিছু লক্ষণীয় পার্থক্যও বিদ্যমান।[২১২] খ্রিস্টীয় ৬০০ থেকে ৯০০ অব্দের মধ্যবর্তী সময়ে দিগম্বর জৈনেরা অপ্রধান প্রামাণ্য শাস্ত্র রচনা করে তাকে চারটি অংশ বা "বেদ"-এ ভাগ করেন: ইতিহাস, সৃষ্টিবিদ্যা, দর্শন ও নীতিবিদ্যা।[২১৩][চ]
জৈনধর্মের সর্বাধিক জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী ধর্মগ্রন্থগুলি হল এই ধর্মের অপ্রধান সাহিত্য। এগুলির মধ্যে "কল্পসূত্র" বিশেষভাবে শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ে জনপ্রিয়তা লাভ করে। শ্বেতাম্বরেরা ভদ্রবাহুকে (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দ) এই গ্রন্থের রচয়িতা মনে করেন। এই প্রাচীন পণ্ডিত দিগম্বর সম্প্রদায়েও সম্মানিত হয়ে থাকেন। তাঁরা মনে করেন যে, ইনিই তাঁরের প্রাচীন দক্ষিণ কর্ণাটক অঞ্চলে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁদের পরম্পরার সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন।[২১৫] অপরদিকে শ্বেতাম্বরেরা মনে করেন যে ভদ্রবাহু নেপালে চলে গিয়েছিলেন।[২১৫] উভয় সম্প্রদায়ই তাঁর চরিত "নির্যুক্তি" ও "সংহিতা"-গুলিকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। উমাস্বাতী রচিত প্রাচীনতম প্রাপ্ত সংস্কৃত গ্রন্থ "তত্ত্বার্থসূত্র" জৈনধর্মের সকল সম্প্রদায়েই প্রামাণিক বলে বিবেচিত হয়।[২১৬][ছ][২১৮] দিগম্বর সম্প্রদায়ে কুন্দকুন্দ কর্তৃক রচিত গ্রন্থগুলি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন হয়ে থাকে এবং এগুলি ঐতিহাসিকভাবে প্রভাবশালীও বটে।[২১৯][২২০][২২১] অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জৈন ধর্মগ্রন্থ হল "সময়সার", "রত্নকরন্দ শ্রাবকাচার" ও "নিয়মসার"।[২২২]
বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্মের সঙ্গে তুলনা
হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন তিন ধর্মই কর্ম ও পুনর্জন্মের ন্যায় ধ্যানধারণা ও মতবাদে বিশ্বাসী; এই তিন ধর্মের উৎসব-অনুষ্ঠান ও সন্ন্যাসপ্রথার মধ্যেও অনেক সাদৃশ্য আছে।[২২৩][২২৪][২২৫] তিন ধর্মের কোনওটিই চিরন্তন স্বর্গ বা নরক অথবা বিচারদিনে বিশ্বাস করে না। দেবদেবীতে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস, মূল মতবাদের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করা এবং প্রার্থনা, আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসবে যোগদানের ক্ষেত্রে তিন ধর্মই অনুগামীদের স্বাধীনতা দিয়ে থাকে। তিন ধর্মেই অহিংসার ন্যায় নীতিকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়,[২২৬] কামনা, ব্যক্তির কর্ম, উদ্দেশ্যের সঙ্গে দুঃখকে যুক্ত করে এবং আধ্যাত্মিকতাকে অজ্ঞানতামুক্ত শান্তি, পরম সুখাবস্থা ও মোক্ষের উপায় মনে করা হয়।[২২৭][২২৮]
অস্তিত্বের স্বরূপ-সংক্রান্ত দার্শনিক মতের দিক থেকে জৈনধর্ম বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের ভিন্ন মত পোষণ করে। তিন ধর্মই ক্ষণস্থায়িত্বে বিশ্বাস করে। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম "অনাত্তা"-র ("চিরন্তন সত্ত্বা বা আত্মার অনস্তিত্ব") ধারণাটি যোগ করে। হিন্দুধর্ম চিরন্তন অপরিবর্তনীয় আত্মার তত্ত্বে বিশ্বাস করে, যেখানে জৈনধর্ম চিরন্তন কিন্তু পরিবর্তনশীল "জীব"-এর ("আত্মা") ধারণায় বিশ্বাস করে।[২২৯]{{sfn|উইলি|২০০৪|pp=২–৫}[২৩০] জৈন বিশ্বাসে, প্রধানত পুনর্জন্মের চক্রে চিরন্তন জীব অসংখ্য এবং "সিদ্ধ"-দের (মোক্ষপ্রাপ্ত) সংখ্যা নগন্য।[২৩১] জৈনধর্মের বিপরীতে হিন্দু দর্শন অদ্বৈতবাদে বিশ্বাস করে। অদ্বৈত মতে, জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন নয়, বরং পরস্পর সংযুক্ত।[২৩২][২৩৩][২৩৪]
হিন্দুধর্ম ও জৈনধর্মে আত্মার অস্তিত্বকে স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলে মনে করা হয়। অধিকাংশ হিন্দু দার্শনিক শাখায় আত্মাকে অবিনশ্বর, অনন্ত ও অপরিবর্তনীয় ("বিভু") মনে করা হয়; তবে কোনও কোনও আত্মাকে আণবিকও মনে করেন। আত্মা ও ব্রহ্ম বিষয়ক হিন্দু ধারণাটি সাধারণত আলোচিত হয় অদ্বৈত বা দ্বৈতবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে। অন্যদিকে জৈনধর্মে ব্রহ্মের অধিবিদ্যামূলক ধারণাটিকে খারিজ করা হয় এবং জৈন দর্শন মনে করে যে, আত্মা চিরপরিবর্তনশীল এবং প্রত্যেক জীবনকালে দেহ বা বস্তুর সঙ্গে আবদ্ধ, তদনুযায়ী একটি সীমায়িত আকার ধরে এক জীবন্ত সত্ত্বার সমগ্র শরীরে সঞ্চারিত হয়।[২৩৫]
জৈনধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সাদৃশ্য প্রধানত বেদের প্রামাণিকতা ও ব্রহ্ম ধারণার অস্বীকারে। অন্যদিকে জৈনধর্ম ও হিন্দুধর্ম উভয়ের আত্মার অস্তিত্বকে স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলে গ্রহণ করে।[২৩৬][২৩৭] জৈন ও হিন্দুদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক সুপ্রচলিত, বিশেষত ভারতের উত্তর, মধ্য ও পশ্চিমাঞ্চলে।[২৩৮][২৩৯] আদি ঔপনিবেশিক যুগের কয়েকজনের মত ছিল যে, বৌদ্ধধর্মের মতো জৈনধর্মও আংশিকভাবে হিন্দু বর্ণপ্রথার ফলে জাতিচ্যুত একটি শাখা।[২৪০][২৪১] কিন্তু পরবর্তীকালের গবেষকেরা এটিকে পাশ্চাত্য গবেষকদের ভ্রান্তি বলেই স্বীকার করে নিয়েছেন।[২৪২] জৈন সমাজের ইতিহাসে যে জাতিব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তার ভিত্তি মানুষের জন্ম ছিল না। বরং জৈনধর্ম মানুষের পরিবর্তনে মনোনিবেশ করেছিল, সমাজ পরিবর্তনে নয়।[২৩৮][২৪৩][২৪৪][২৪৫][জ]
তিন ধর্মেই সন্ন্যাসপ্রথার অস্তিত্ব রয়েছে।[২৪৯][২৫০] তিন ধর্মেই সন্ন্যাসপ্রথার নিয়ম, পদমর্যাদাক্রম, বর্ষাকালে চতুর্মাস্য ব্রতের নিয়ম এবং ব্রহ্মচর্যের নিয়ম একই।[২৫০] এগুলির উৎপত্তি মহাবীর বা বুদ্ধেরও পূর্বে।[২৪৯] জৈন ও হিন্দু সন্ন্যাসী সম্প্রদায় প্রথাগতভাবেই পরিযায়ী জীবন যাপন করে থাকেন, অন্যদিকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা সংঘের (মঠ) আশ্রয়ে থাকতে পছন্দ করেন এবং সংঘের প্রাঙ্গনেই বসবাস করেন।[২৫১] বৌদ্ধ সন্ন্যাস প্রথায় সন্ন্যাসীদের সংঘের স্বাতন্ত্র্যসূচক রক্তাভ বস্ত্র ছাড়া বাইরে যেতে বা কাষ্ঠপাত্র ব্যবহার করতে বারণ করা হয়।[২৪৯] অপরপক্ষে জৈন সন্ন্যাসপ্রথায় সন্ন্যাসীদের হয় নগ্ন অবস্থায় (দিগম্বর সম্প্রদায়ে) অথবা শ্বেতবস্ত্র পরে (শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ে) থাকতে হয় এবং জৈন সন্ন্যাসীদের মধ্যে ভিক্ষাপাত্র হিসেবে কাষ্ঠপাত্র বা শুকনো লাউয়ের খোলা দিয়ে তৈরি শূন্য পাত্র ব্যবহারের বৈধতা আছে কিনা তা নিয়ে দ্বিমত আছে।[২৪৯][ঝ]
হিন্দুদের মতো জৈনরাও মনে করে যে আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে হিংসা ন্যায্য[২৫৩] এবং যে সৈন্য যুদ্ধে শত্রু বধ করে সে বৈধ কর্তব্যই পালন করে।[২৫৪] জৈন সম্প্রদায় নিজেদের আত্মরক্ষার বিষয়ে সামরিক শক্তির ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিয়েছিল। ইতিহাসে জৈন রাজন্যবর্গ, সেনানায়ক ও সৈনিকের উল্লেখও পাওয়া যায়।[২৫৫] জৈন ও হিন্দু সম্প্রদায় প্রায়শই অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও পরস্পরের প্রতি অনুকুল ভাব পোষণ করে এসেছে। কোনও কোনও হিন্দু মন্দিরের প্রাঙ্গনে কোনও জৈন তীর্থংকরের মূর্তি সম্মানের সঙ্গে স্থান পেয়েছে।[২৫৬][২৫৭] আবার বাদামি গুহামন্দিরসমূহ ও খাজুরাহোর মন্দির চত্বরের মতো জায়গায় হিন্দু ও জৈন স্থাপত্য পাশাপাশিই গড়ে উঠেছিল।[২৫৮][২৫৯]
শিল্পকলা ও স্থাপত্য

ভারতীয় শিল্পকলা ও স্থাপত্যে জৈনধর্মের অবদান বেশ গুরুত্বপূর্ণ। জৈন শিল্পকলায় তীর্থংকর ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের জীবনের কিংবদন্তিগুলি প্রদর্শিত হয়ে থাকে। এর মধ্যে এঁদের দেখা যায় উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান অবস্থায় ধ্যানরত ভঙ্গিতে। তীর্থংকরদের রক্ষাকারী অনুচর আত্মা যক্ষ ও যক্ষিণীদেরও তাঁদের মূর্তির সঙ্গে দেখা যায়।[২৬১] আদিতম জ্ঞাত জৈন মূর্তিটি বর্তমানে পটনা জাদুঘরে রক্ষিত। এটি আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর মূর্তি।[২৬১] পার্শ্বনাথের ব্রোঞ্জ মূর্তি রক্ষিত আছে মুম্বইয়ের প্রিন্স অফ ওয়েলস জাদুঘর ও পটনা জাদুঘরে; এগুলি খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে নির্মিত।[২৬২]
"অয়গপত" নামে এক ধরনের মানতপূর্তি ফলক প্রথম দিকের শতাব্দীগুলিতে জৈনধর্মে দান ও পূজার জন্য ব্যবহৃত হত। স্তুপ, ধর্মচক্র ও ত্রিরত্নের ন্যায় জৈন পূজার্চনার কেন্দ্রীয় বস্তু ও নকশা দ্বারা এই ফলকগুলি সজ্জিত থাকত। ভারতের উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের মথুরার নিকট কঙ্কালী টিলা ইত্যাদি প্রাচীন জৈন ক্ষেত্রগুলিতে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের সময় এমন অসংখ্য প্রস্তরফলক আবিষ্কৃত হয়েছে। এই ধরনের ফলক দানের প্রথা নথিবদ্ধ হয়ে আছে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত।[২৬৩][২৬৪] বিভিন্ন সত্ত্বাকে নিয়ে এককেন্দ্রীয়ভাবে উপবিষ্ট তীর্থংকরদের উপদেশসভা "সমবসরণ" জৈন শিল্পকলার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু।[২৬৫]
রাজস্থান রাজ্যের চিতোরের জৈন স্তম্ভ জৈন স্থাপত্যের একটি সুন্দর উদাহরণ।[২৬৬] জৈন গ্রন্থাগারগুলিতে অলংকৃত পুথিগুলি রক্ষিত আছে। এগুলির মধ্যে জৈন বিশ্বতত্ত্ব রেখাচিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যাত হয়েছে।[২৬৭] অধিকাংশ চিত্র ও অলংকরণে "পঞ্চ কল্যাণক" নামে পরিচিত ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি চিত্রিত। এগুলি গৃহীত হয়েছিল তীর্থংকরদের জীবনকথা থেকে। প্রথম তীর্থংকর ঋষভনাথ চিত্রিত হয়ে থাকেন হয় পদ্মাসনে বা "কায়োৎসর্গ" (দণ্ডায়মান) ভঙ্গিতে। অন্য তীর্থংকরদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য তাঁর কাঁধ পর্যন্ত আলম্বিত কেশরাশিতে। তাঁর ভাস্কর্যের বৃষচিহ্নও খচিত থাকে।[২৬৮] চিত্রকলায় তাঁর বিবাহ বা ইন্দ্র কর্তৃক তাঁর মস্তকে তিলক অঙ্কনের মতো জীবনের ঘটনাবলি চিত্রিত হয়েছে। অন্যান্য চিত্রে তাঁকে দেখা যায় অনুগামীদের মৃৎপাত্র উপহার দিতে; এছাড়াও তাঁকে দেখা গৃহ অঙ্কন করতে, তাঁত বুনতে এবং মাতা মারুদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।[২৬৯] চব্বিশ জন তীর্থংকরের প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা প্রতীক ছিল; এগুলির তালিকা পাওয়া যায় "তিলোয়পন্নতি", "কহবালী" ও "প্রবচনসারোধার" ইত্যাদি গ্রন্থে।[২৭০]
মন্দির
টেমপ্লেট:প্রধান জৈন মন্দিরসমূহ জৈন মন্দিরকে বলা হয় "দেরাসর" বা "বসদি"।[২৭১] মন্দিরে থাকে তীর্থংকরদের মূর্তি। এই মূর্তিগুলির কয়েকটি প্রতিষ্ঠিত, কয়েকটি চালনীয়।[২৭১] মন্দিরের দু’টি অংশ থাকে: গর্ভগৃহ ও নাটমন্দির। এর মধ্যে তীর্থংকর মূর্তি থাকে গর্ভগৃহে।[২৭১] মূর্তিগুলির একটিকে বলা হয় "মূলনায়ক" (প্রধান দেবতা)।[২৭২] জৈন মন্দিরগুলির সম্মুখে প্রায়শই "মানস্তম্ভ" (সম্মানের স্তম্ভ) নামে একটি স্তম্ভ নির্মাণ করা হয়।[২৭৩] মন্দির নির্মাণ করাকে এক পুণ্যকর্ম জ্ঞান করা হয়।[২৭৪]
প্রাচীন জৈন স্মারকগুলির অন্যতম হল মধ্যপ্রদেশের ভেলসার (বিদিশা) কাছে উদয়গিরি পাহাড়, মহারাষ্ট্রে ইলোরা, গুজরাতে পালিতানা মন্দিরসমূহ এবং রাজস্থানে আবু পর্বতের কাছে দিলওয়াড়ার জৈন মন্দিরসমূহ।[২৭৫] রণকপুরের চৌমুখ মন্দিরটিকে সুন্দরতম জৈন মন্দিরগুলির একটি বলে বিবেচনা করা হয়। এই মন্দিরটি বিস্তারিত খোদাইচিত্রের জন্য বিখ্যাত।[২৭৬] জৈন ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী, শিখরজিতে চব্বিশজন জৈন তীর্থংকরের মধ্যে কুড়ি জন এবং অন্যান্য অনেক সাধু মোক্ষ লাভ করেছিলেন (অর্থাৎ পুনর্জন্ম ব্যতিরেকে দেহত্যাগ করেছিলেন এবং তাঁদের আত্মা সিদ্ধশীলে প্রবেশ করেছিল)। উত্তরপূর্ব ঝাড়খণ্ডে অবস্থিত শিখরজি তাই একটি তীর্থস্থান হিসেবে গণ্য হয়।[২৭৭][ঞ] শ্বেতাম্বর মূর্তিপূজক সম্প্রদায়ের কাছে পবিত্রতম পুণ্যস্থান হল পালিতানা মন্দিরসমূহ।[২৭৯] শিখরজির সঙ্গে দু’টি ক্ষেত্রকে জৈন সমাজ সকল তীর্থস্থানের মধ্যে পবিত্রতম মনে করেন।[২৮০] খাজুরাহোর জৈন চত্বর ও জৈন নারায়ণ মন্দির একটি ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের অংশ।[২৮১][২৮২] শ্রবণবেলগোলা, সাবীর কম্বড বসদি বা সহস্র স্তম্ভ ও ব্রহ্মা জিনালয় হল কর্ণাটকের গুরুত্বপূর্ণ জৈন কেন্দ্র।[২৮৩][২৮৪][২৮৫] মাদুরাইয়ের আশেপাশে ২৬টি গুহা, ২০০টি প্রস্তরবেদি, ৬০টি অভিলিখন এবং শতাধিক ভাস্কর্য পাওয়া গিয়েছে।[২৮৬]
খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয়-প্রথম শতাব্দীর উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি গুহাসমূহ তীর্থংকর ও দেবদেবীদের খোদাইচিত্রে এবং হাতিগুম্ফা শিলালিপি সহ একাধিক শিলালিপিতে সমৃদ্ধ।[২৮৭][২৮৮] বাদামি, মাঙ্গি-টুঙ্গি ও ইলোরা গুহাসমূহের জৈন গুহা মন্দিরগুলিকেও গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয়।[২৮৯] সিট্টনবসল গুহা মন্দিরটি জৈন শিল্পকলার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এর মধ্যে একটি আদিযুগীয় গুহাবাস এবং অজন্তার সঙ্গে তুলনীয় উন্নতমানের সদ্যোরঙ্গ (ফ্রেস্কো) চিত্র সহ মধ্যযুগীয় পাথরে কাটা মন্দির পাওয়া গিয়েছে। গুহার ভিতরে রয়েছে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর তামিল-ব্রাহ্মী অভিলিখন সহ সতেরোটি প্রস্তরবেদি।[২৯০] খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর কাঝুগুমলই মন্দির দক্ষিণ ভারতে জৈনধর্মের পুনরুজ্জীবনের স্মৃতি বহন করে।[২৯১]
- ভারতে ও বহির্ভারতে বিভিন্ন শৈলীর জৈন মন্দির
তীর্থ

জৈন তীর্থক্ষেত্রগুলি নিম্নোক্ত শ্রেণিগুলিতে বিভক্ত:[২৯২]
- সিদ্ধক্ষেত্র – যে-সকল ক্ষেত্রকে কোনও এক অরিহন্ত (কেবলিন্) বা তীর্থংকরের মোক্ষ লাভের স্থান বলে মনে করা হয়। যেমন: অষ্টপদ, শিখরজি, গিরনার, পাওয়াপুরী, পালিতানা, মাঙ্গি-তুঙ্গি ও চম্পাপুরী (অঙ্গের রাজধানী)।
- অতিশয়ক্ষেত্র – যে-সকল ক্ষেত্রকে দৈব ঘটনাস্থল বলে মনে করা হয়। যেমন: মহাবীরজি, ঋষভদেও, কুন্দলপুর, তিজারা ও আহারজি।
- পুরাণক্ষেত্র{{snds}যে-সকল ক্ষেত্রে মহাপুরুষেরা বাস করেছিলেন। যেমন: অযোধ্যা, বিদিশা, হস্তিনাপুর ও রাজগির।
- জ্ঞানক্ষেত্র – যে-সকল ক্ষেত্র বিশিষ্ট আচার্যদের স্মৃতিধন্য বা শিক্ষাকেন্দ্র। যেমন: শ্রবণবেলগোলা।
পাকিস্তানের সিন্ধুপ্রদেশে জৈন সম্প্রদায় নগরপকর জৈন মন্দিরটি নির্মাণ করেছিল। যদিও একটি ইউনেস্কো আপাত-স্থিরীকৃত বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান আবেদন অনুযায়ী, নগরপকর জৈনধর্মের একটি "প্রধান ধর্মীয় কেন্দ্র বা তীর্থস্থান" নয়, কিন্তু "১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর সর্বশেষ জৈন ধর্মাবলম্বীরা [পাকিস্তান] ত্যাগ করার" পূর্বাবধি এক সময় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র ছিল।[২৯৩]
মূর্তি ও ভাস্কর্য

জৈন ভাস্কর্যে সাধারণত চব্বিশজন তীর্থংকরের কোনও না কোনও একজনকে দেখা যায়। এঁদের মধ্যে পার্শ্বনাথ, ঋষভনাথ ও মহাবীর অধিকতর জনপ্রিয়। এঁদের প্রায়ই পদ্মাসন বা "কায়োৎসর্গ" ভঙ্গিতে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখা যায়। এঁরা ছাড়া অরিহন্ত, বাহুবলী ও অম্বিকার ন্যায় রক্ষয়িত্রী দেবদেবীরাও জনপ্রিয়।[২৯৪] চতুর্পাক্ষিক মূর্তিগুলিও জনপ্রিয়। তীর্থংকর মূর্তিগুলি একই রকম দেখতে, এগুলিকে শুধু প্রত্যেক তীর্থংকরের পৃথক পৃথক প্রতীক দ্বারা চিহ্নিত করা যায়। ব্যতিক্রম শুধুই পার্শ্বনাথ। তাঁর মূর্তিতে একটি সর্পখচিত মুকুট দেখা যায়। দিগম্বর সম্প্রদায়ের মূর্তিগুলিও নগ্ন এবং অনাড়ম্বর; অন্যদিকে শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের মূর্তিগুলি বস্ত্রাবৃত এবং সুসজ্জিত অবস্থায় থাকে।[২৯৫]
অধুনা কর্ণাটক রাজ্যের শ্রবণবেলগোলার একটি পর্বতচূড়ায় ৯৮১ খ্রিস্টাব্দে গঙ্গ মন্ত্রী ও সেনানায়ক চবুন্দরায় বাহুবলী গোমতেশ্বরের ১৮-মিটার (৫৯-ফুট) দীর্ঘ একশিলা মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন। দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক আয়োজিত একটি এসএমএস সমীক্ষায় এটি ভারতের সাত আশ্চর্যের মধ্যে প্রথম হিসেবে বিবেচিত হয়। [২৯৬] ২০১৫ সালে মহারাষ্ট্রের নাসিক জেলায় ৩৩ মি (১০৮ ফু) দীর্ঘ অহিংসার মূর্তি (ঋষভনাথের মূর্তি) নির্মিত হয়।[২৯৭] জৈনদের মূর্তি প্রায়শই নির্মিত হয় অষ্টধাতু, আকোটা ব্রোঞ্জ, পিতল, সোনা, রুপো, একশিলা, পাথর-খোদাই ও মূল্যবান পাথরে।[২৯৮][২৯৯]
প্রতীক
জৈন মূর্তি ও শিল্পকলার মধ্যে স্বস্তিক ওঁ ও "অষ্টমঙ্গল" জাতীয় প্রতীকচিহ্নগুলি দেখা যায়। জৈনধর্মে "ওঁ" প্রতীকটি পঞ্চ-পরমেষ্ঠির (অরিহন্ত, অশিরি, আচার্য, উপজ্ঝয় ও মুনি) আদ্যক্ষরের ("অ-অ-আ-উ-ম") সমষ্টি মনে করা হয়।[৩০০][৩০১] আবার এই "ওঁ" প্রতীকটি এই ধর্মের "ণমোকার মন্ত্রের" পাঁচ পংক্তির আদ্যক্ষরেরও সমষ্টি বটে।[৩০২][৩০৩] "অষ্টমঙ্গল" হল আটটি পবিত্র প্রতীকের সমন্বয়ায়িত রূপ।[৩০৪] দিগম্বর সম্প্রদায়ে এগুলি হল ছত্র, ধ্বজ, কলস, চামর, দর্পণ, আসন, হাতপাখা ও পাত্র। শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ে এগুলি হল স্বস্তিক, "শ্রীবৎস", "নন্দাবর্ত", "বর্ধমানক" (খাদ্যপাত্র), "ভদ্রাসন" (আসন), কলস, দর্পণ ও জোড়া মাছ।[৩০৪]
চক্রের উপর করতলের চিহ্নটি অহিংসার প্রতীক। এখানে চক্রটি ধর্মচক্রের প্রতীক, যা অবিশ্রান্তভাবে অহিংসা নীতি অনুসরণের মাধ্যমে সংসার চক্রে পরিভ্রমণ বন্ধ হওয়ার দ্যোতক। জৈন পতাকার পাঁচটি রং একাধারে পঞ্চ-পরমেষ্ঠি ও পঞ্চ প্রতিজ্ঞার প্রতীক।[৩০৫] স্বস্তিক চিহ্নের চারটি বাহু জৈনধর্ম মতে পুনর্জন্মের ক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত চার ধরনের জীবের প্রতীক: মাববসত্ত্বা, দেবসত্ত্বা, নারকীয় সত্ত্বা ও মানবেতর সত্ত্বা।[৩০৬][৩০৭] স্বস্তিকের উপর তিনটি বিন্দু প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলিতে বর্ণিত আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অত্যাবশ্যক রত্নত্রয়ের (সম্যক দর্শন, সম্যক জ্ঞান, সম্যক চরিত্র) প্রতীক।[৩০৮]
১৯৭৪ সালে মহাবীরের নির্বাণের ২৫০০ বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে জৈন সমাজ তাদের ধর্মের জন্য একক একটি সমন্বিত প্রতীক গ্রহণ করে।[৩০৯] এই প্রতীকে তিন লোক (স্বর্গ, মানবলোক ও নরক) প্রদর্শিত হয়। সর্বোপরি অর্ধ-চক্রাকার অংশটি ছিল তিন লোকের উর্ধ্বে অবস্থিত সিদ্ধশীলের প্রতীক। জৈন স্বস্তিক ও অহিংসার চিহ্নটিও অন্তর্ভুক্ত হয়; সেই সঙ্গে হয় পরস্পরোপগ্রহো জীবানাম এই জৈন মন্ত্রটিও।[৩১০] এই মন্ত্রটি গৃহীত হয়েছিল উমাস্বাতী রচিত "তত্ত্বার্থসূত্র" গ্রন্থের ৫.২১ সংখ্যক সূত্র থেকে। এটির অর্থ হল "আত্মাগণ একে অপরের সেবায় আত্মনিয়োগ করুক"।[৩১১]
ইতিহাস

প্রাচীন যুগ
জৈনধর্ম হল একটি প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম। এই ধর্মের উৎস অস্পষ্ট।[৩১২][৩১৩][৩১৪] জৈনরা দাবি করেন যে, এটি একটি সনাতন ধর্ম এবং প্রথম তীর্থংকর ঋষভনাথ এই ধর্মের প্রথম পার্থিব প্রতিষ্ঠাতা।[৩১৫] গবেষকেরা অনুমান করেন যে, সিন্ধু সভ্যতার সিলমোহরে দৃষ্ট বৃষের চিত্রগুলি জৈনধর্মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।[৩১৬] এটি প্রাচীন ভারতের বেদ-বিরোধী অন্যতম "শ্রমণ" ধর্মবিশ্বাস।[৩১৭][৩১৮] দার্শনিক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের মতে এই ধর্মমতের অস্তিত্ব বেদসমূহের পূর্বেও ছিল।[৩১৯][৩২০]
প্রথম বাইশ জন তীর্থংকরের অস্তিত্ব এখনও প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি।[৩২১][৩২২] ত্রয়োবিংশ তীর্থংকর পার্শ্বনাথ ছিলেন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব।[৩২৩][৩২৪]তাঁর সময়কাল সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী।[৩২৫] মহাবীরকে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক মনে করা হয়।[৩২৬][৩২৭] জৈন ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও বুদ্ধের সমসাময়িক কালেই শুরু হয়েছিল।[৩২৮] পরবর্তীকালে অনুগামী এবং যে বাণিজ্য প্রক্রিয়া দুই ধর্মকে পুষ্ট করত তা নিয়ে দুই ধর্মের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়।[২৫১][৩২৯] বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থগুলির শিরোনাম কয়েকটি ক্ষেত্রে একই বা একই প্রকারের, কিন্তু এগুলিতে পৃথক মতবাদ ব্যক্ত হয়েছে।[৩৩০]
জৈনরা মনে করেন যে হর্যঙ্ক রাজবংশের রাজা বিম্বিসার (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৫৫৮-৪৯১ অব্দ), অজাতশত্রু (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৪৯২-৪৬০ অব্দ) ও উদয়ন (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৪৬০-৪৪০ অব্দ) ছিলেন জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষক।[৩৩১] জৈন বিশ্বাসে মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা তথা মহামতি অশোকের পিতামহ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (খ্রিস্টপূর্ব ৩২২-২৯৮) শেষ জীবনে জৈন সাধু ভদ্রবাহুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সাধু হয়ে যান।[৩৩২][৩৩৩] জৈন ধর্মগ্রন্থগুলিতে বলা হয়েছে যে, শ্রবণবেলগোলায় স্বেচ্ছায় অনশন ব্রত করে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[৩৩৪][৩৩২] বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলিতে চন্দ্রগুপ্তের কাহিনিটির বিভিন্ন পাঠান্তর পাওয়া যায়।[৩৩৫][৩৩৬]
খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে সম্রাট অশোক তাঁর স্তম্ভলিপিতে নিগন্থ অর্থাৎ জৈনদের কথা উল্লেখ করেছিলেন।[৩৩৭] খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে নির্মিত জৈন মূর্তিও পাওয়া গিয়েছে।[৩৩৮] প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ এমনই ইঙ্গিত করে যে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর পর থেকে মথুরা একটি গুরুত্বপূর্ণ জৈন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।[২৬৪] অন্ততপক্ষে খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর অভিলিখনগুলি থেকে বোঝা যায় ততদিনের মধ্যে জৈনরা দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল।[৩৩৯] অভিলিখনের প্রমাণ থেকে জানা যায় যে, খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় বা প্রথম শতাব্দীতেও দক্ষিণ ভারতে জৈন সাধুরা বাস করতেন এবং প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ থেকে বোঝা যায় খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে গুজরাতের সৌরাষ্ট্র অঞ্চলে জৈন সাধুরা থাকতেন।[৩৪০]
রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা জৈনধর্মের বিকাশ ও পতনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।[৩৪১] খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রাষ্ট্রকূট রাজবংশের হিন্দু রাজারা প্রধান প্রধান জৈন গুহামন্দিরগুলির পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন।[৩৪২] সপ্তম শতাব্দীতে রাজা হর্ষবর্ধন জৈনধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্মের সকল সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন।[৩৪৩] পল্লব রাজা প্রথম মহেন্দ্রবর্মণ (৬০০-৬৩০ খ্রিস্টাব্দ) জৈনধর্ম ত্যাগ করে শৈবধর্ম গ্রহণ করেন।[৩৪৪] তাঁর লেখা মত্তবিলাস প্রহসন-এ কয়েকটি শৈব সম্প্রদায় ও বৌদ্ধদের উপহাস করা হয়েছে এবং জৈন সাধুদের ঘৃণ্য আখ্যা দেওয়া হয়েছে।[৩৪৫] ৭০০ থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দে যাদব রাজবংশ ইলোরা গুহাসমূহে অনেকগুলি মন্দির নির্মাণ করেছিল।[৩৪৬][৩৪৭][৩৪৮]
অষ্টম শতাব্দীতে রাজা আম জৈনধর্মে ধর্মান্তরিত হন। এই যুগেই জৈন তীর্থযাত্রার প্রথাটি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।[৩৪৯] খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীতে চালুক্য রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মূলরাজ নিজে জৈন না হলেও একটি জৈন মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[৩৫০] একাদশ শতাব্দীতে কলচুরির রাজা দ্বিতীয় বিজলের মন্ত্রী বসব অনেক জৈনকে লিঙ্গায়েত শৈব সম্প্রদায়ে ধর্মান্তরিত করেন। লিঙ্গায়েতরা অনেক জৈন মন্দির ধ্বংস করে এবং সেগুলিকে নিজেদের উপাসনালয়ে পরিণত করে।[৩৫১] হোয়সল রাজা বিষ্ণুবর্ধন (আনুমানিক ১১০৮-১১৫২ খ্রিস্টাব্দ) রামানুজের প্রভাবে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন এবং অধুনা কর্ণাটক ভূখণ্ডে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে।[৩৫২]
মধ্যযুগ
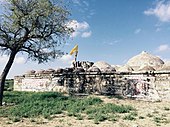
ভারতীয় উপমহাদেশ মুসলমান বিজয়ের পরে জৈনরা মুসলমান শাসকদের নিপীড়নের শিকার হন।[৩৫৪] মাহমুদ গজনি (১০০১), মহম্মদ ঘোরি (১১৭৫) ও আলাউদ্দিন খিলজি (১২৯৮) প্রমুখ মুসলমান শাসকেরা জৈন সম্প্রদায়ের উপর আরও অত্যাচার চালায়।[৩৫৫] তারা জৈনদের মূর্তিগুলি ধ্বংস করে এবং জৈন মন্দিরগুলিকে হয় ধ্বংস করে বা সেগুলিকে মসজিদে রূপান্তরিত করেছিল। তবে মুসলমান শাসকদের মধ্যে কয়েকজন ব্যতিক্রমীও ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, সম্রাট আকবর (১৫৪২টেমপ্লেট:Nsndns১৬০৫) তাঁর কিংবদন্তি ধর্মীয় সহিষ্ণুতার কারণে জৈনদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে জৈনদের পর্যুষন উৎসবে খাঁচাবন্দী পাখিদের মুক্তি দেওয়ার ও প্রাণীহত্যা বন্ধ রাখার নির্দেশ দিতেন।[৩৫৬] আকবরের রাজত্বকাল সমাপ্ত হওয়ার পর সপ্তদশ শতাব্দীতে জৈনরা আবার প্রবল মুসলমান নিপীড়নের সম্মুখীন হন।[৩৫৭][৩৫৮] ঐতিহ্যগতভাবে জৈন সম্প্রদায় ছিল ব্যাংকার ও ধনিক শ্রেণি এবং তা মুসলমান শাসকদের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। যদিও ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমান শাসনকালে তাঁরা কদাচিৎই রাজনৈতিক ক্ষমতার অংশ হয়েছিলেন।[৩৫৯]
ঔপনিবেশিক যুগ
১৮৯৩ সালে প্রথম বিশ্ব ধর্ম মহাসভায় জৈনধর্মের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন বীরচন্দ গান্ধী নামে এক বিশিষ্ট গুজরাতি জৈন পণ্ডিত। তিনি জৈনদের অধিকার রক্ষার জন্য আন্দোলন করেছিলেন এবং জৈনধর্ম সম্পর্কে বহু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন এবং বক্তৃতা দিয়েছিলেন। [৩৬০][৩৬১]
গুজরাত অঞ্চলে জৈনধর্মের পুনঃপ্রচলনের পুরোভাগে ছিলেন শ্রীমদ্ রাজচন্দ্র নামে এক অতীন্দ্রিয়বাদী, কবি ও দার্শনিক। ১৮৮৭ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি তিনি স্যার ফ্রামজি কোয়াসজি ইনস্টিটিউটে শতাবধান (১০০ অবধান) সম্পূর্ণ করেছিলেন। এর ফলে তিনি প্রশংসা ও জনপ্রিয়তা দুইই অর্জন করেছিলেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও জনসাধারণ কর্তৃক তিনি একাধিক স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সেই সঙ্গে কৈশোরেই তিনি "সাক্ষাৎ সরস্বতী" উপাধি অর্জন করেছিলেন।[৩৬২][৩৬৩] জাতীয় সংবাদপত্রগুলিতে তাঁর কাজকর্ম বহুল প্রচার লাভ করেছিল।[৩৬৪] বিশ্ব ধর্ম মহাসভায় বীরচন্দ গান্ধী শ্রীমদ্ রাজচন্দ্রের কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করেছিলেন।[৩৬৫]
তিনি মহাত্মা গান্ধীর অন্যতম আধ্যাত্মিক গুরু হিসেবেও সুপরিচিত ছিলেন।[৩৬৬] ১৮৯১ সালে বোম্বাই (অধুনা মুম্বই) শহরে তাঁদের সাক্ষাৎ হয় এবং গান্ধী যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় ছিলেন তখন পত্রবিনিময়ের মাধ্যমে তাঁদের অনেক কথোপকথন হয়েছিল। নিজের আত্মজীবনী দ্য স্টোরি অফ মাই এক্সপেরিমেন্টস উইথ ট্রুথ গ্রন্থে শ্রীমদ্ রাজচন্দ্রের প্রতি নিজের মনোভাব প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী তাঁকে নিজের "গুরু ও সহায়ক" এবং তাঁর "আধ্যাত্মিক সংকটকালের মুহুর্তে আশ্রয়" বলে উল্লেখ করেন। শ্রীমদ্ রাজচন্দ্রের উপদেশাবলি প্রত্যক্ষভাবে গান্ধীর অহিংস নীতিকে প্রভাবিত করেছিল।[৩৬৭][৩৬৮][৩৬৬]
ঔপনিবেশ যুগের প্রতিবেদনে ও খ্রিস্টীয় মিশনারিদের চোখে জৈনধর্মকে নানা চোখে দেখা হয়েছিল। কেউ এই ধর্মকে হিন্দুধর্মের, কেউ বা বৌদ্ধধর্মের একটি সম্প্রদায় মনে করেছিলেন; আবার কেউ বা এটিকে আলাদা একটি ধর্ম মনে করেছিলেন।[৩৬৯][৩৭০][৩৭১] পৌত্তলিক সৃষ্টিকর্তা দেবদেবীতে অবিশ্বাসী জৈনরা খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হতে অস্বীকার করায় খ্রিস্টীয় ধর্মপ্রচারকেরা বিফল মনোরথ হয়েছিলেন। সেই সঙ্গে চম্পৎ রাই জৈন প্রমুখ ঔপনিবেশিক যুগের জৈন পণ্ডিতেরা জৈনধর্মের বিরুদ্ধ সমালোচনা এবং খ্রিস্টীয় ধর্মপ্রচারকদের ভ্রান্ত ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন।[৩৭২] খ্রিস্টীয় ও ইসলামীয় ধর্মপ্রচারকেরা জৈন প্রথা ও রীতিনীতিগুলিকে পৌত্তলিক ও কুসংস্কারমূলক মনে করতেন।[৩৭৩] জন ই. কর্ট বলেছেন যে, এই জাতীয় সমালোচনাগুলি ত্রুটিযুক্ত এবং খ্রিস্টানদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একই ধরণের রীতিনীতিগুলিকে উপেক্ষা করেই করা হয়েছিল।[৩৭৪]
ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার ও বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য আইন প্রণয়ন করে নগ্ন অবস্থায় ঘুরে বেড়ানোকে গ্রেফতারিযোগ্য অপরাধ আখ্যা দেয়। এই আইনের ফলে বিশেষ প্রভাব পড়েছিল জৈন দিগম্বর সাধুদের উপর।[৩৭৫] অখিল ভারতীয় জৈন সমাজ এই আইনের বিরোধিতা করে বলে যে এতে জৈনদের ধর্মীয় অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। আচার্য শান্তিসাগর ১৯২৭ সালে বোম্বাই শহরে প্রবেশ করেন; কিন্তু তাঁকে দেহ বস্ত্রাচ্ছাদিত করতে বাধ্য করা হয়। তারপর তিনি নিজের অনুগামী নিয়ে নগ্ন হয়ে ভারতব্যাপী দিগম্বর তীর্থযাত্রায় বের হন। মহারাষ্ট্র অঞ্চলের দেশীয় রাজারা তাঁকে স্বাগত জানান।[৩৭৫] ব্রিটিশ রাজত্বে দিগম্বর সাধুদের উপর এই নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে এবং এই আইন প্রত্যাহারের জন্য শান্তিসাগর অনশন করেছিলেন।[৩৭৬] স্বাধীনতা লাভের পর ভারতে আইনগুলি প্রত্যাহৃত হয়।[৩৭৭]
আধুনিক যুগ
আচার্য সম্মানে বিভূষিতা প্রথম নারী ছিলেন চন্দনাজি। ১৯৮৭ সালে তিনি এই সম্মান অর্জন করেন।[৩৭৮]
জৈনধর্মের অনুগামীদের বলা হয় "জৈন"। এই শব্দটি উৎসারিত হয়েছে সংস্কৃত জিন (বিজয়ী) শব্দটি থেকে। জিন বলতে সেই সব সর্বজ্ঞ ব্যক্তিদের বোঝায় যাঁরা মোক্ষের পথ প্রদর্শন করান।[৩৭৯][৩৬] জৈনদের অধিকাংশই বর্তমানে ভারতে বসবাস করেন। সমগ্র বিশ্বে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ জৈনধর্মের অনুগামী।[৩৮০][৩৮১] সেই হিসেবে জগতের প্রধান ধর্মসমূহের তুলনায় জৈনধর্ম ক্ষুদ্র একটি ধর্মবিশ্বাস। সমগ্র ভারতের জনসংখ্যার ০.৩৭ শতাংশ জৈন ধর্মাবলম্বী। এঁদের অধিকাংশই বসবাস করেন মহারাষ্ট্র (২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী ১৪ লক্ষ,[৩৮২] ভারতীয় জৈনদের ৩১.৪৬ শতাংশ), রাজস্থান (১৩.৯৭ শতাংশ), গুজরাত (১৩.০২ শতাংশ) ও মধ্যপ্রদেশ (১২.৭৪ শতাংশ) রাজ্যে। এছাড়া কর্ণাটক (৯.৮৯ শতাংশ), উত্তরপ্রদেশ (৪.৭৯ শতাংশ), দিল্লি (৩.৭৩ শতাংশ) ও তামিলনাড়ুতেও (২.০১ শতাংশ) জৈনদের উপস্থিতি উল্লেখনীয়।[৩৮২] ভারতের বাইরে জৈনরা বাস করেন ইউরোপ, যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা,[৩৮৩] অস্ট্রেলিয়া ও কেনিয়ায়।[৩৮৪] এছাড়া জাপানেও দ্রুত হারে জৈনধর্ম প্রসার লাভ করছে; সে-দেশে পাঁচ হাজারেরও বেশি পরিবার জৈনধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে।[৩৮৫]
২০১৫-১৬ সালে গৃহীত জাতীয় পরিবার ও স্বাস্থ্য সমীক্ষা (এনএফএইচএস-৪) অনুযায়ী, জৈনরা ভারতের ধনীতম সম্প্রদায়।[৩৮৬] ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী, ভারতে বয়সের দিক থেকে সাত বছর থেকে বরিষ্ঠতম ব্যক্তিদের মধ্যে জৈন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই সাক্ষরতার হার সবচেয়ে বেশি (৮৭ শতাংশ) এবং অধিকাংশই স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।[৩৮৭] অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের বাদ দিলে ভারতে জৈনদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ৯৭ শতাংশ। ভারতে জৈনদের মধ্যে লিঙ্গানুপাত ৯৪০; অবশ্য ০-৬ বছর বয়সীদের মধ্যে এই লিঙ্গানুপাতের ক্ষেত্রে জৈনরা দ্বিতীয় নিম্নতম (প্রতি ১০০০ বালকে ৮৭০ জন বালিকা)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্বদেশে এই স্থানে নিম্নতম স্থানের অধিকারী শিখরা।[৩৮৮]
কয়েকটি প্রথা ও মতবাদের জন্য জৈনধর্ম বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রণী নেতা মহাত্মা গান্ধী জৈনধর্মের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে বলেছিলেন:[৩৮৯]
বিশ্বে আর কোনও ধর্মই অহিংসার নীতিটিকে এত গভীর ও প্রণালীবদ্ধভাবে ব্যাখ্যা করেনি, যেমনটি জৈনধর্মে প্রতিটি মানুষের জীবনে এটির প্রয়োগযোগ্যতার সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। অহিংসার মঙ্গলময় নীতিটি যখনই বিশ্ববাসীর দেহান্ত ও পরকালেও [কিছু] অর্জনের জন্য আরোপিত হবে, তখন নিশ্চিতভাবেই জৈনধর্ম সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করবে এবং মহাবীর নিশ্চয়ই অহিংসার শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা হিসেবে সম্মানীত হবেন।[৩৯০]
আরও দেখুন
পাদটীকা
- ↑ সকল জৈন উপসম্প্রদায় অবশ্য এই বিষয়ে একমত নয়। উদাহরণস্বরূপ, প্রায় আড়াই লক্ষ অনুগামীর তেরাপন্থি জৈন পরম্পরা মনে করে দয়ার্দ্র চিত্তে দানের ন্যায় সৎকর্ম এবং পাপের মতো দুষ্কর্ম উভয়েই ব্যক্তির আত্মাকে জাগতিক নৈতিকতার বন্ধনে আবদ্ধ করে। এই পরম্পরায় মনে করায় মানুষের সীমাবদ্ধ দৃষ্টিকোণ থেকে যে কোনও কর্মই "চরম অহিংসতা"-র এক অপলাপে পৌঁছে দেয়। এই পন্থায় তাই সাধু ও সাধ্বীদের যে কোনও সত্ত্বাকে আঘাত করা থেকে প্রতিহত থেকে ও তাদের সাহায্য করে মোক্ষ অনুসন্ধান করতে বলে।[৬৫]
- ↑ বৌদ্ধ ও হিন্দুসাহিত্যের মতো জৈনসাহিত্যেও খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে হিংসা ও অহিংসার দিকগুলি নিয়ে দ্বিমত রয়েছে।[৭৮]
- ↑ জৈনধর্মের অহিংসা নীতিতে কোনও সাধু বা সাধ্বীকে বৃক্ষ সহ সকল জীবিত সত্ত্বাকে স্পর্শ অথবা বিরক্ত করা থেকে বিরত থাকতে হয়। এই ধর্মে জলে সাঁতার কাটা, আগুন জ্বালানো বা নেভানো, শূন্যে হস্ত আস্ফালনও নিষিদ্ধ। কারণ, এই ধরনের কাজগুলি সেই সব বস্তুর অবস্থায় স্থিত জীবদের নিপীড়ন বা আঘাত করতে পারে।[৭২]
- ↑ প্রথমটি হল "দেশবকশিক" (আবদ্ধ পরিমণ্ডলে বাস করে জাগতিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ রাখা)। তৃতীয়টি হল "পোসধোপবাস" (শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমী ও চতুর্দশী তিথিতে উপবাস)। চতুর্থটি হল "দান" (জৈন সাধু, সাধ্বী বা আধ্যাত্মিক ব্যক্তিদের ভিক্ষাপ্রদান)।[১৩৭]
- ↑ ডুন্ডাসের মতে, আদিকালীন জৈনধর্মে সম্ভবত সামায়িকের অর্থ ছিল সম্যক চরিত্র।[১৪২]
- ↑ এগুলি হিন্দুধর্মের চার বেদ হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির।[২১৪]
- ↑ "জৈনদের কাছে "তত্ত্বার্থসূত্র" নামে পরিচিত গ্রন্থটি জৈনদের সকল চারটি পরম্পরাতেই তাঁদের ধর্মের আদিতম, সর্বাধিক প্রামাণ্য ও সর্ব-সমন্বিত সংক্ষিপ্তসার বলে স্বীকৃত হয়।"[২১৭]
- ↑ রিচার্ড গমব্রিচ ও অন্যান্য গবেষকদের মতে বৌদ্ধধর্মও প্রাচীন বর্ণপ্রথা প্রত্যাখ্যান করেনি বা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেনি। এই ধর্মটিও পুনর্জন্ম ও দুঃখের হাত থেকে ব্যক্তির মুক্তির উপরেই দৃষ্টি আরোপ করেছিল। বহির্ভারতের বৌদ্ধ সমাজে ও সংঘগুলিতে বর্ণপ্রথার কথা নথিবদ্ধ হয়েছে। গমব্রিচ বলেছেন, "কোনও কোনও আধুনিকতাবাদী তো এতদূর পর্যন্ত বলেছেন যে বুদ্ধ সামগ্রিকভাবে বর্ণপ্রথার বিরুদ্ধে ছিলেন: কিন্তু কার্যত তা নয়, বরং [এটি] পাশ্চাত্য লেখকদের [রচনা থেকে] সংগৃহীত ভ্রান্তিগুলির একটি।" (মূল উদ্ধৃতি: "Some modernists go so far as to say that the Buddha was against caste altogether: this is not the case, but is one of the mistakes picked up from western authors.")[২৪৬][২৪৭][২৪৮]
- ↑ জৈন সন্ন্যাসীদের বস্ত্র বা ভিক্ষাপাত্রের ন্যায় ভিক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরণ ন্যায্য বা বৈধ কিনা তা মোক্ষলাভের পথে এক প্রতিবন্ধকতা জ্ঞান করা হয়। জৈনধর্মের বিভিন্ন উপসম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদের এটি একটি প্রধান উপাদান থেকে যায় এবং দিগম্বর-শ্বেতাম্বর বিভাজনের জন্য এই বিবাদ অংশতভাবে দায়ী। যদিও বিভাজনের এই শিকড়টিকে শুধুমাত্র সন্ন্যাসীদের বস্ত্র ও ভিক্ষাপাত্রের মধ্যে বিভাজনের মধ্যে আবদ্ধ রাখলে সেটি হবে অতিমাত্রায় অতিসরলীকরণ।[২৫২]
- ↑ কোনও কোনও গ্রন্থে এই স্থানটিকে সম্মেত পর্বত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[২৭৮]
তথ্যসূত্র
- ↑ ""Jainism" (ODE)", অক্সফোর্ড ডিকশনারিজ
- ↑ "তীর্থংকর", জৈনিজম নলেজ
- ↑ ইয়ানডেল ১৯৯৯, পৃ. ২৪৩।
- ↑ সিনহা ১৯৪৪, পৃ. ২০।
- ↑ ক খ গ গ্রিমস ১৯৯৬, পৃ. ১১৮–১১৯।
- ↑ নেমিচন্দ্র ও বলবীর ২০১০, পৃ. ভূমিকার প্রথম পৃষ্ঠা।
- ↑ চম্পৎ রাই জৈন ১৯১৭, পৃ. ১৫।
- ↑ ফন গ্লাসেনাপ ১৯২৫, পৃ. ১৮৮–১৯০।
- ↑ জৈনি ১৯৮০, পৃ. ২১৯–২২৮।
- ↑ ফন গ্লাসেনাপ ১৯২৫, পৃ. ১৭৭–১৮৭।
- ↑ ক খ জৈনি ১৯৯৮, পৃ. ১৫১।
- ↑ ডুন্ডাস ২০০২, পৃ. ৯৬–৯৮।
- ↑ বেইলি ২০১২, পৃ. ১০৮।
- ↑ লং ২০১৩, পৃ. ১৮, ৯৮–১০০।
- ↑ জৈনি ১৯৯৮, পৃ. ১০৩।
- ↑ ক খ জৈনি ১৯৯৮, পৃ. ১০৪–১০৬।
- ↑ ফন গ্লাসেনাপ ১৯২৫, পৃ. ১৯৪।
- ↑ লং ২০১৩, পৃ. ৯২–৯৫।
- ↑ ডুন্ডাস ২০০২, পৃ. ৯৯–১০৩।
- ↑ ক খ জৈনি ১৯৮০, পৃ. ২২৬।
- ↑ জৈনি ১৯৮০, পৃ. ২২৮।
- ↑ জৈনি ২০০০, পৃ. ১৩০–১৩১।
- ↑ জৈনি ১৯৮০, পৃ. ২২৩–২২৫।
- ↑ জৈনি ১৯৮০, পৃ. ২২৪–২২৫।
- ↑ শেঠিয়া ২০০৪, পৃ. ৩০–৩১।
- ↑ জৈনি ১৯৮০, পৃ. ২২৭–২২৮।
- ↑ ক খ ডুন্ডাস ২০০২, পৃ. ১০৪–১০৫।
- ↑ জৈনি ১৯৮০, পৃ. ২২৫।
- ↑ ক খ জৈনি ১৯৮০, পৃ. ২২২–২২৩।
- ↑ ডুন্ডাস ২০০২, পৃ. ৯০–৯২।
- ↑ ফন গ্লাসেনাপ ১৯২৫, পৃ. ২৪১।
- ↑ ক খ গ লং ২০১৩, পৃ. ৮৩–৮৫।
- ↑ নাথুভাই শাহ ১৯৯৮, পৃ. ২৫।
- ↑ ক খ ডনিগার ১৯৯৯, পৃ. ৫৫১।
- ↑ বিজয় কে. জৈন ২০১১, পৃ. ৪৬।
- ↑ ক খ উপিন্দর সিং ২০১৬, পৃ. ৩১৩।
- ↑ ফন গ্লাসেনাপ ১৯২৫, পৃ. ২৭১–২৭২।
- ↑ ডুন্ডাস ২০০২, পৃ. ১৩।
- ↑ চম্পৎ রাই জৈন ১৯২৯বি, পৃ. ১২৪।
- ↑ দালাল ২০১০এ, পৃ. ২৭।
- ↑ ক খ জিমার ১৯৫৩, পৃ. ১৮২।
- ↑ ফন গ্লাসপেনাপ ১৯২৫, পৃ. ২৪১।
- ↑ ফন গ্লাসেনাপ ১৯২৫, পৃ. ২৪১–২৪২।
- ↑ ফন গ্লাসেনাপ ১৯২৫, পৃ. ২৪১–২৪৩।
- ↑ ফন গ্লাসেনাপ ১৯২৫, পৃ. ২৪৭–২৪৯, ২৬২–২৬৩।
- ↑ ডুন্ডাস ২০০২, পৃ. ২০–২১, ৩৪–৩৫, ৭৪, ৯১, ৯৫–৯৬, ১০৩।
- ↑ ক খ গ ফন গ্লাসেনাপ ১৯২৫, পৃ. ২৬২–২৬৩।
- ↑ ডুন্ডাস ২০০২, পৃ. ৯১, ৯৫–৯৬।
- ↑ র্যানকিন ও মার্ডিয়া ২০১৩, পৃ. ৪০।
- ↑ গ্রিমস ১৯৯৬, পৃ. ২৩৮।
- ↑ ক খ সোনি ২০০০, পৃ. ৩৬৭–৩৭৭।
- ↑ ডুন্ডাস ২০০২, পৃ. ৭৫–৭৬, ১৩১, ২২৯–২৩০।
- ↑ ডুন্ডাস ২০০২, পৃ. ২২৯–২৩০।
- ↑ এস. এ. জৈন ১৯৯২, পৃ. ১৬।
- ↑ ক খ বিজয় কে. জৈন ২০১১, পৃ. ৬।
- ↑ ক খ কর্ট ২০০১এ, পৃ. ৬–৭।
- ↑ ফোর ২০১৫, পৃ. ৯–১০, ৩৭।
- ↑ জৈনি ১৯৯৮, পৃ. ১৪১–১৪৭।
- ↑ ক খ জৈনি ১৯৯৮, পৃ. ১৪৮, ২০০।
- ↑ কর্ট ২০০১এ, পৃ. ৭।
- ↑ ক খ গ ঘ ডুন্ডাস ২০০২, পৃ. ১৬০।
- ↑ ক খ মারখাম ও লোর ২০০৯, পৃ. ৭১।
- ↑ ক খ গ প্রাইস ২০১০, পৃ. ৯০।
- ↑ ক খ গ ডুন্ডাস ২০০২, পৃ. ১৬০–১৬২।
- ↑ ফ্লুগেল ২০০২, পৃ. ১২৬৬–১২৬৭।
- ↑ Dundas 2002, পৃ. 160–162।
- ↑ সুন্দররাজন ও মুখোপাধ্যায় ১৯৯৭, পৃ. ৩৯২–৪১৭।
- ↑ ইজাওয়া ২০০৮, পৃ. ৭৮–৮১।
- ↑ শেঠিয়া ২০০৪, পৃ. ২।
- ↑ উইন্টারনিৎজ ১৯৯৩, পৃ. ৪০৯।
- ↑ Dundas 2002, পৃ. 88–89, 257–258।
- ↑ ক খ টেলর ২০০৮, পৃ. ৮৯২–৮৯৪।
- ↑ গ্র্যানফ ১৯৯২।
- ↑ ক খ ডুন্ডাস ২০০২, পৃ. ১৬২–১৬৩।
- ↑ লোরেনজেন ১৯৭৮, পৃ. ৬১–৭৫।
- ↑ Dundas 2002, পৃ. 163।
- ↑ মূল উদ্ধৃতি: "anybody engaged in a religious activity who was forced to fight and kill somebody would not lose any spiritual merit but instead attain deliverance"
- ↑ ওলসন ২০১৪, পৃ. ১–৭।
- ↑ ক খ গ ঘ চরিত্রপ্রজ্ঞ ২০০৪, পৃ. ৭৫–৭৯।
- ↑ ক খ ডুন্ডাস ২০০২, পৃ. ২২৯–২৩১।
- ↑ জৈন ফিলোজফি ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে, আইইপি, মার্ক ওয়েন ওয়েব, টেক্সাস টেক বিশ্ববিদ্যালয়
- ↑ সোয়ার্ৎজ ২০১৮।
- ↑ মতিলাল ১৯৯০, পৃ. ৩০১–৩০৫।
- ↑ বালসারোউইকজ ২০১৫, পৃ. ২০৫–২১৮।
- ↑ মতিলাল ১৯৯৮, পৃ. ১২৮–১৩৫।
- ↑ ডুন্ডাস ২০০২, পৃ. ৯০–৯৯, ১০৪–১০৫, ২২৯–২৩৩।
- ↑ ক খ ডুন্ডাস ২০০২, পৃ. ২৩২–২৩৪।
- ↑ শেঠিয়া ২০০৪, পৃ. ৮৬–৯১।
- ↑ লং ২০০৯, পৃ. ৯৮–১০৬।
- ↑ ডুন্ডাস ২০০২, পৃ. ২৩৩।
- ↑ ক খ গ নাথুভাই শাহ ২০০৪, পৃ. ১১২।
- ↑ ক খ ডুন্ডাস ২০০২, পৃ. ১১৭, ১৫২।
- ↑ নাথুভাই শাহ ২০০৪, পৃ. ১১২–১১৩।
- ↑ ক খ গ ঘ ফন গ্লাসেনাপ ১৯২৫, পৃ. ২২৮–২৩১।
- ↑ ক খ গ ঘ ফন গ্লাসেনাপ ১৯২৫, পৃ. ২২৮।
- ↑ ক খ গ শাহ, প্রবীণ কে. (২০১১), ফাইভ গ্রেট ভওজ (মহা-ব্রতজ) অফ জৈনিজম, হার্বার্ড ইউনিভার্সিটি লিটারেচার সেন্টার, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা, সংগ্রহের তারিখ ৭ মে ২০১৭
- ↑ বিজয় কে. জৈন ২০১২, পৃ. ৩৩।
- ↑ বিজয় কে. জৈন ২০১২, পৃ. ৬৮।
- ↑ ফন গ্লাসেনাপ ১৯২৫, পৃ. ২৩১।
- ↑ লং ২০০৯, পৃ. ১০৯।
- ↑ বিজয় কে. জৈন ২০১২, পৃ. ৮৭–৮৮।
- ↑ টুকোল ১৯৭৬, পৃ. ৫।
- ↑ ডুন্ডাস ২০০২, পৃ. ১৭৯–১৮০।
- ↑ জৈনি ২০০০, পৃ. ১৬।
- ↑ টুকোল ১৯৭৬, পৃ. ৭।
- ↑ উইলিয়ামস ১৯৯১, পৃ. ১৬৬–১৬৭।
- ↑ ক খ কর্ট ২০০১এ, পৃ. ১১৮–১২২।
- ↑ কিউভার্নস্টর্ম ২০০৩, পৃ. ১১৩।
- ↑ কিউভার্নস্টর্ম ২০০৩, পৃ. ১৬৯–১৭৪, ১৭৮–১৯৮ পাদটীকা সহ।
- ↑ কিউভার্নস্টর্ম ২০০৩, পৃ. ২০৫–২১২ পাদটীকা সহ।
- ↑ বালসারোউইকজ ২০১৫, পৃ. ১৪৪–১৫০।
- ↑ কর্ট ২০০১এ, পৃ. ১২০–২১।
- ↑ ক খ কর্ট ২০০১এ, পৃ. ১২০–১২২।
- ↑ কিউভার্নস্টর্ম ২০০৩, পৃ. ১৮২ সঙ্গে পাদটীকা ৩।
- ↑ জনসন ১৯৯৫, পৃ. ১৯৬–১৯৭।
- ↑ কিউভার্নস্টর্ম ২০০৩, পৃ. ১৬৯–১৭৪, ১৭৮–১৯৮ সঙ্গে পাদটীকা।
- ↑ কর্ট ২০০১এ, পৃ. ১২১–১২২।
- ↑ শান্তি লাল জৈন ১৯৯৮, পৃ. ৫১।
- ↑ বালসারোউইকজ ২০১৫, পৃ. ১৫–১৮, ৪১–৪৩।
- ↑ কর্ট ২০০১এ, পৃ. ৪৮–৪৯।
- ↑ বাল্লসারোউইকজ ২০০৯, পৃ. ১৭।
- ↑ নাথুভাই শাহ ২০০৪, পৃ. ২–৩।
- ↑ বিজয় কে. জৈন ২০১৩, পৃ. ১৯৭।
- ↑ ডুন্ডাস ২০০২, পৃ. ১৫২, ১৬৩–১৬৪।
- ↑ জৈনি ১৯৯৮, পৃ. ১৯০।
- ↑ ভুর্স্ট ২০১৫, পৃ. ১০৫।
- ↑ সানগেভ ১৯৮০, পৃ. ২৬০।
- ↑ ক খ জৈনি ২০০০, পৃ. ২৮৫।
- ↑ ক খ উইলি ২০০৯, পৃ. ৮৫।
- ↑ উইলি ২০০৯, পৃ. ৮৫–৮৬।
- ↑ রাম ভূষণ প্রসাদ সিং ২০০৮, পৃ. ৯২–৯৪।
- ↑ ক খ উইলি ২০০৯, পৃ. ৭২।
- ↑ উইলি ২০০৯, পৃ. ৭২, ৮৫–৮৬।
- ↑ Wiley 2009, পৃ. 85।
- ↑ ক খ উইলি ২০০৯, পৃ. ৮৬।
- ↑ ক খ ডুন্ডাস ২০০২, পৃ. ১৬৬–১৬৯।
- ↑ ক খ জৈনি ১৯৯৮, পৃ. ১৮০–১৮১।
- ↑ জৈনি ১৯৯৮, পৃ. ১৮০–১৮২।
- ↑ এস. এ. জৈন ১৯৯২, পৃ. ২৬১।
- ↑ নাথুভাই শাহ ২০০৪, পৃ. ১২৮–১৩১।
- ↑ Johnson 1995, পৃ. 189–190।
- ↑ ডুন্ডাস ২০০২, পৃ. ১৭০।
- ↑ ক খ গ ডুন্ডাস ২০০২, পৃ. ১৮৭–১৮৯।
- ↑ ক খ জৈনি ১৯৯৮, পৃ. ১৬২–১৬৫, ২৯৫–২৯৬।
- ↑ জৈনি ১৯৯৮, পৃ. ২৯১–২৯৯।
- ↑ উইলি ২০০৯, পৃ. ১৮৬–১৮৭।
- ↑ জৈনি ১৯৯৮, পৃ. ২৯৫–২৯৯।
- ↑ ডুন্ডাস ২০০২, পৃ. ৪০।
- ↑ কর্ট ২০১০, পৃ. ১৮২–১৮৪।
- ↑ জৈনি ১৯৯৮, পৃ. ১৯৬, ৩৪৩, ৩৪৭।
- ↑ জৈনি ১৯৯৮, পৃ. ১৯৬–১৯৯।
- ↑ ক খ উইলি ২০০৯, পৃ. ৪৫–৪৬, ২১৫।
- ↑ লিন্ডসে জোনস ২০০৫, পৃ. ৪৭৭১।
- ↑ উইলি ২০০৯, পৃ. ৩৩, ৫৯, ৯২, ১৩৮, ১৯১।
- ↑ কর্ট ১৯৮৭, পৃ. ২৩৫–২৫৫।
- ↑ মিশ্র ও রায় ২০১৬, পৃ. ১৪১–১৪৮।
- ↑ দালাল ২০১০এ, পৃ. ৩৬৫।
- ↑ ক খ জৈনি ১৯৯৮, পৃ. ১৯৯–২০০।
- ↑ প্রতাপাদিত্য পাল ১৯৮৬, পৃ. ২৯।
- ↑ ডুন্ডাস ২০০২, পৃ. ২০৪–২০৫।
- ↑ সালভাডোরি ১৯৮৯, পৃ. ১৬৯–১৭০।
- ↑ বাব ১৯৯৬, পৃ. ৩২–৩৩।
- ↑ ক খ ডুন্ডাস ২০০২, পৃ. ৮১–৮২।
- ↑ নায়নার ২০০৫, পৃ. ৩৫।
- ↑ ভুর্স্ট ২০১৫, পৃ. ১০৭।
- ↑ গঘ ২০১২, পৃ. ১–৪৭।
- ↑ কর্ট ২০০১বি, পৃ. ৪১৭–৪১৯।
- ↑ ক খ গ ঘ দালাল ২০১০এ, পৃ. ১৬৪, ২৮৪।
- ↑ ক খ মেলটন ২০১১, পৃ. ৬৭৩।
- ↑ দালাল ২০১০এ, পৃ. ২৮৪।
- ↑ কর্ট ১৯৯৫, পৃ. ১৬০।
- ↑ ক খ দালাল ২০১০এ, পৃ. ২২০।
- ↑ নাথুভাই শাহ ২০০৪, পৃ. ২১১।
- ↑ পেশিলিস ও রাজ ২০১৩, পৃ. ৮৬।
- ↑ পেসিলিস ও রাজ ২০১৩, পৃ. ৮৬।
- ↑ পেসিলিস ও রাজ ২০১৩, পৃ. ৮৫।
- ↑ দালাল ২০১০এ, পৃ. ১৬৪।
- ↑ ডুন্ডাস ২০০২, পৃ. ৪৫।
- ↑ ক্লার্ক ও বেয়ার ২০০৯, পৃ. ৩২৬।
- ↑ ডুন্ডাস ২০০২, পৃ. ৪৭।
- ↑ ফন গ্লাসেনাপ ১৯২৫, পৃ. ৪৬।
- ↑ প্রাইস ২০১০, পৃ. ১০৪–১০৫।
- ↑ ফোর ২০১৫, পৃ. ২১–২২।
- ↑ জৈনি ১৯৯১, পৃ. ৩।
- ↑ জোন্স ও রায়ান ২০০৭, পৃ. ২১১।
- ↑ ক খ উমাকান্ত পি. শাহ ১৯৮৭, পৃ. ৫।
- ↑ ডুন্ডাস ২০০২, পৃ. ৩১–৩৩।
- ↑ কৈলাস চন্দ জৈন ১৯৯১, পৃ. ১২।
- ↑ নাথুভাই শাহ ২০০৪, পৃ. ৭৩–৭৪।
- ↑ ডুন্ডাস ২০০২, পৃ. ২১।
- ↑ উমাকান্ত পি. শাহ ১৯৮৭, পৃ. ১৭।
- ↑ উমাকান্ত পি. শাহ ১৯৮৭, পৃ. ৭৯–৮০।
- ↑ ক খ দালাল ২০১০এ, পৃ. ১৬৭।
- ↑ কর্ট ২০০১এ, পৃ. ৪৭।
- ↑ ফুগেল ২০০৬, পৃ. ৩১৪–৩৩১, ৩৫৩–৩৬১।
- ↑ লং ২০১৩, পৃ. ৩৬–৩৭।
- ↑ ক খ হার্ভে ২০১৬, পৃ. ১৮২–১৮৩।
- ↑ ডুন্ডাস ২০০২, পৃ. ৫৫–৫৯।
- ↑ ভ্যালেলি ২০০২, পৃ. ১৫।
- ↑ ডুন্ডাস ২০০২, পৃ. ৫৬।
- ↑ ক খ গ জৈনি ২০০০, পৃ. ১৬৭।
- ↑ ফ্লুগেল ২০০৫, পৃ. ১৯৪–২৪৩।
- ↑ সূর্যপ্রজ্ঞপ্তিসূত্র ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ১৫ জুন ২০১৭ তারিখে, দ্য শোয়েন কালেকশন, লন্ডন/অসলো
- ↑ ক খ ডুন্ডাস ২০০২, পৃ. ৬০–৬১।
- ↑ চম্পৎ রাই জৈন ১৯২৯বি, পৃ. ১৩৫–১৩৬।
- ↑ ফন গ্লাসেনাপ ১৯২৫, পৃ. ১০৯–১১০।
- ↑ ডুন্ডাস ২০০২, পৃ. ৬১।
- ↑ ফন গ্লাসেনাপ ১৯২৫, পৃ. ১১২-১১৩, ১২১–১২২।
- ↑ বিজয় কে. জৈন ২০১৬, পৃ. বারো।
- ↑ জৈনী ১৯৯৮, পৃ. ৭৮–৮১।
- ↑ ফন গ্লাসেনাপ ১৯২৫, পৃ. ১২৪।
- ↑ ফন গ্লাসেনাপ ১৯২৫, পৃ. ১২১–১২২।
- ↑ ফন গ্লাসেনাপ ১৯২৫, পৃ. ১২৩–১২৪।
- ↑ দালাল ২০১০এ, পৃ. ১৬৪–১৬৪।
- ↑ ক খ ফন গ্লাসেনাপ ১৯২৫, পৃ. ১২৫–১২৬।
- ↑ জোনস ও রায়ান ২০০৭, পৃ. ৪৩৯–৪৪০।
- ↑ উমাস্বাতী ১৯৯৪, পৃ. এগারো–তেরো।
- ↑ ডুন্ডাস ২০০৬, পৃ. ৩৯৫–৩৯৬।
- ↑ ফিনেগান ১৯৮৯, পৃ. ২২১।
- ↑ বারকারোউইকজ ২০০৩, পৃ. ২৫–৩৪।
- ↑ চট্টোপাধ্যায় ২০০০, পৃ. ২৮২–২৮৩।
- ↑ জৈনি ১৯৯১, পৃ. ৩২–৩৩।
- ↑ সলোমন ও হিগিনস ১৯৯৮, পৃ. ১১–২২।
- ↑ অ্যাপেলটন ২০১৬, পৃ. ১–২১, ২৫–২৭, ৫৭–৫৮, ৮২–৮৪।
- ↑ ম্যাকফাউল ২০০৬, পৃ. ২৭–২৮।
- ↑ শ ও ডেমি ২০১৭, পৃ. ৬৩৫।
- ↑ সলোমন ও হিগিনস ১৯৯৮, পৃ. ১৮–২২।
- ↑ ম্যাকফাউল ২০০৬, পৃ. ২৭–৪০।
- ↑ ডুন্ডাস ২০০২, পৃ. ৮৭–৮৮।
- ↑ লং ২০১৩, পৃ. ১২২–১২৫।
- ↑ হিরিয়ান্না ১৯৯৩, পৃ. ১৫৭–১৫৮, ১৬৮–১৬৯।
- ↑ হিরিয়ান্না ১৯৯৩, পৃ. ৫৪–৬২, ৭৭–৮২, ১৩২।
- ↑ পেরেট ২০১৩, পৃ. ২৪৭–২৪৮।
- ↑ বার্টলি ২০১৩, পৃ. ১–১০, ৭৬–৭৯, ৮৭–৯৮।
- ↑ জৈনি ১৯৯৮, পৃ. ৫৮, ১০২–১০৫।
- ↑ দালাল ২০১০বি, পৃ. ১৭৪–১৭৫।
- ↑ সলোমন ও হিগিননস ১৯৯৮, পৃ. ১৮–২২।
- ↑ ক খ জুয়েরগেনসমেয়ার ২০১১, পৃ. ৫৪।
- ↑ কেল্টিং ২০০৯, পৃ. ২০৬ টীকা ৪।
- ↑ নেসফিল্ড ১৮৮৫, পৃ. ১১৬–১১৭।
- ↑ পোপ ১৮৮০, পৃ. ৪০–৪১।
- ↑ অ্যালবার্টস ২০০৭, পৃ. ২৫৮–২৫৯।
- ↑ ডুন্ডাস ২০০২, পৃ. ১৪৭–১৪৯, ৩০৪ টীকা ২৪।
- ↑ বাব ১৯৯৬, পৃ. ১৩৭–১৪৫, ৫৪, ১৭২।
- ↑ সানগেভ ১৯৮০, পৃ. ৭৩, ৩১৬–৩১৭।
- ↑ গমব্রিক ২০১২, পৃ. ৩৪৪–৩৫৩ পাদটীকা সহ।
- ↑ অ্যালবার্টস ২০১৭, পৃ. ২৫৮–২৫৯।
- ↑ ফ্লোরিডা ২০০৫, পৃ. ১৩৪–১৩৭।
- ↑ ক খ গ ঘ জনস্টন ২০০০, পৃ. ৬৮১–৬৮৩।
- ↑ ক খ ক্যালিয়াট ২০০৩এ, পৃ. ৩০–৩৪ সঙ্গে পাদটীকা ২৮।
- ↑ ক খ হিরাকাওয়া ১৯৯৩, পৃ. ৪–৭।
- ↑ বালসারোউইকজ ২০১৫, পৃ. ৪২–৪৩।
- ↑ "নিশীথভাষ্য" ("নিশীথসূত্র" গ্রন্থে) ২৮৯; জিনদত্ত সুরি: "উপদেশরসায়ন" ২৬; ডুন্ডাস পৃ. ১৬২–১৬৩; তাহতিনেন পৃ. ৩১
- ↑ জিন্দল পৃ. ৮৯–৯০; লেইডল পৃ. ১৫৪–১৫৫; জৈনি, পদ্মনাভ এস.: অহিংসা অ্যান্ড "জাস্ট ওয়ার" ইন জৈনিজম, মূল গ্রন্থ: অহিংসা, অনেকান্ত অ্যান্ড জৈনিজম, সম্পা. তারা শেঠিয়া, নতুন দিল্লি ২০০৪, পৃ. ৫২–৬০; তাহতিনেন পৃ. ৩১
- ↑ হরিসেন, "বৃহৎকথাকোষ" ১২৪ (১০ম শতাব্দী); জিন্দল পৃ. ৯০–৯১; সানগেভ পৃ. ২৫৯
- ↑ লং ২০০৯, পৃ. ৫–৬।
- ↑ শর্মা ও ঘোষাল ২০০৬, পৃ. ১০০–১০৩।
- ↑ মিশেল ২০১৪, পৃ. ৩৮–৫২, ৬০–৬১।
- ↑ রিং, ওয়াটসন এবং শেলিংগার ১৯৯৬, পৃ. ৪৬৮–৪৭০।
- ↑ উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি গুহাসমূহ ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ২৯ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে, ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ, ভারত সরকার
- ↑ ক খ নাথুভাই শাহ ১৯৯৮, পৃ. ১৮৪।
- ↑ উমাকান্ত পি. শাহ ১৯৮৭, পৃ. ৯৫।
- ↑ কিশোর ২০১৫, পৃ. ১৭–৪৩।
- ↑ ক খ জৈন ও ফিশার ১৯৭৮, পৃ. ৯–১০।
- ↑ উইলি ২০০৯, পৃ. ১৮৪।
- ↑ ওয়েন ২০১২বি, পৃ. ১–২।
- ↑ নাথুভাই শাহ ১৯৯৮, পৃ. ১৮৩।
- ↑ নাথুভাই শাহ ১৯৯৮, পৃ. ১১৩।
- ↑ জৈন ও ফিশার ১৯৭৮, পৃ. ১৬।
- ↑ নাথুভাই শাহ ১৯৯৮, পৃ. ১৮৭।
- ↑ ক খ গ বাব ১৯৯৬, পৃ. ৬৬।
- ↑ বাব ১৯৯৬, পৃ. ৬৮।
- ↑ সেটার ১৯৮৯, পৃ. ১৯৫।
- ↑ সানগেভ ২০০১, পৃ. ১৮৮।
- ↑ বারিক, বিভূতি (২২ জুন ২০১৫), "প্ল্যান টু বিউটিফাই খণ্ডগিরি – মনুমেন্ট রিভ্যাম্প টু অ্যাট্র্যাক্ট মোর ট্যুরিস্টস", দ্য টেলিগ্রাফ, ভুবনেশ্বর, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা, সংগ্রহের তারিখ ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
- ↑ সহদেব কুমার ২০০১, পৃ. ১০৬।
- ↑ কর্ট ২০১০, পৃ. ১৩০–১৩৩।
- ↑ জেকবি ১৯৬৪, পৃ. ২৭৫।
- ↑ বার্জার ২০১০, পৃ. ৩৫২।
- ↑ "মূর্তিপূজকস, জৈনিজম", এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়নস (ফিলটার), ক্যামব্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩ অক্টোবর ২০০৭ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা
- ↑ খাজুরাহো গ্রুপ অফ মনুমেন্টস, ইউনেস্কো, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা, সংগ্রহের তারিখ ১৪ মার্চ ২০১৭
- ↑ গ্রুপ অফ মনুমেন্টস অ্যাট পাট্টাডাকাল, ইউনেস্কো, ২৬ মার্চ ২০১৪ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা, সংগ্রহের তারিখ ১৪ মার্চ ২০১৭
- ↑ বুতালিয়া ও স্মল ২০০৪, পৃ. ৩৬৭।
- ↑ ফার্গুসন ১৮৭৬, পৃ. ২৭১।
- ↑ পাণ্ড্য ২০১৪, পৃ. ১৭।
- ↑ এস. এস. কবিতা (৩১ অক্টোবর ২০১২), "নাম্মা মাদুরাই: হিস্ট্রি হিডেন ইনসাইড আ কেভ", দ্য হিন্দু, ৩ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা, সংগ্রহের তারিখ ১৫ নভেম্বর ২০১৩
- ↑ "সোর্স", proel.org, ১ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা, সংগ্রহের তারিখ ১৩ জানুয়ারি ২০১৯
- ↑ উপিন্দর সিং ২০১৬, পৃ. ৪৬০।
- ↑ ওয়েন ২০১২বি, পৃ. ৫০।
- ↑ এস. এস. কবিতা (৩ ফেব্রুয়ারি ২০১০), "প্রিজার্ভিং দ্য পাস্ট", দ্য হিন্দু, ৩ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা, সংগ্রহের তারিখ ১৫ নভেম্বর ২০১৩
- ↑ "আরিট্টপট্টি ইন্সক্রিপশন থ্রোজ লাইট অন জৈনিজম", দ্য হিন্দু, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৩, ২৩ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা, সংগ্রহের তারিখ ১৫ নভেম্বর ২০১৩
- ↑ টিৎজে ১৯৯৮।
- ↑ নগরপকর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ১০ মে ২০১৭ তারিখে, আপাত-স্থিরীকৃত তালিকা, বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী কেন্দ্র
- ↑ আরোরা ২০০৭, পৃ. ৪০৫।
- ↑ কর্ট ২০১০, পৃ. ১৮৪।
- ↑ "অ্যান্ড ইন্ডিয়া'জ ৭ ওয়ান্ডারস আর", দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ৫ আগস্ট ২০০৭, ১৮ অক্টোবর ২০১২ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা, সংগ্রহের তারিখ ৩ জানুয়ারি ২০১৩
- ↑ বোটেকর, অভিলাষ (৪ ডিসেম্বর ২০১৫), "৭০-ক্রোড় প্ল্যান ফর আইডল ইনস্টলেশন অ্যাট মাঙ্গি-টুঙ্গি", দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, নাসিক, টিএনএন, ১৯ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা, সংগ্রহের তারিখ ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
- ↑ প্রতাপাদিত্য পাল ১৯৮৬, পৃ. ২২।
- ↑ মেট মিউজিয়াম, ৬ মে ২০১৭ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা, সংগ্রহের তারিখ ১৬ এপ্রিল ২০১৭
- ↑ "ওঁ – সিগনিফিকেন্স ইন জৈনিজম, ল্যাঙ্গুয়েজেস অ্যান্ট স্ক্রিপ্টস অফ ইন্ডিয়া , কলোরাডো রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়", cs.colostate.edu
- ↑ ফন গ্লাসেনাপ ১৯২৫, পৃ. ৪১০–৪১১।
- ↑ আগরওয়াল ২০১২, পৃ. ১৩৫।
- ↑ আগরওয়াল ২০১৩, পৃ. ৮০।
- ↑ ক খ টিৎজে ১৯৯৮, পৃ. ২৩৪।
- ↑ বিজয় কে. জৈন ২০১২, পৃ. চার।
- ↑ কর্ট ২০০১এ, পৃ. ১৭।
- ↑ জান্সমা ও জৈন ২০০৬, পৃ. ১২৩।
- ↑ কর্ট ২০০১এ, পৃ. ১৭–১৮।
- ↑ রবিনসন ২০০৬, পৃ. ২২৫।
- ↑ সানগাভে ২০০১, পৃ. ১২৩।
- ↑ ভ্যালেলি ২০১৩, পৃ. ৩৫৮।
- ↑ স্যানগেভ ২০০১, পৃ. ১৮৫।
- ↑ র্যানকিন ও মারডিয়া ২০১৩, পৃ. ৯৭৫।
- ↑ ফন গ্লাসেনাপ ১৯২৫, পৃ. ১৩।
- ↑ ফন গ্লাসেনাপ ১৯২৫, পৃ. ১৬।
- ↑ লং ২০১৩, পৃ. ৫৩–৫৪।
- ↑ লকটেফোল্ড ২০০২, পৃ. ৬৩৯।
- ↑ বিলিমোরিয়া ১৯৮৮, পৃ. ১–৩০।
- ↑ জম্বুবিজয় ২০০২, পৃ. ১১৪।
- ↑ পান্ডে ১৯৫৭, পৃ. ৩৫৩।
- ↑ স্যানগেভ ২০০১, পৃ. ১০৪, ১২৯।
- ↑ সরস্বতী ১৯০৮, পৃ. ৪৪৪।
- ↑ জিমার ১৯৫৩, পৃ. ১৮৩।
- ↑ জৈনি ১৯৯৮, পৃ. ১০।
- ↑ বার্নেট ১৯৫৭, পৃ. ৭।
- ↑ ডুন্ডাস ২০০৩এ, পৃ. ৩৮৩।
- ↑ কেওন ও প্রেবিশ ২০১৩, পৃ. ১২৭–১৩০।
- ↑ স্যানগেভ ২০০১, পৃ. ১০৫।
- ↑ নিলিস ২০১০, পৃ. ৭২–৭৬।
- ↑ কিউভার্নস্টর্ম ২০০৩, পৃ. নয়–এগারো, ১৫১–১৬২।
- ↑ ফন গ্লাসেনাপ ১৯২৫, পৃ. ৪১।
- ↑ ক খ কুলকে ও রদারমান্ড ২০০৪, পৃ. ৬৩–৬৫।
- ↑ বোয়েশে ২০০৩, পৃ. ৭–১৮।
- ↑ মুখোপাধ্যায় ১৯৯৮, পৃ. ৩৯–৪৬, ২৩৪–২৩৬।
- ↑ মুখোপাধ্যায় ১৯৮৮, পৃ. ৪–২১, ২৩২–২৩৭।
- ↑ ফন গ্লাসেনাপ ১৯২৫, পৃ. ৪২।
- ↑ ফন গ্লাসেনাপ ১৯২৫, পৃ. ৪৩।
- ↑ উপিন্দর সিং ২০১৬, পৃ. ৪৪৪।
- ↑ ফন গ্লাসেনাপ ১৯২৫, পৃ. ৪৯।
- ↑ কর্ট ২০১০, পৃ. ২০২।
- ↑ নাথুভাই শাহ ২০০৪, পৃ. ৬৯–৭০।
- ↑ পেরেইরা ১৯৭৭, পৃ. ২১–২৪।
- ↑ ফন গ্লাসেনাপ ১৯২৫, পৃ. ৫২।
- ↑ লকটেফেল্ড ২০০২, পৃ. ৪০৯।
- ↑ অরুণাচলম ১৯৮১, পৃ. ১৭০।
- ↑ বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান – ইলোরা গুহাসমূহ ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ৭ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে, ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (২০১১), ভারত সরকার
- ↑ গোপাল ১৯৯০, পৃ. ১৭৮।
- ↑ ওয়েন ২০১২বি, পৃ. ১–১০।
- ↑ ফন গ্লাসেনাপ ১৯২৫, পৃ. ৫২–৫৪।
- ↑ ফন গ্লাসেনাপ ১৯২৫, পৃ. ৫৬।
- ↑ ফন গ্লাসেনাপ ১৯২৫, পৃ. ৭৫–৭৭।
- ↑ দাস ২০০৫, পৃ. ১৬১।
- ↑ কেন্দ্র, ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী। "নগরপকর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র – ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী কেন্দ্র"। whc.unesco.org (ইংরেজি ভাষায়)। ১০ মে ২০১৭ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৪ এপ্রিল ২০১৭।
- ↑ ডুন্ডাস ২০০২, পৃ. ১৪৫–১৪৬, ১২৪।
- ↑ ফন গ্লাসেনাপ ১৯২৫, পৃ. ৭৪–৭৫।
- ↑ ডুন্ডাস ২০০২, পৃ. ১৪৬।
- ↑ ডুন্ডাস ২০০২, পৃ. ২২০–২২১।
- ↑ ট্রুশকে ২০১৫, পৃ. ১৩১১–১৩৪৪।
- ↑ কর্ট ১৯৯৮, পৃ. ৮৫–৮৬।
- ↑ ট্রাইবিউন, ইন্ডিয়া। "বীরচন্দ গান্ধী – আ গান্ধী বিফোর গান্ধী অ্যান আনসাং গান্ধী হু সেট কোর্স অফ হিজ নেমসেক"। ইন্ডিয়া ট্রাইবিউন। সংগ্রহের তারিখ ১৭ আগস্ট ২০১২।
- ↑ হাওয়ার্ড, শ্রীমতী চার্লস (এপ্রিল ১৯০২)। দি ওপেন কোর্ট, খণ্ড ১৬, এনআর. ৪ "দ্য ডেথ অফ মি. বীরচন্দ আর. গান্ধী"। Chicago: দি ওপেন কোর্ট পাবলিশিং কোম্পানি।
- ↑ "লাইফ অফ শ্রীমদ্ রাজচন্দ্র"। কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগ, কলোরাডো রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়। সংগ্রহের তারিখ ৮ জানুয়ারি ২০১৭।
- ↑ স্যালটার ২০০২, পৃ. ১৩২।
- ↑ স্যালটার ২০০২, পৃ. ১৩৩।
- ↑ বাঘু এফ. কারভারি; বীরচন্দ রাঘবজী গান্ধী (১৯১১)। দ্য জৈন ফিলোজফি: কালেক্টেড অ্যান্ড এডিটেড বাই বাঘু এফ. কারবারি। এন. এম. ত্রিপাঠী অ্যান্ড কোম্পানি। পৃষ্ঠা ১১৬–১২০।
- ↑ ক খ স্যালটার ২০০২, পৃ. ১৪৫।
- ↑ পেতিত, জেরোম (২০১৬)। "রাজচন্দ্র"। জৈনপেডিয়া। সংগ্রহের তারিখ ৯ জানুয়ারি ২০১৭।
- ↑ টমাস ওয়েবার (২ ডিসেম্বর ২০০৪)। গান্ধী অ্যাজ ডিসাইপল অ্যান্ড মেন্টর
 । কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস। পৃষ্ঠা ৩৪–৩৬। আইএসবিএন 978-1-139-45657-9।
। কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস। পৃষ্ঠা ৩৪–৩৬। আইএসবিএন 978-1-139-45657-9।
- ↑ ভেরিয়াস সেন্সাস অফ ইন্ডিয়া: ১৮৭১–১৮৭২। ভারত সরকার। ১৮৬৭। পৃষ্ঠা ৩১ টীকা ১৪০।
- ↑ হপকিনস ১৯০২, পৃ. ২৮৩।
- ↑ সুনবল ১৯৩৪, পৃ. ৯১–৯৩।
- ↑ জৈনি ২০০০, পৃ. ৩৩।
- ↑ হ্যাকেট ২০০৮, পৃ. ৬৩–৬৮।
- ↑ কর্ট ২০১০, পৃ. ১২–১৬, ২০০–২০৭, ২০৮–২১৯, ২৫১ সঙ্গে টীকা ১০।
- ↑ ক খ ফ্লুগেল ২০০৬, পৃ. ৩৪৮–৩৪৯।
- ↑ নাথুভাই শাহ ২০০৪, পৃ. ৫৬।
- ↑ ফ্লুগেল ২০০৬, পৃ. ৩৫৯–৩৬০।
- ↑ ক্রিস্টোফার প্যাট্রিক মিলার; জেফরি ডি. লং; মাইকেল রিডিং (১৫ ডিসেম্বর ২০১৯)। বিকনস অফ ধর্ম: স্পিরিচুয়াল এক্সঅ্যাম্পলারস ফর দ্য মডার্ন এজ। রোওম্যান অ্যান্ড লিটলফিল্ড। পৃষ্ঠা ৭, ১০–। আইএসবিএন 978-1-4985-6485-4।
- ↑ স্যানগেভ ২০০৬, পৃ. ১৫।
- ↑ ভুর্স্ট ২০১৪, পৃ. ৯৬।
- ↑ মেল্টন ও বাউমান ২০১০, পৃ. উনষাট, ১৩৯৫।
- ↑ ক খ রেজিস্টার জেনারেল ও জনগণনা কমিশনারের কার্যালয় (২০১১), সি-১ পপুলেশন বাই রিলিজিয়াস কমিউনিটি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, ভারত সরকার, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা, সংগ্রহের তারিখ ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫
- ↑ উইলি ২০০৯, পৃ. ৪৩।
- ↑ মুগাম্বি ২০১০, পৃ. ১০৮।
- ↑ "থাউসেন্ডস অফ জাপানিজ মেকিং আ স্মুথ ট্রানজিশন ফ্রম জেন টু জৈন"। হিন্দুস্তান টাইমস। ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০।
- ↑ "দিল্লি অ্যান্ড পাঞ্জাব রিচেস্ট স্টেটস, জৈন ওয়েদিয়েস্ট কমিউনিটি: ন্যাশনাল সার্ভে"। হিন্দুস্তান টাইমস। ১৩ জানুয়ারি ২০১৮।
- ↑ জৈনস হ্যাভ হাইয়েস্ট পারসেন্টেজ অফ লিটারেটস: সেনসাস ২০১১, দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ৩১ আগস্ট ২০১৬, ২৯ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা, সংগ্রহের তারিখ ১৯ মে ২০১৭
- ↑ ভারতের জনগণনা (২০১১), ডিস্ট্রিবিউশন অফ পপুলেশন বাই রিলিজিয়নস (পিডিএফ), ভারত সরকার, ৪ মার্চ ২০১৬ তারিখে মূল (পিডিএফ) থেকে আর্কাইভ করা, সংগ্রহের তারিখ ১৯ মে ২০১৭
- ↑ রুডলফ ও রুডলফ ১৯৮৪, পৃ. ১৭১।
- ↑ জনার্দন পান্ডে ১৯৯৮, পৃ. ৫০।
- ↑ মূল উদ্ধৃতি: No religion in the World has explained the principle of Ahiṃsā so deeply and systematically as is discussed with its applicability in every human life in Jainism. As and when the benevolent principle of Ahiṃsā or non-violence will be ascribed for practice by the people of the world to achieve their end of life in this world and beyond, Jainism is sure to have the uppermost status and Mahāvīra is sure to be respected as the greatest authority on Ahiṃsā.
উল্লেখপঞ্জি
- আগরওয়াল, এম. কে. (২০১২), ফ্রম ভারত টু ইন্ডিয়া (খণ্ড ১: ক্রাইসি দ্য গোল্ডেন সংস্করণ), আইইউনিভার্স, আইএসবিএন 978-1-4759-0766-7
- আগরওয়াল, এম. কে. (২০১৩), দ্য বেদিক কোর অফ হিউম্যান হিস্ট্রি: অ্যান্ড ট্রুথ উইল বি দ্য সেভিয়র, আইইউনিভার্স, আইএসবিএন 978-1-4917-1595-6
- অ্যালবার্টস, ওয়ান্ডা (২০০৭), ইন্টিগ্রেটিভ রিলিজিয়াস এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া: আ স্টাডি-অফ-রিলিজিয়াস অ্যাপ্রোচ, ওয়াল্টার ডে গ্রুইটার, আইএসবিএন 978-3-11-097134-7
- অ্যাপেলটন, নাওমি (২০১৬), শেয়ার্ড ক্যারেকটারস ইন জৈন, বুদ্ধিস্ট অ্যান্ড হিন্দু ন্যারাটিভ: গডস, কিংস অ্যান্ড আদার হিরোজ, টেলর অ্যান্ড ফ্রান্সিস, আইএসবিএন 978-1-317-05574-7
- আরোরা, উদয় প্রকাশ (২০০৭), উদয়ন
- অরুণাচলম, এম., সম্পাদক (১৯৮১), ঐন্তাম উলকত তামিল মানাটু-কারুট্টারাণকু আয়বুক কট্টুরৈকল, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোশিয়েসন অফ তামিল রিসার্চ
- বাব, লরেন্স এ. (১৯৯৬), অ্যাবসেন্ট লর্ড: এস্থেটিকস অ্যান্ড কিংস ইন আ জৈন রিচুয়াল কালচার, ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস, আইএসবিএন 978-0-520-91708-8
- বেইলি, উইলিয়াম (২০১২), দ্য থিওলজিক্যাল ইউনিভার্স, বেইলি পাবলিশিং, পিএ, আইএসবিএন 978-1-312-23861-9
- বালসারোউকজ, পিওট্র (২০০৩), এসেজ ইন জৈন ফিলোফফি অ্যান্ড রিলিজিয়ন, মোতিলাল বনারসিদাস, আইএসবিএন 978-81-208-1977-1
- বালসারোউকজ, পিওট্র (২০০৯), জৈনিজম অ্যান্ড দ্য ডেফিনেশন অফ রিলিজিয়ন (১ম সংস্করণ), মুম্বই: হিন্দি গ্রন্থ কার্যালয়, আইএসবিএন 978-81-88769-29-2
- বালসারোউকজ, পিওট্র (২০১৫), আর্লি অ্যাসেটিজম ইন ইন্ডিয়া: আজীবিকিজম অ্যান্ড জৈনিজম, রটলেজ, আইএসবিএন 978-1-317-53853-0
- বার্নেট, লিঙ্কন (১৯৫৭), ওয়েলস, স্যাম, সম্পাদক, দ্য ওয়ার্ল্ড’স গ্রেট রিলিজিয়নস (1st সংস্করণ), নিউ ইয়র্ক: টাইম ইনকর্পোরেটেড
|display-authors=এবং অন্যান্যঅবৈধ (সাহায্য) - বার্টলি, সি. জে. (২০১৩), দ্য থিওলজি অফ রামানুজ: রিয়ালিজম অ্যান্ড রিলিজিয়ন, রটলেজ, আইএসবিএন 978-1-136-85306-7
- বার্গার, পিটার (২০১০), দি অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল ভ্যালুজ: এসেজ ইন অনরিং অফ জর্জ পেফার, India: পিয়ারসন এডুকেশন, আইএসবিএন 978-81-317-2820-8
- বিলিমোরিয়া, পি. (১৯৮৮), শব্দপ্রমাণ: ওয়ার্ড অ্যান্ড নলেজ, স্টাডিজ অফ ক্ল্যাসিকাল ইন্ডিয়া, ১০, স্প্রিংগার, আইএসবিএন 978-94-010-7810-8
- বোয়েশে, রজার (২০০৩), দ্য ফার্স্ট গ্রেট পলিটিক্যাল রিয়ালিস্ট: কৌটিল্য অ্যান্ড হিজ অর্থশাস্ত্র, লেক্সিংটন বুকস, আইএসবিএন 978-0-7391-0607-5
- বুটালিয়া, তরুণজিৎ সিং; স্মল, ডায়ন পি., সম্পাদকগণ (২০০৪), রিলিজিয়ন ইন ওহিও: প্রোফাইলস অফ ফেইথ কমিউনিটিজ, ওহিও ইউনিভার্সিটি প্রেস, আইএসবিএন 978-0-8214-1551-1
- কালিয়াট, কোলেট (২০০৩এ), গ্লিনিংস ফ্রম আ কমপেয়ার্যাটিভ স্টাডি অফ আর্লি ক্যাননিক্যাল বুদ্ধিস্ট অ্যান্ড জৈন টেক্সটস, ২৬ (১), জার্নাল অফ দি ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোশিয়েশন অফ অফ বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ এখানে তারিখের মান পরীক্ষা করুন:
|তারিখ=(সাহায্য) - চম্পৎ রাই জৈন (১৯১৭), দ্য প্র্যাকটিক্যাল পাথ, দ্য সেন্ট্রাল জৈন পাবলিশিং হাউজ
- চরিত্রপ্রজ্ঞা, সমানি (২০০৪), শেঠিয়া, তারা, সম্পাদক, অহিংসা, অনেকান্ত, অ্যান্ড জৈনিজম, মোতিলাল বনারসিদাস, আইএসবিএন 978-81-208-2036-4
- চট্টোপাধ্যায়, অসীম কুমার (২০০০), আ কমপ্রিহেনসিভ হিস্ট্রি অফ জৈনিজম: ফ্রম দি আর্লিয়েস্ট বিগিনিংস টু এডি ১০০০, মুন্সিরাম মনোহরলাল, আইএসবিএন 978-81-215-0931-2
- ক্লার্ক, পিটার; বেয়ার, পিটার (২০০৯), দ্য ওয়ার্ল্ড’স রিলিজিয়নস: কমিউনিটিজ অ্যান্ড ট্রান্সফর্মেশনস, রটলেজ, আইএসবিএন 978-0-203-87212-3
- কর্ট, জন ই. (১৯৮৭), "মিডিয়াভাল জৈন গডেস ট্র্যাডিশন", নুমেন, ৩৪ (২): ২৩৫–২৫৫, ডিওআই:10.1163/156852787x00047
- কর্ট, জন ই. (১৯৯৫), "দ্য জৈন নলেজ ওয়্যারহাউসেজ: ট্র্যাডিশনাল লাইব্রেরিজ ইন ইন্ডিয়া", জার্নাল অফ দি আমেরিকান ওরিয়েন্টাল সোসাইটি, ১১৫ (১): ৭৭–৮৭, জেস্টোর 605310, ডিওআই:10.2307/605310
- কর্ট, জন ই., সম্পাদক (১৯৯৮), ওপেন বাউন্ডারিজ: জৈন কমিউনিটিজ অ্যান্ড কালচারাল ইন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি, সানি প্রেস, আইএসবিএন 978-0-7914-3785-8
- কর্ট, জন ই. (২০০১a), জৈনস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড: রিলিজিয়াস ভ্যালুজ অ্যান্ড আইডিওলজি ইন ইন্ডিয়া, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, আইএসবিএন 978-0-19-513234-2
- কর্ট, জন ই. (২০০১বি), হোয়াইট, ডেভিড গর্ডন, সম্পাদক, তন্ত্র ইন প্র্যাকটিস, মোতিলাল বনারসিদাস, আইএসবিএন 978-81-208-1778-4 এখানে তারিখের মান পরীক্ষা করুন:
|তারিখ=(সাহায্য) - কর্ট, জন ই. (২০১০), ফ্রেমিং দ্য জিনাস: ন্যারেটিভস অফ আইকনস অ্যান্ড আইডলস ইন জৈন হিস্ট্রি, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, আইএসবিএন 978-0-19-538502-1
- দালাল, রোশেন (২০১০এ) [2006], দ্য রিলিজিয়নস অফ ইন্ডিয়া: আ কনসাইস গাইড টু নাইন মেজর ফেইথস, পেঙ্গুইন বুকস, আইএসবিএন 978-0-14-341517-6 এখানে তারিখের মান পরীক্ষা করুন:
|তারিখ=(সাহায্য) - দালাল, রোশেন (২০১০বি), হিন্দুইজম: অ্যান অ্যালফাবেটিক্যাল গাইড, পেঙ্গুইন বুকস, আইএসবিএন 978-0-14-341421-6 এখানে তারিখের মান পরীক্ষা করুন:
|তারিখ=(সাহায্য) - দাশ, শিশির কুমার (২০০৫), আ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান লিটারেচার, ৫০০–১৩৯৯: ফ্রম কোর্টলি টু দ্য পপুলার, সাহিত্য অকাদেমি, আইএসবিএন 978-81-260-2171-0
- ডনিগার, ওয়েন্ডি, সম্পাদক (১৯৯৯), এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়নস, মেরিয়াম-ওয়েবস্টার, আইএসবিএন 978-0-87779-044-0
- ডুন্ডাস, পল (২০০২) [1992], দ্য জৈনস (২য় সংস্করণ), লন্ডন ও নিউ ইয়র্ক: রটলেজ, আইএসবিএন 978-0-415-26605-5
- ডুন্ডাস, পল (২০০৩এ), "জৈনিজম অ্যান্ড বুদ্ধিজম", বাসওয়েল, রবার্ট ই., এনসাইক্লোপেডিয়া অফ বুদ্ধিজম, নিউ ইয়র্ক: ম্যাকমিলান রেফারেন্স লাইব্রেরি, আইএসবিএন 978-0-02-865718-9 এখানে তারিখের মান পরীক্ষা করুন:
|তারিখ=(সাহায্য) - ডুন্ডাস, পল (২০০৬), অলিভেল এ., প্যাট্রিক, সম্পাদক, বিটুইন দি এম্পায়ারস: সোসাইটি ইন ইন্ডিয়া ৩০০ বিসিই টু ৪০০ সিই, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, আইএসবিএন 978-0-19-977507-1
- ফার্গুসন, জেমস (১৮৭৬), আ হিস্ট্রি অফ আর্কিটেকচার ইন অল কান্ট্রিজ: ফ্রম দি আর্লিয়েস্ট টাইমস টু দ্য প্রেজেন্ট ডেজ, ৩, জন মারি
- ফিনেগান, জ্যাক (১৯৮৯), অ্যান আর্কিওলজিক্যাল হিস্ট্রি অফ রিলিজিয়নস অফ ইন্ডিয়ান এশিয়া, প্যারাগন হাউজ, আইএসবিএন 978-0-913729-43-4
- ফ্লোরিডা, রবার্ট ই. (২০০৫), হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড’স মেজর রিলিজিয়নস: দ্য বুদ্ধিস্ট ট্র্যাডিশনস, এবিসি-ক্লিও, আইএসবিএন 978-0-313-31318-9
- ফ্লুগেল, পিটার (২০০২), "তেরাপন্থ শ্বেতাম্বর জৈন ট্র্যাডিশন", মেল্টন, জে. জি.; বাউম্যান, জি., রিলিজিয়নস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড: আ কমপ্রিহেনসিভ এনসাইক্লোপিডিয়া অফ বিলিফস অ্যান্ড প্র্যাকটিশেস, এবিসি-ক্লিও, আইএসবিএন 978-1-57607-223-3
- ফ্লুগেল, পিটার (২০০৫), কিং, আনা এস.; ব্রোকিংটন, জৈন, সম্পাদকগণ, "প্রেজেন্ট লর্ড: সীমান্ধর স্বামী অ্যান্ড দি অক্রম বিজ্ঞান মুভমেন্ট" (পিডিএফ), দি ইন্টিমেন্ট আদার: লভ ডিভাইন ইন দি ইন্ডিক রিলিজিয়নস, নতুন দিল্লি: ওরিয়েন্ট লংম্যান, আইএসবিএন 978-81-250-2801-7
- ফ্লুগেল, পিটার (২০০৬), স্টাডিজ ইন জৈন হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার: ডিসপিউটস অ্যান্ড ডায়ালগস, রটলেজ, আইএসবিএন 978-1-134-23552-0
- ফোর, শেরি (২০১৫), জৈনিজম: আ গাইড ফর দ্য পারপ্লেক্সড, ব্লুমসবেরি পাবলিশিং, আইএসবিএন 978-1-4742-2756-8
- ফোর, শেরি (২০১৫), জৈনিজম: আ গাইড ফর ফ্য পারপ্লেক্সড, ব্লুমসবেরি অ্যাকাডেমিক, আইএসবিএন 978-1-4742-2755-1
- গোমব্রিক, রিচার্ড (২০১২), বুদ্ধিস্ট প্রিসেপ্ট অ্যান্ড প্র্যাকটিশ, রটলেজ, আইএসবিএন 978-1-136-15623-6
- গোপাল, মদন (১৯৯০), গৌতম, কে. এস., সম্পাদক, ইন্ডিয়া থ্রু দি এজেস, প্রকাশনা বিভাগ, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক, ভারত সরকার
- গঘ, এলান (২০১২), শেডস অফ এনলাইটেনমেন্ট: আ জৈন তান্ত্রিক ডায়াগ্রাম অ্যান্ড দ্য কালার্স অফ দ্য তীর্থংকরস, ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ জৈন স্টাডিজ, ৮ (১)
- গ্র্যানোফ, ফিলিস (১৯৯২), "দ্য ভায়োলেন্স অফ নন-ভায়োলেন্স: আ স্টাডি অফ সাম জৈন রেসপন্সেস টু নন-জৈন রিলিজিয়াস প্র্যাকটিসেস", দ্য জার্নাল অফ দি ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোশিয়েশন অফ বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ, ১৫ (১)
- গ্রিমস, জন (১৯৯৬), আ কনসাইস ডিকশনারি অফ ইন্ডিয়ান ফিলোজফি: সংস্কৃত টার্মস ডিফাইন্ড ইন ইংলিশ, New York: সানি প্রেস, আইএসবিএন 0-7914-3068-5
- হ্যাকেট, রোজালিন্ড আই. জে. (২০০৮), প্রসেলিটাইজেশন রিভিজিটেড: রাইটস টক, ফ্রি মার্কেটস অ্যান্ড কালচার ওয়ার্স, ইকুইনক্স অ্যাকাডেমিকস, আইএসবিএন 978-1-84553-227-7
- হার্ভে, গ্রাহাম (২০১৬), রিলিজিয়নস ইন ফোকাস: নিউ অ্যাপ্রোচেস টু ট্র্যাডিশনস অ্যান্ড কনটেম্পোরারি প্র্যাকটিশেস, রটলেজ, আইএসবিএন 978-1-134-93690-8
- জেকবি, হার্মান (১৯৬৪), ম্যাক্সকুমার (সি সেক্রেড বুকস অফ দি ইস্ট সিরিজ, দ্বাবিংশ খণ্ড), সম্পাদক, জৈন সূত্রজ (অনুবাদ), মোতিলাল বনারসিদাস (আদি প্রকাশক: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস)
- হিরাকাওয়া, আকিরা (১৯৯৩), আ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান বুদ্ধিজম: ফ্রম শাক্যমুণি টু আর্লি মহাযান, মোতিলাল বনারসিদাস, আইএসবিএন 978-81-208-0955-0
- হিরিয়ান্না, এম. (১৯৯৩), আউটলাইনস অফ ইন্ডিয়ান ফিলোজফি, মোতিলাল বনারসিদাস, আইএসবিএন 978-81-208-1086-0
- হপকিনস, এডওয়ার্ড ওয়াশবার্ন (১৯০২), দ্য রিলিজিয়নস অফ ইন্ডিয়া, জিন অ্যান্ড কোম্পানি
- ইজাওয়া, এ. (২০০৮), এমপ্যাথি ফর পেইন ইন বেদিক রিচুয়াল, ১২, জার্নাল অফ দি ইন্টারন্যাশনাল কলেজ ফর অ্যাডভান্সড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ, কোকুসাই বুককযোগকু দইগকুইন দাইগাকু
- জৈন, চম্পৎ রাই (১৯২৯), দ্য প্র্যাকটিক্যাল ধর্ম, দি ইন্ডিয়ান প্রেস,
 এই উৎস থেকে এই নিবন্ধে লেখা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা পাবলিক ডোমেইনে রয়েছে।
এই উৎস থেকে এই নিবন্ধে লেখা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা পাবলিক ডোমেইনে রয়েছে। - জৈন, জ্যোতীন্দ্র; ফিশার, এবারহার্ড (১৯৭৮), জৈন আইকনোগ্রাফি, ১২, ব্রিল, আইএসবিএন 978-90-04-05259-8
- জৈন, কৈলাশ চন্দ (১৯৯১), লর্ড মহাবীর অ্যান্ড হিজ টাইমস, মোতিলাল বনারসিদাস, আইএসবিএন 978-81-208-0805-8
- জৈন, এস. এ. (১৯৯২) [১ম সংস্করণ ১৯৬০], রিয়ালিটি (শ্রীমৎ পূজ্যপাদাচার্যের সর্বার্থসিদ্ধির ইংরেজি অনুবাদ) (২য় সংস্করণ), জ্বালামালিনী ট্রাস্ট,
 এই উৎস থেকে এই নিবন্ধে লেখা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা পাবলিক ডোমেইনে রয়েছে।
এই উৎস থেকে এই নিবন্ধে লেখা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা পাবলিক ডোমেইনে রয়েছে। - জৈন, শান্তি লাল (১৯৯৮), এবিসি অফ জৈনিজম, জ্ঞানোদয় বিদ্যাপীঠ, আইএসবিএন 978-81-7628-000-6
- জৈন, বিজয় কে. (২০১১), আচার্য উমাস্বামী’জ তত্ত্বার্থসূত্র (1st সংস্করণ), বিকল্প প্রিন্টার্স, আইএসবিএন 978-81-903639-2-1,
 এই উৎস থেকে এই নিবন্ধে লেখা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা পাবলিক ডোমেইনে রয়েছে।
এই উৎস থেকে এই নিবন্ধে লেখা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা পাবলিক ডোমেইনে রয়েছে। - জৈন, বিজয় কে. (২০১২), আচার্য অমৃতচন্দ্র’জ পুরুষার্থ সিদ্ধ্যুপায়: রিয়েলাইজেশন অফ দ্য পিয়র সেলফ, উইথ হিন্দি অ্যান্ড ইংলিশ ট্রান্সলেশন, বিকল্প প্রিন্টার্স, আইএসবিএন 978-81-903639-4-5,
 এই উৎস থেকে এই নিবন্ধে লেখা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা পাবলিক ডোমেইনে রয়েছে।
এই উৎস থেকে এই নিবন্ধে লেখা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা পাবলিক ডোমেইনে রয়েছে। - জৈন, বিজয় কে. (২০১৩), আচার্য অমৃতচন্দ্র’জ দ্রব্যসংগ্রহ, বিকল্প প্রিন্টার্স, আইএসবিএন 978-81-903639-5-2,
 এই উৎস থেকে এই নিবন্ধে লেখা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা পাবলিক ডোমেইনে রয়েছে।
এই উৎস থেকে এই নিবন্ধে লেখা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা পাবলিক ডোমেইনে রয়েছে। - জৈন, বিজয় কে. (২০১৬), আচার্য সামন্তভদ্র’জ রত্নকরন্দক-শ্রাবকাচার: দ্য জুয়েল-ক্যাসকেট অফ হাউজহোল্ডার’স কনডাক্ট, বিকল্প প্রিন্টার্স, আইএসবিএন 978-81-903639-9-0,
 এই উৎস থেকে এই নিবন্ধে লেখা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা পাবলিক ডোমেইনে রয়েছে।
এই উৎস থেকে এই নিবন্ধে লেখা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা পাবলিক ডোমেইনে রয়েছে। - জৈনি, পদ্মনাভ (১৯৮০), ডনিগার, ওয়েন্ডি, সম্পাদক, কর্ম অ্যান্ড রিবার্থ ইন ক্ল্যাসিক্যাল ইন্ডিয়ান ট্র্যাডিশনস, ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস, আইএসবিএন 978-0-520-03923-0
- Jaini, Padmanabh S. (১৯৯১), Gender and Salvation: Jaina Debates on the Spiritual Liberation of Women, University of California Press, আইএসবিএন 978-0-520-06820-9
- জৈনি, পদ্মনাভ এস. (১৯৯৮) [1979], দ্য জৈন পাথ অফ পিউরিফিকেশন, Delhi: মোতিলাল বনারসিদাস, আইএসবিএন 978-81-208-1578-0
- জৈনি, পদ্মনাভ এস., সম্পাদক (২০০০), কালেক্টেড পেপারস অন জৈন স্টাডিজ (১ম সংস্করণ), দিল্লি: মোতিলাল বনারসিদাস, আইএসবিএন 978-81-208-1691-6
- জম্বুবিজয়, মুনি (২০০২), পিয়ত্র বালসারোউইকজ ও মারেক মেজর, সম্পাদক, এসেজ ইন জৈন ফিলোজফি অ্যান্ড রিলিজিয়ন, মোতিলাল বনারসিদাস, আইএসবিএন 978-81-208-1977-1
- জান্সমা, রুডি; জৈন, স্নেহ রানি (২০০৬), ইন্ট্রোডাকশন টু জৈনিজম, জয়পুর: প্রাকৃত ভারতী অ্যাকাডেমি, আইএসবিএন 978-81-89698-09-6
- জনসন, ডব্লিউ. জে. (১৯৯৫), হার্মলেস সোলস: কার্মিক বন্ডেজ অ্যান্ড রিলিজিয়াস চেঞ্জ ইন আর্লি জৈনিজম উইথ স্পেশাল রেফারেন্স টু উমাস্বাতী অ্যান্ড কুন্দকুন্দ, মোতিলাল বনারসিদাস, আইএসবিএন 978-81-208-1309-0
- জনস্টন, উইলিয়াম এম. (২০০০), এনসাইক্লোপিডিয়া অফ মনাস্টিসিজিম: এ–এল, রটলেজ, আইএসবিএন 978-1-57958-090-2
- জোনস, কনস্ট্যান্স; রায়ান, জেমস ডি. (২০০৭), এনসাইক্লোপিডিয়া অফ হিন্দুইজম, ইনফোবেস পাবলিশিং, আইএসবিএন 978-0-8160-5458-9
- জোনস, লিন্ডসে (২০০৫), এনসাইক্লোপিডিয়া অফ রিলিজিয়ন, ম্যাকমিলান রেফারেন্স, আইএসবিএন 978-0-02-865733-2
- জুয়েরগেনসমেয়ার, মার্ক (২০১১), দি অক্সফোর্ড হ্যান্ডবুক অফ গ্লোবাল রিলিজিয়ন, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, আইএসবিএন 978-0-19-976764-9
- কেল্টিং, এম. হুইটনি (২০০৯), হিরোইক ওয়াভস রিচুয়ালস, স্টোরিজ অ্যান্ড দ্য ভার্চুজ অফ জৈন ওয়াইফহুড, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, আইএসবিএন 978-0-19-973679-9
- কেওন, দামিয়েন; প্রেবিশ, চার্লস এস. (২০১৩), এনসাইক্লোপিডিয়া অফ বুদ্ধিজম, রটলেজ, আইএসবিএন 978-1-136-98588-1
- রিং, ট্রুডি; ওয়াটসন, নোয়েল; শেলিংগার, পল, সম্পাদকগণ (১৯৯৬), এশিয়া অ্যান্ড ওশিয়ানিয়া: ইন্টারন্যাশনাল ডিকশনারি অফ হিস্টোরিক প্লেসেস, রটলেজ, আইএসবিএন 978-1-884964-04-6
- কিশোর, কণিকা (১৬ জুন ২০১৫), "সিম্বল অ্যান্ড ইমেজ ওয়ারশিপ ইন জৈনিজম", ইন্ডিয়ান হিস্টোরিক্যাল রিভিউ (ইংরেজি ভাষায়), ৪২ (১): ১৭–৪৩, এসটুসিআইডি 151841865, ডিওআই:10.1177/0376983615569814
- কুলকে, হারমান; রদারমান্ড, ডায়েটমার (২০০৪), আ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া, রটলেজ, আইএসবিএন 978-0-415-32920-0
- কুমার, সহদেব (২০০১), আ থাউজ্যান্ড পেটালড লোটাস: জৈন টেম্পলস অফ রাজস্থান: আর্কিটেকচার অ্যান্ড আইকনোগ্রাফি, অভিনব পাবলিকেশনস, আইএসবিএন 978-81-7017-348-9
- লকটেফেল্ড, জেমস জি. (২০০২), দি ইলাস্ট্রেটেড এনসাইক্লোপিডিয়া অফ হিন্দুইজম: এ–এম, ১, দ্য রসেন পাবলিশিং গ্রুপ, আইএসবিএন 978-0-8239-3179-8
- লকটেফেল্ড, জেমস জি. (২০০২), দি ইলাস্ট্রেটেড এনসাইক্লোপিডিয়া অফ হিন্দুইজম: এন–জেড, ২, দ্য রসেন পাবলিশিং গ্রুপ, আইএসবিএন 978-0-8239-2287-1
- লং, জেফরি ডি. (২০০৯), জৈনিজম: অ্যান ইন্ট্রোডাকশন, আই. বি. টরিস, আইএসবিএন 978-0-85773-656-7
- লং, জেফরি ডি. (২০১৩), জৈনিজম: অ্যান ইন্ট্রোডাকশন, আই. বি. টরিস, আইএসবিএন 978-0-85771-392-6
- লরেনজেন, ডেভিড এন. (১৯৭৮), "ওয়ারিয়র এসেটিকস ইন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি", জার্নাল অফ দি আমেরিকান ওরিয়েন্টাল সোসাইটি, ৯৮ (১): ৬১–৭৫, জেস্টোর 600151, ডিওআই:10.2307/600151
- মার্কহ্যাম, ইয়ান এস.; লোর, ক্রিস্টি (২০০৯), আ ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়নস রিডার, জন উইলি অ্যান্ড সনস, আইএসবিএন 978-1-4051-7109-0
- মতিলাল, বিমল কৃষ্ণ (১৯৯০), লজিক, ল্যাংগুয়েজ অ্যান্ড রিয়েলিটি: ইন্ডিয়ান ফিলোজফি অ্যান্ড কনটেম্পোরারি ইস্যুজ, মোতিলাল বনারসিদাস, আইএসবিএন 978-81-208-0717-4
- মতিলাল, বিমল কৃষ্ণ (১৯৯৮), গনেরি, জোনার্ডন; তিওয়ারি, হিরামন, সম্পাদকগণ, দ্য ক্যারেক্টার অফ লজিক ইন ইন্ডিয়া, স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ইয়র্ক প্রেস, আইএসবিএন 978-0-7914-3739-1
- ম্যাকফাউল, টমাস আর. (২০০৬), দ্য ফিউচার অফ পিস অ্যান্ড জাস্টিস ইন দ্য গ্লোবাল ভিলেজ: দ্য রোল অফ দ্য ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়নস ইন দ্য টোয়েন্টি-ফার্স্ট সেঞ্চুরি, গ্রিনউড পাবলিশিং, আইএসবিএন 978-0-275-99313-9
- মেল্টন, জে. গর্ডন, সম্পাদক (২০১১), রিলিজিয়াস সেলিব্রেশনস: অ্যান এনসাইক্লোপিডিয়া অফ হলিডেজ, ফেস্টিভ্যালস, সলেম অবজার্ভেন্স, অ্যান্ড স্পিরিচুয়াল কোমেমোরেশন, ১, এবিসি-ক্লিও, আইএসবিএন 978-1-59884-206-7
- মেল্টন, জে. গর্ডন; বাউমান, মার্টিন, সম্পাদকগণ (২০১০), রিলিজিয়নস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড: আ কমপ্রিহেনসিভ এনসাইক্লোপিডিয়া অফ বিলিফস অ্যান্ড প্র্যাকটিশেস, এক: এ–বি (২য় সংস্করণ), এবিসি-ক্লিও, আইএসবিএন 978-1-59884-204-3
- মিশেল, জর্জ আই (২০১৪), টেম্পল আর্কিটেকচার অ্যান্ড আর্ট অফ দি আর্লি চালুক্যজ: বাদামি, মহাকূট, আইহোল, পাট্টাডাকাল, নিয়োগি বুকস, আইএসবিএন 978-93-83098-33-0
- মিশ্র, সুসান বর্মা; রায়, হিমাংশু প্রভা (২০১৬), দি আর্কিওলজি অফ সেক্রেড স্পেসেজ: দ্য টেম্পলস ইন ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়ান, ২এন্ড সেঞ্চুরি বিসিই–৮থ সেঞ্চুরি সিই, রটলেজ, আইএসবিএন 978-1-317-19374-6
- মুখোপাধ্যায়, রাধাকুমুদ (১৯৮৮) [first published in 1966], চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য অ্যান্ড হিজ টাইমস (৪র্থ সংস্করণ), মোতিলাল বনারসিদাস, আইএসবিএন 978-81-208-0433-3
- মুগাম্বি, জে. এন. কে., সম্পাদক (২০১০) [1990], আ কমপেয়ারেটিভ স্টাডি অফ রিলিজিয়নস (২য় সংস্করণ), ইউনিভার্সিটি অফ নাইরোবি প্রেস, আইএসবিএন 978-9966-846-89-1
- নায়ানার (২০০৫), গাথা ১.২৯
- নিলিস, জেসন (২০১০), আর্লি বুদ্ধিস্ট ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ট্রেড নেটওয়ার্কস: মোবিলিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ উইথইন অ্যান্ড বিয়ন্ড দ্য নর্থওয়েস্টার্ন বর্ডারল্যান্ডস অফ সাউথ এশিয়া, ব্রিল অ্যাকাডেমিক, আইএসবিএন 978-90-04-18159-5
- নেমিচন্দ্র, আচার্য; বলবীর, নলিনী (২০১০), দ্রব্যসংগ্রহ: এক্সপোজিশন অফ দ্য সিক্স সাবস্টেন্সেস, (প্রাকৃত ও সংস্কৃত) পণ্ডিত নাথুরাম প্রেমী রিসার্চ সিরিজ (খণ্ড ১৯), মুম্বই: হিন্দি গ্রন্থ কার্যালয়, আইএসবিএন 978-81-88769-30-8
- নেসফিল্ড, জন কলিনসন (১৮৮৫), ব্রিফ ভিউ অফ দ্য কাস্ট সিস্টেম অফ দ্য নর্থ-ওয়েস্টার্ন প্রভিন্সেস অ্যান্ড অবধ, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অবধ সরকার প্রেস
- ওলসন, কার্ল (২০১৪), "দ্য কনফ্লিক্টিং থিমস অফ ননভায়োলেন্স অ্যান্ড ভায়োলেন্স ইন এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়ান এসেটিজম অ্যাজ এভিডেন্ট ইন দ্য প্র্যাকটিশ অফ ফাস্টিং", ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ ধর্ম স্টাডিজ, ১ (২): ১, ডিওআই:10.1186/2196-8802-2-1

- ওয়েন, লিসা (২০১২এ), কার্ভিং ডিভোশন ইন দ্য জৈন কেভস অ্যাট ইলোরা, ব্রিল, আইএসবিএন 978-90-04-20629-8 এখানে তারিখের মান পরীক্ষা করুন:
|তারিখ=(সাহায্য) - ওয়েন, লিসা (২০১২বি), কার্ভিং ডিভোশন অফ দ্য জৈন কেভস অ্যাট ইলোরা, ব্রিল Academic, আইএসবিএন 978-90-04-20629-8 এখানে তারিখের মান পরীক্ষা করুন:
|তারিখ=(সাহায্য) - পাল, প্রতাপাদিত্য (১৯৮৬), ইন্ডিয়ান স্কাল্পচার: সিরকা ৫০০ বি.সি.–এ.ডি. ৭০০, 1, লস এঞ্জেলেস কান্ট্রি মিউজিয়াম অফ আর্ট, ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস, আইএসবিএন 978-0-87587-129-5
- পান্ডে, গোবিন্দ (১৯৫৭), স্টাডিজ ইন দি অরিজিনস অফ বুদ্ধিজম, মোতিলাল বনারসিদাস (পুনর্মুদ্রণ: ১৯৯৫), আইএসবিএন 978-81-208-1016-7
- পাণ্ডে, জনার্দন (১৯৯৮), গান্ধী অ্যান্ড ২১র্স্ট সেঞ্চুরি, আইএসবিএন 978-81-7022-672-7
- পাণ্ড্য, প্রশান্ত এইচ. (২০১৪), ইন্ডিয়ান ফিলাটেলি ডাইজেস্ট
- পেশিলিস, কারেন; রাজ, সেলভা জে., সম্পাদকগণ (২০১৩), সাউথ এশিয়ান রিলিজিয়নস: ট্র্যাডিশনস অ্যান্ড টুডে, রটলেজ, আইএসবিএন 978-0-203-07993-5
- পেরেইয়া, জোস (১৯৭৭), মনোলিথিক জিনাস, মোতিলাল বনারসিদাস, আইএসবিএন 978-81-208-2397-6
- পেরেট, রয় ডব্লিউ. (২০১৩), ফিলোজফি অফ রিলিজিয়ন: ইন্ডিয়ান ফিলোজফি, রটলেজ, আইএসবিএন 978-1-135-70322-6
- পোপ, জর্জ উগ্লো (১৮৮০), আ টেক্সট-বুক অফ ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি, ডব্লিউ. এইচ. অ্যালেন অ্যান্ড কোম্পানি
- প্রাইস, জোয়ান (২০১০), সেক্রেড স্ক্রিপচার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়ন: অ্যান ইন্ট্রোডাকশন, ব্লুমসবেরি অ্যাকাডেমিকস, আইএসবিএন 978-0-8264-2354-2
- কিউভার্রস্টর্ম, ওলি, সম্পাদক (২০০৩), জৈনিজম অ্যান্ড আর্লি বুদ্ধিজম: এসেজ ইন অনর অফ পদ্মনাভ এস. জৈনি, জৈন পাবলিশিং কোম্পানি, আইএসবিএন 978-0-89581-956-7
- র্যানকিং, আইড্যান ডি.; মারদিয়া, কান্তিলাল (২০১৩), লিভিং জৈনিজম: অ্যান এথিক্যাল সায়েন্স, জন হান্ট পাবলিশিং, আইএসবিএন 978-1-78099-911-1
- রবিনসন, টমাস আর্থার (২০০৬), ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়নস, হিমস এনশিয়েন্ট অ্যান্ড মডার্ন লিমিটেড, আইএসবিএন 978-0-334-04014-9
- রুডলফ, লয়েড আই.; রুডলফ, সুসান হোয়েবার (১৯৮৪), দ্য মডার্নিটি অফ ট্র্যাডিশন: পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট ইন ইন্ডিয়া, ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগো প্রেস, আইএসবিএন 978-0-226-73137-7
- সল্টার, এমা (সেপ্টেম্বর ২০০২)। রাজ ভক্ত মার্গ: দ্য পাথ অফ ডিভোশন টু শ্রীমদ রাজচন্দ্র। আ জৈন কমিউনিটি অফ দ্য টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি (Doctoral thesis)। ইউনিভার্সিটি অফ ওয়েলস। পৃষ্ঠা ১২৫–১৫০। সংগ্রহের তারিখ ২০১৮-০৯-২১ – ইউনিভার্সিটি অফ হাডারসফিল্ড রেপোসিটরি-এর মাধ্যমে।
- সালভাডোরি, সিন্থিয়া (১৯৮৯), থ্রু ওপেন ডোরস, কেনওয়ে, আইএসবিএন 978-9966-848-05-5
- সাংগাভে, বিলাস আদিনাথ (১৯৮০), জৈন কমিউনিটি: আ সোশ্যাল সার্ভে (২য় সংস্করণ), বোম্বে: পপুলার প্রকাশন, আইএসবিএন 978-0-317-12346-3
- সাংগাভে, বিলাস আদিনাথ (২০০১), ফ্যাসেটস অফ জৈনোলজি: সিলেক্টেড রিসার্চ পেপার্স অন জৈন সোসাইটি, রিলিজিয়ন, অ্যান্ড কালচার, মুম্বই: পপুলার প্রকাশন, আইএসবিএন 978-81-7154-839-2
- সাংগাভে, বিলাস আদিনাথ (২০০৬) [1990], অ্যাসপেক্টস অফ জৈন রিলিজিয়ন (৫ সংস্করণ), ভারতীয় জ্ঞানপীঠ, আইএসবিএন 978-81-263-1273-3
- সরস্বতী, দয়ানন্দ (১৯০৮), অ্যান ইংলিশ ট্র্যানসলেশন অফ সত্যার্থ প্রকাশ (১৯৭০ সালে পুনর্মুদ্রিত), লাহোর : বীরগণান্দ প্রেস
- শেঠিয়া, তারা (২০০৪), অহিংসা, অনেকান্ত অ্যান্ড জৈনিজম, মোতিলাল বনারসিদাস, আইএসবিএন 978-81-208-2036-4
- সেট্টার, এস. (১৯৮৯), ঈশ্বরন, কে., সম্পাদক, ইনভাইটিং ডেথ: ইন্ডিয়ান অ্যাটিচিউড টুওয়ার্ডস রিচুয়াল ডেথ, ই. জে. ব্রিল, আইএসবিএন 90-04-08790-7
- সিং, রাম ভূষণ প্রসাদ (২০০৮) [1975], জৈনিজম ইন আর্লি মিডিয়াভাল কর্ণাটক, মোতিলাল বনারসিদাস, আইএসবিএন 978-81-208-3323-4
- সিং, উপিন্দর (২০১৬), আ হিস্ট্রি অফ এনশিয়েন্ট অ্যান্ড আর্লি মিডিয়াভাল ইন্ডিয়া: ফ্রম দ্য স্টোন এজ টু দ্য ১২থ সেঞ্চুরি, পিয়ারসন এডুকেশন, আইএসবিএন 978-93-325-6996-6
- শাহ, নাথুভাই (১৯৯৮), জৈনিজম: দ্য ওয়ার্ল্ড অফ কনকারার্স, ২, সাসেক্স অ্যাকাডেমিক প্রেস, আইএসবিএন 978-1-898723-31-8
- শাহ, নাথুভাই (২০০৪) [১৯৯৮ সালে প্রথম প্রকাশিত], জৈনিজম: দ্য ওয়ার্ল্ড অফ কনকারার্স, এক, মোতিলাল বনারসিদাস, আইএসবিএন 978-81-208-1938-2
- শাহ, উমাকান্ত প্রেমানন্দ (১৯৮৭), জৈন-রূপ-মণ্ডন: জৈন আইকনোগ্রাফি, অভিনব পাবলিকেশনস, আইএসবিএন 978-81-7017-208-6
- শর্মা, রমেশ চন্দ্র; ঘোষাল, প্রণতি (২০০৬), জৈন কনট্রিবিউশন টু বারাণসী, জ্ঞানপ্রবাহ, আইএসবিএন 978-81-246-0341-3
- শ, জেফরি এম.; ডেমি, টিমোথি জে. (২০১৭), ওয়ার অ্যান্ড রিলিজিয়ন: অ্যান এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ফেইথ অ্যান্ড কনফ্লিক্ট, এবিসি-ক্লিও, আইএসবিএন 978-1-61069-517-6
- সিনহা, যদুনাথ (১৯৪৪), ইন্ডিয়ান সাইকোলজি
- সলোমন, রবার্ট সি.; হিগিনস, ক্যাথলিন এম. (১৯৯৮), আ প্যাশন ফর উইসডম: আ ভেরি ব্রিফ হিস্ট্রি অফ ফিলোজফি, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, আইএসবিএন 978-0-19-511209-2
- সোনি, জয়ন্দ্র (২০০০), "বেসিক জৈন এপিস্টেমোলজি", ফিলোজফি ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট, ৫০ (৩): ৩৬৭–৩৭৭, জেস্টোর 1400179
- সুনবল, এ. জে. (১৯৩৪), আদর্শ সাধু: অ্যান আইডিয়াল মংক, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, আইএসবিএন 978-1-001-40429-5
- সুন্দররাজন, কে. আর.; মুখোপাধ্যায়, বীথিকা, সম্পাদকগণ (১৯৯৭), "২০", হিন্দু স্পিরিচুয়ালিটি: পোস্টক্ল্যাসিকাল অ্যান্ড মডার্ন, মোতিলাল বনারসিদাস, আইএসবিএন 978-81-208-1937-5
- শোয়ার্ৎজ, উইলিয়াম অ্যান্ড্রিউ (২০১৮), দ্য মেটাফিজিক্স অফ প্যারাডক্স: জৈনিজম, অ্যাবসোলিউট রিলেটিভিটি, অ্যান্ড রিলিজিয়াস প্লুরালিজম, লেক্সিংটন বুকস, আইএসবিএন 978-1-4985-6392-5, ২৪ আগস্ট ২০১৮ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা, সংগ্রহের তারিখ ২৩ আগস্ট ২০১৮
- টেলর, ব্রোন (২০০৮), এনসাইক্লোপিডিয়া অফ রিলিজিয়ন অ্যান্ড নেচার, ব্লুমসবেরি অ্যাকাডেমিক, আইএসবিএন 978-1-4411-2278-0
- টিৎজে, কার্ট (১৯৯৮), জৈনিজম: আ পিক্টোরিয়াল গাইড টু দ্য রিলিজিয়ন অফ নন-ভায়োলেন্স (২ সংস্করণ), মোতিলাল বনারসিদাস, আইএসবিএন 978-81-208-1534-6
- ট্রাশকে, অড্রে (১ সেপ্টেম্বর ২০১৫), "ডেঞ্চারাস ডিবেটস: জৈন রেসপন্স টু থিওলজিক্যাল চ্যালেঞ্জেস অ্যাট দ্য মুঘল কোর্ট", মডার্ন এশিয়া স্টাডিজ, ৪৯ (৫): ১৩১১–১৩৪৪, আইএসএসএন 0026-749X, এসটুসিআইডি 146540567, ডিওআই:10.1017/S0026749X14000055
- টু্কোল, বিচারপতি টি. কে. (১৯৭৬), সল্লেখনা ইজ নট সুইসাইড (১ম সংস্করণ), আহমেদাবাদ: এল. ডি. ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডোলজি,
 এই উৎস থেকে এই নিবন্ধে লেখা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা পাবলিক ডোমেইনে রয়েছে।
এই উৎস থেকে এই নিবন্ধে লেখা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা পাবলিক ডোমেইনে রয়েছে। - উমাস্বাতী, উমাস্বামী (১৯৯৪), দ্যাট হুইচ ইজ (অনুবাদ: নাথুমল তাতিয়া), রোওম্যান অ্যান্ড লিটলফিল্ড, আইএসবিএন 978-0-06-068985-8
- ভ্যালেলি, অ্যানি (২০০২), গার্ডিয়ানস অফ দ্য ট্র্যানসেডেন্ট: অ্যান এথনোলজি অফ আ জৈন এসেটিক কমিউনিটি, ইউনিভার্সিটি অফ টরেন্টো প্রেস, আইএসবিএন 978-0-8020-8415-6
- ভ্যালেলি, অ্যানি (২০১৩), বুলিভ্যান্ট, স্টিফেন; রুস, মাইকেল, সম্পাদকগণ, দি অক্সফোর্ড হ্যান্ডবুক অফ এথেইজম, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, আইএসবিএন 978-0-19-166739-8
- ফন গ্লাসেনাপ, হেলমুথ (১৯২৫), জৈনিজম: অ্যান ইন্ডিয়ান রিলিজিয়ন অফ স্যালভেশন [Der Jainismus: Eine Indische Erlosungsreligion], শ্রীধর বি. শ্রোত্রী (অনুবাদ), Delhi: মোতিলাল বনারসিদাস (পুনর্মুদ্রণ: ১৯৯৯), আইএসবিএন 978-81-208-1376-2
- ভুর্স্ট, রবার্ট ই. ভ্যান (২০১৪), আরইএলজি: ওয়ার্ল্ড (২ সংস্করণ), সেনগেজ লার্নিং, আইএসবিএন 978-1-285-43468-1
- ভুর্স্ট, রবার্ট ই. ভ্যান (২০১৫), আরইএলজি: ওয়ার্ল্ড (২য় সংস্করণ), সেনগেজ লার্নিং, আইএসবিএন 978-1-285-43468-1
- উইলি, ক্রিস্টি এল. (২০০৪), হিস্টোরিক্যাল ডিকশনারি অফ জৈনিজম, স্কেয়ারক্রো, আইএসবিএন 978-0-8108-6558-7
- উইলি, ক্রিস্টি এল. (২০০৯), দি এ টু জেড অফ জৈনিজম, ৩৮, স্কেয়ারক্রো, আইএসবিএন 978-0-8108-6337-8
- উইলিয়ামস, রবার্ট (১৯৯১), জৈন যোগ: আ সার্ভে অফ দ্য মিডিয়াভাল শ্রাবকাচারস, মোতিলাল বনারসিদাস, আইএসবিএন 978-81-208-0775-4
- উইন্টারনিৎজ, মরিজ (১৯৯৩), হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান লিটারেচার: বুদ্ধিস্ট অ্যান্ড জৈন লিটারেচার, মোতিলাল বনারসিদাস, আইএসবিএন 978-81-208-0265-0
- ইয়ান্ডেল, কেইথ ই. (১৯৯৯), ফিলোজফি অফ রিলিজিয়ন আ কনটেম্পোরারি ইন্ট্রোডাকশন
- জিমার, হেইনরিখ (১৯৫৩) [1952], ক্যাম্পবেল, জোসেফ, সম্পাদক, ফিলোজফিজ অফ ইন্ডিয়া, লন্ডন: রটলেজ অ্যান্ড কেগান পল লিমিটেড, আইএসবিএন 978-81-208-0739-6






























