অ্যামলথিয়া (প্রাকৃতিক উপগ্রহ)
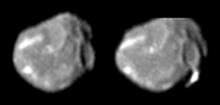 গ্যালিলিও প্রোব থেকে তোলা অ্যামলথিয়ার গ্রেস্কেল ছবি | |||||||||
| আবিষ্কার | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| আবিষ্কারক | ই. ই. বার্নার্ড | ||||||||
| আবিষ্কারের তারিখ | ৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৯২ | ||||||||
| বিবরণ | |||||||||
| উচ্চারণ | /æməlˈθiːə/[১] | ||||||||
| নামকরণের উৎস | অ্যামলথিয়া (Ἀμάλθεια, Amaltheia) | ||||||||
| বিশেষণ | অ্যামলথিয়ান /æməlˈθiːən/[২][৩] | ||||||||
| কক্ষপথের বৈশিষ্ট্য | |||||||||
| অনুসূর | ১৮১১৫০ কিমি[ক] | ||||||||
| অপসূর | ১৮২৮৪০ কিমি[ক] | ||||||||
| কক্ষপথের গড় ব্যাসার্ধ | ১৮১৩৬৫.৮৪±০.০২ কিমি (২.৫৪ আরজে)[৪] | ||||||||
| উৎকেন্দ্রিকতা | ০.০০৩১৯±০.০০০০৪[৪] | ||||||||
| কক্ষীয় পর্যায়কাল | ০.৪৯৮১৭৯৪৩±০.০০০০০০০৭ d (১১ ঘণ্টা, ৫৭ মিনিট, ২৩ সেকেন্ড)[৪] | ||||||||
| গড় কক্ষীয় দ্রুতি | ২৬.৫৭ কিমি/সে[ক] | ||||||||
| নতি | ০.৩৭৪°±০.০০২° (বৃহস্পতির বিষুবরেখার প্রতি)[৪] | ||||||||
| যার উপগ্রহ | বৃহস্পতি | ||||||||
| ভৌত বৈশিষ্ট্যসমূহ | |||||||||
| মাত্রাসমূহ | ২৫০ × ১৪৬ × ১২৮ কিলোমিটার[৫] | ||||||||
| গড় ব্যাসার্ধ | ৮৩.৫±২.০ কিমি[৫] | ||||||||
| আয়তন | (২.৪৩±০.২২)×১০৬ km3[৬] | ||||||||
| ভর | (২.০৮±০.১৫)×১০১৮ কিg[৬] | ||||||||
| গড় ঘনত্ব | ০.৮৫৭±০.০৯৯ g/cm3[৬] | ||||||||
| বিষুবীয় পৃষ্ঠের অভিকর্ষ | ≈ ০.০২০ m/s2 (≈ 0.002 g)[ক] | ||||||||
| মুক্তি বেগ | ≈ ০.০৫৮ km/s[ক] | ||||||||
| ঘূর্ণনকাল | সমলয়[৫] | ||||||||
| অক্ষীয় ঢাল | শূন্য[৫] | ||||||||
| প্রতিফলন অনুপাত | ০.০৯০±০.০০৫[৭] | ||||||||
| |||||||||
| আপাত মান | ১৪.১[৮] | ||||||||
অ্যামলথিয়া (ইংরেজি: Amalthea, /æməlˈθiːə/) হল বৃহস্পতির একটি প্রাকৃতিক উপগ্রহ। বৃহস্পতির যতগুলি উপগ্রহের কথা জানা যায়, সেগুলির মধ্যে অ্যামলথিয়ার কক্ষপথ গ্রহটির তৃতীয় নিকটতম। বৃহস্পতির পঞ্চম আবিষ্কৃত উপগ্রহ বলে এটি বৃহস্পতি ৫ (ইংরেজি: Jupiter V) নামেও পরিচিত। ১৮৯২ সালের ৯ সেপ্টেম্বর এডওয়ার্ড এমারসন বার্নার্ড এটি আবিষ্কার করেন এবং গ্রিক পুরাণের অ্যামলথিয়ার নামানুসারে এটির নামকরণ করেন।[১০] অ্যামলথিয়াই প্রত্যক্ষ দৃষ্টিনির্ভর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আবিষ্কৃত শেষ প্রাকৃতিক উপগ্রহ; পরবর্তীকালের সকল উপগ্রহই আলোকচিত্র বা ডিজিটাল ইমেজিং-এর মাধ্যমে আবিষ্কৃত হয়।
অ্যামলথিয়া বৃহস্পতির খুব কাছ থেকে সেটিকে প্রদক্ষিণ করছে। উপগ্রহটি এটির পৃষ্ঠভাগ থেকে উৎক্ষিপ্ত ধূলির দ্বারা গঠিত অ্যামলথিয়া ঊর্ণনাভ বলয়ের বহিঃপ্রান্তের মধ্যেই অবস্থিত।[১১] অ্যামলথিয়ার পৃষ্ঠভাগ থেকে বৃহস্পতির ব্যাসরেখাটি ৪৬.৫ ডিগ্রি কোণে অবস্থিত বলে মনে হয়।[খ] বৃহস্পতির অভ্যন্তরীণ উপগ্রহগুলির মধ্যে অ্যামলথিয়াই বৃহত্তম। এটি অনিয়তাকার এবং লালচে রঙের। মনে করা হয়, এই উপগ্রহটি সরন্ধ্র জলীয় বরফ ও অজ্ঞাত পরিমাণে অন্যান্য উপাদান দ্বারা গঠিত। এটির পৃষ্ঠভাগে বড়ো বড়ো আকারের সংঘাত গহ্বর ও শৈলশিরা দেখা যায়।[৫]
১৯৭৯ সালে ভয়েজার ১ ও ২ মহাকাশযান খুব কাছ থেকে অ্যামলথিয়ার ছবি তোলে। ১৯৯০-এর দশকে গ্যালিলিও অরবিটার আরও বিস্তারিতভাবে উপগ্রহটিকে পর্যবেক্ষণ করে।[৫]
ইতিহাস[সম্পাদনা]
আবিষ্কার[সম্পাদনা]

১৮৯২ সালের ৯ সেপ্টেম্বর এডওয়ার্ড এমারসন বার্নার্ড লিক মানমন্দিরের ৩৬ ইঞ্চি (৯১ সেমি) প্রতিফলক দূরবীনটির মাধ্যমে অ্যামলথিয়া উপগ্রহটিকে আবিষ্কার করেন।[১০][১২] এটিই শেষ গ্রহীয় উপগ্রহ যা প্রত্যক্ষ দৃষ্টিনির্ভর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আবিষ্কৃত হয়। ১৬১০ সালে গ্যালিলিও গ্যালিলেই কর্তৃক বৃহস্পতির চারটি বৃহত্তম উপগ্রহ আবিষ্কৃত হওয়ার পর অ্যামলথিয়াই ছিল বৃহস্পতির পঞ্চম আবিষ্কৃত উপগ্রহ।[১৩]
নাম[সম্পাদনা]
অ্যামলথিয়ার নামকরণ করা হয়েছে গ্রিক পুরাণের উপদেবী অ্যামলথিয়ার নামানুসারে। ইনি শিশু জিউসকে (রোমান দেবতা জুপিটারের গ্রিক প্রতিরূপ) ছাগদুগ্ধ পান করিয়ে শুশ্রুষা করেছিলেন।[১৪] অ্যামলথিয়ার সংখ্যাগত নামটি হল বৃহস্পতি ৫। ১৯৭৬ সালেই প্রথম আইএইউ "অ্যামলথিয়া" নামটি আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করে।[১৫][১৬] যদিও নামটি তার আগেই অনেক দশক থেকে লৌকিকভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। নামটি প্রথম প্রস্তাব করেছিলেন ক্যামিলে ফ্লেমারিয়ন।[১৭] ১৯৭৬ সালের আগে অ্যামলথিকে সাধারণভাবে বৃহস্পতি ৫ নামেই অভিহিত করা হত।[৯]
পাদটীকা[সম্পাদনা]
- ↑ ক খ গ ঘ ঙ অন্যান্য স্থিতিমাপের ভিত্তিতে পরিগণিত।
- ↑ জ্ঞাত দূরত্ব, আকার, পর্যায়কাল ও দৃশ্যমান মাত্রার (পৃথিবী থেকে যা দেখা যায়) ভিত্তিতে পরিগণিত। Jupiter mj থেকে দৃশ্যমান মাত্রাগুলি পরিগণিত হয়েছে Earth mv-তে দৃশ্যমান মাত্রা থেকে সূত্র mj=mv−log2.512(Ij/Iv) ব্যবহার করে; এই সূত্রে Ij ও Iv হল নিজ নিজ ঔজ্জ্বল্য (দৃশ্য মান দেখুন)ম যার মাপদণ্ড বিপরীত বর্গ নীতির অনুসারী। দৃশ্য মানের জন্য দেখুন http://www.oarval.org/ClasSaten.htm ও বৃহস্পতি (গ্রহ)।
<references>-এ সংজ্ঞায়িত "sizecalc" নামসহ <ref> ট্যাগ পূর্ববর্তী লেখায় ব্যবহৃত হয়নি।তথ্যসূত্র[সম্পাদনা]
- ↑ টেমপ্লেট:MW
- ↑ Basil Montagu (1848) The works of Francis Bacon, vol. 1, p. 303
- ↑ Isaac Asimov (1969) "Dance of the Satellites", The Magazine of Fantasy and Science Fiction, vol. 36, p. 105–115
- ↑ ক খ গ ঘ Cooper Murray et al. 2006।
- ↑ ক খ গ ঘ ঙ চ Thomas Burns et al. 1998।
- ↑ ক খ গ Anderson Johnson et al. 2005।
- ↑ Simonelli Rossier et al. 2000।
- ↑ Observatorio ARVAL।
- ↑ ক খ Simonelli 1983।
- ↑ ক খ Barnard 1892।
- ↑ Burns Simonelli et al. 2004।
- ↑ Lick Observatory (১৮৯৪)। A Brief Account of the Lick Observatory of the University of California। The University Press। পৃষ্ঠা 7–।
- ↑ Bakich M. E. (২০০০)। The Cambridge Planetary Handbook। Cambridge University Press। পৃষ্ঠা 220–221। আইএসবিএন 9780521632805।
- ↑ "Planet and Satellite Names and Discoverers"। Gazetteer of Planetary Nomenclature। International Astronomical Union (IAU) Working Group for Planetary System Nomenclature (WGPSN)। ২০১৪-০৮-২১ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০১৪-১০-০৮।
- ↑ Blunck J. (২০১০)। Solar System Moons: Discovery and Mythology (পিডিএফ)। Springer। পৃষ্ঠা 9–15। আইএসবিএন 978-3-540-68852-5। ডিওআই:10.1007/978-3-540-68853-2। বিবকোড:2010ssm..book.....B। ৪ মার্চ ২০১৬ তারিখে মূল (পিডিএফ) থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ৩ অক্টোবর ২০২০।
- ↑ Flammarion C.; Kowal C.; Blunck J. (১৯৭৫-১০-০৭)। "Satellites of Jupiter"। IAU Circular। Central Bureau for Astronomical Telegrams। ২০১৪-০২-২২ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০১৪-১০-১৭। (টেমপ্লেট:Bibcode)
- ↑ Flammarion 1893।
উদ্ধৃতি ত্রুটি: <references>-এ সংজ্ঞায়িত "Fieseler_2004" নামসহ <ref> ট্যাগ পূর্ববর্তী লেখায় ব্যবহৃত হয়নি।
উদ্ধৃতি ত্রুটি: <references>-এ সংজ্ঞায়িত "IAU_2003" নামসহ <ref> ট্যাগ পূর্ববর্তী লেখায় ব্যবহৃত হয়নি।
উদ্ধৃতি ত্রুটি: <references>-এ সংজ্ঞায়িত "JPL_2003" নামসহ <ref> ট্যাগ পূর্ববর্তী লেখায় ব্যবহৃত হয়নি।
<references>-এ সংজ্ঞায়িত "Lakdawalla_2013" নামসহ <ref> ট্যাগ পূর্ববর্তী লেখায় ব্যবহৃত হয়নি।উল্লিখিত সূত্র
- Anderson, J. D.; Johnson, T. V.; Schubert, G.; Asmar, S.; Jacobson, R. A.; Johnston, D.; Lau, E. L.; Lewis, G.; Moore, W. B.; Taylor, A.; Thomas, P. C.; Weinwurm, G. (২৭ মে ২০০৫)। "Amalthea's Density is Less Than That of Water"। Science। 308 (5726): 1291–1293। ডিওআই:10.1126/science.1110422। পিএমআইডি 15919987। বিবকোড:2005Sci...308.1291A।
- Barnard, E. E. (১২ অক্টোবর ১৮৯২)। "Discovery and observations of a fifth satellite to Jupiter"। The Astronomical Journal। 12 (11): 81–85। ডিওআই:10.1086/101715। বিবকোড:1892AJ.....12...81B।
- Burns, Joseph A.; Showalter, Mark R.; Hamilton, Douglas P.; Nicholson, Philip D.; de Pater, Imke; Ockert-Bell, Maureen E.; Thomas, Peter C. (১৪ মে ১৯৯৯)। "The Formation of Jupiter's Faint Rings"। Science। 284 (5417): 1146–1150। ডিওআই:10.1126/science.284.5417.1146। পিএমআইডি 10325220। বিবকোড:1999Sci...284.1146B।
- Burns, Joseph A.; Simonelli, Damon P.; Showalter, Mark R.; Hamilton, Douglas P.; Porco, Carolyn C.; Throop, Henry; Esposito, Larry W. (২০০৪)। "Jupiter's Ring-Moon System" (পিডিএফ)। Bagenal, Fran; Dowling, Timothy E.; McKinnon, William B.। Jupiter: the Planet, Satellites and Magnetosphere। Cambridge University Press। পৃষ্ঠা 241–262। আইএসবিএন 978-0-521-81808-7। বিবকোড:2004jpsm.book..241B।
- Cooper, N. J.; Murray, C. D.; Porco, C. C.; Spitale, J. N. (মার্চ ২০০৬)। "Cassini ISS astrometric observations of the inner jovian satellites, Amalthea and Thebe"। Icarus। 181 (1): 223–234। ডিওআই:10.1016/j.icarus.2005.11.007। বিবকোড:2006Icar..181..223C।
- Flammarion, Camille (১৮৯৩)। "Le Nouveau Satellite de Jupiter"। L'Astronomie। 12: 91–94। বিবকোড:1893LAstr..12...91F।
- Observatorio ARVAL (১৫ এপ্রিল ২০০৭)। "Classic Satellites of the Solar System"। Observatorio ARVAL। ৯ জুলাই ২০১১ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৭ ডিসেম্বর ২০১১।
- Simonelli, D. P. (জুন ১৯৮৩)। "Amalthea: Implications of the temperature observed by Voyager"। Icarus। 54 (3): 524–538। আইএসএসএন 0019-1035। ডিওআই:10.1016/0019-1035(83)90244-0। বিবকোড:1983Icar...54..524S।
- Simonelli, D. P.; Rossier, L.; Thomas, P. C.; Veverka, J.; Burns, J. A.; Belton, M. J. S. (অক্টোবর ২০০০)। "Leading/Trailing Albedo Asymmetries of Thebe, Amalthea, and Metis"। Icarus। 147 (2): 353–365। ডিওআই:10.1006/icar.2000.6474। বিবকোড:2000Icar..147..353S।
- "Swiss Cheese Moon: Jovian Satellite Full of Holes"। Space.com। ৯ ডিসেম্বর ২০০২। ২৮ আগস্ট ২০০৮ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা।
- Takato, Naruhisa; Bus, Schelte J.; Terada, H.; Pyo, Tae-Soo; Kobayashi, Naoto (২৪ ডিসেম্বর ২০০৪)। "Detection of a Deep 3-μm Absorption Feature in the Spectrum of Amalthea (JV)"। Science। 306 (5705): 2224–2227। ডিওআই:10.1126/science.1105427। পিএমআইডি 15618511। বিবকোড:2004Sci...306.2224T।
- Thomas, P. C.; Burns, J. A.; Rossier, L.; Simonelli, D.; Veverka, J.; Chapman, C. R.; Klaasen, K.; Johnson, T. V.; Belton, M. J. S.; Galileo Solid State Imaging Team (সেপ্টেম্বর ১৯৯৮)। "The Small Inner Satellites of Jupiter"। Icarus। 135 (1): 360–371। ডিওআই:10.1006/icar.1998.5976। বিবকোড:1998Icar..135..360T।
- USGS/IAU। "Amalthea Nomenclature"। Gazetteer of Planetary Nomenclature। USGS Astrogeology। সংগ্রহের তারিখ ২০১২-০৩-২৭।
বহিঃসংযোগ[সম্পাদনা]
- অ্যামলথিয়া পরিলেখ - নাসার সোলার সিস্টেম এক্সপ্লোরেশন থেকে
- অ্যামলথিয়ার নামকরণ - ইউএসজিএস গ্রহীয় নামকরণপদ্ধতি-সংক্রান্ত পৃষ্ঠা থেকে
- জুপিটার’স অ্যামলথিয়া সারপ্রাইজিংলি জাম্বলড – জেপিএল প্রেস রিলিজ (২০০২-১২-০৯)
- জুপিটার ফ্রম অ্যামলথিয়া, ফ্র্যাংক হেটিক অঙ্কিত একটি চিত্র, ২০০২।
- অ্যামলথিয়ার অ্যানিমেশন ত্রিমাত্রিক আকারগত মডেল
আরও দেখুন[সম্পাদনা]
- গ্যালিলিয়ান উপগ্রহ (বৃহস্পতির বৃহত্তম চারটি প্রাকৃতিক উপগ্রহ)

