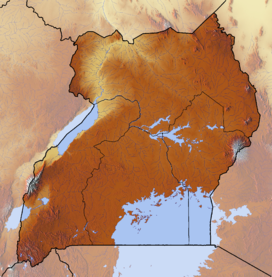রুয়ানযোরি পর্বতমালা
| রুয়ানযোরি পর্বতমালা | |
|---|---|
 | |
| সর্বোচ্চ বিন্দু | |
| শিখর | স্ট্যানলি পর্বত |
| উচ্চতা | ৫,১০৯ মিটার (১৬,৭৬২ ফুট) |
| স্থানাঙ্ক | ০০°২৩′০৯″ উত্তর ২৯°৫২′১৮″ পূর্ব / ০.৩৮৫৮৩° উত্তর ২৯.৮৭১৬৭° পূর্ব |
| মাপ | |
| দৈর্ঘ্য | ১২০ কিলোমিটার (৭৫ মাইল) |
| ভূগোল | |
| দেশ | উগান্ডা, গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র |
রুয়ানযোরি পর্বতমালা (মাউন্টেইন্স অব দ্যা মুন নামেও পরিচিত) পূর্ব আফ্রিকার বিষুবীয় অঞ্চলে উগান্ডা এবং কঙ্গোর সীমানায় অবস্থিত একটি বৃহৎ পর্বতমালা। এই পর্বতমালায় প্রচুর হিমবাহ জমা হয় এবং তা নীলনদের পানির গুরুত্বপূর্ণ উৎস। রুয়ানযোরি পর্বতমালার সর্বোচ্চ উচ্চতা ৫,১০৯ মিটার (১৬,৭৬২ ফিট)। সর্বোচ্চ শৃঙ্গগুলো প্রায় সবসময়ই তুষারাবৃত থাকে। রুয়ানযোরি পর্বত জাতীয় উদ্যান এবং ভিরুঙা জাতীয় উদ্যান এই পর্বতমালার অংশ।
ভূতত্ত্ব[সম্পাদনা]
রুয়ানযোরি পর্বতমালা প্রায় ত্রিশ লক্ষ বছর পূর্বে প্লাইওসিন যুগের শেষার্ধে গঠিত হয়। স্ফটিক প্রকৃতির বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের উর্ধ্বমুখী অবস্থানের পরিবর্তনের মাধ্যমে এই পর্বতমালার সৃষ্টি।[১] এই পরিবর্তনের ফলে আফ্রিকার তিনটি বৃহৎ হ্রদ তৈরি হয়: আলবার্ট হ্রদ, এডওয়ার্ড হ্রদ এবং জর্জ হ্রদ।[২]
এই পর্বতমালা প্রস্থে প্রায় ১২০ কিলোমিটার। রুয়ানযোরি পর্বতমালায় ছয়টি পর্বতপ্রাচীর রয়েছে যেগুলো সুগভীর গিরিসঙ্কট দ্বারা পৃথক: স্ট্যানলি পর্বত (৫,১০৯ মিটার), স্পিক পর্বত (৪,৮৯০ মিটার), বেকার পর্বত (৪,৮৪৩ মিটার), এমিন পর্বত (৪,৭৯৮ মিটার), গেছি পর্বত (৪,৭১৫ মিটার) এবং লুইগি দি সাভোয়া পর্বত (৪,৬২৭ মিটার)। স্ট্যানলি পর্বতের বেশ কয়েকটি উপশৃঙ্গ রয়েছে, যার মধ্যে মার্গারিটা শৃঙ্গ সবচেয়ে উঁচু।
উদ্ভি্দরাজি[সম্পাদনা]

রুয়ানযোরি পর্বতমালায় বৈচিত্র্যপূর্ণ উদ্ভিদ জন্মে। এখানে ক্রান্তীয় ঘনবর্ষণ বনাঞ্চল, আলপাইন তৃণভূমি এমনকি তুষারাবৃত অঞ্চলের উপযোগী উদ্ভিদরাজির দেখা মেলে। এই অঞ্চলে মন কিছু প্রজাতির উদ্ভিদ জন্মে যা পৃথিবীর অন্যত্র সচরাচর পাওয়া যায়না। যেমন- জায়ান্ট গ্রাউন্ডসেল, জায়ান্ট লোবেলিয়া। এই পর্বতমালার অধিকাংশই এখন বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের অন্তর্গত। অঞ্চলটির একটি বড় অংশ রুয়ানযোরি পর্বত জাতীয় উদ্যান এবং ভিরুঙা জাতীয় উদ্যানের অধীনে তত্ত্বাবধায়ন করা হয়। রুয়ানযোরি পর্বত জাতীয় উদ্যানটি উগান্ডার দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং ভিরুঙা জাতীয় উদ্যান কঙ্গোর পূর্বে অবস্থিত।[৩]
রুয়ানযোরি অঞ্চলে পানির অভাব নেই। তবে আফ্রোআলপাইন বর্গের কিছু উদ্ভিদ প্রজাতি এখানে জন্মে যেগুলো সাধারণত মরু অঞ্চলে দেখা যায়। এর কারণ মূলত প্রজাতিগুলোর পানি ব্যবহারের ধরন ও অভ্যাস। পানির প্রাচুর্য্য থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় ঐ প্রজাতিগুলো প্রয়োজনমত পানি গ্রহণ করতে পারেনা। রাত্রিকালীন তুষারপাত এসব উদ্ভিদের অভ্যন্তরে প্রাণরস পরিবহন এবং শিকড়ের মাধ্যমে পানিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় বাধা দেয়। দিনের বেলায় বায়ুর তাপমাত্রা এবং বিকিরণ মাত্রা বাড়তে থাকে। ফলে উদ্ভিদের বাহিরের অংশের পানির চাহিদা বেড়ে যায়। উদ্ভিদের পত্রের স্বেদন চাহিদাও গুরুত্বপূর্ণ। এই স্বেদন পক্রিয়া এবং পানি গ্রহণ প্রক্রিয়ার মধ্যে উপযুক্ত ভারসাম্য থাকা বাঞ্ছনীয়। ঠান্ডায় হিমায়িত হওয়া প্রতিহত করতে আফ্রোআলপাইন উদ্ভিদগুলো একধরনের নিজস্ব অন্তরণ পদ্ধতির আশ্রয় নেয়। ফলে এদেরকে এমন স্থানে পাওয়া যায়। এই অভিযোজন ধারা উচ্চতা বাড়ার সাথে সাথে বেশি পরিলক্ষিত হয়।[৪]
রুয়ানযোরি পর্বতমালায় মূলত পাঁচ ধরনের উদ্ভিদরাজি পাওয়া যায়: তৃণভূমি (১০০০–২০০০ মিটার), পার্বত্য বনাঞ্চল ( ২০০০–৩০০০ মিটার), বাঁশবন (২৫০০–৩৫০০ মিটার), গুল্ম অঞ্চল (৩০০০–৪০০০ মিতার) এবং জলাভূমি বা বিস্তীর্ণ প্রান্তর (৪০০০-৪৫০০ মিটার)। অধিক উচ্চতায় কিছু উদ্ভিদ প্রজাতি আকারে অনেক বড় হয়ে উঠে, যেমন – লোবেলিয়া এবং গ্রাউন্ডসেল। রুয়ানযোরি পর্বতমালার উদ্ভিদরাজি বিষুবীয় আলপাইন আফ্রিকা অঞ্চলের অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।[৫]
তথ্যসূত্র[সম্পাদনা]
- ↑ "Climate Change and the Aquatic Ecosystems of the Rwenzori Mountains"। Makerere University and University College London। ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৭। ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪।
- ↑ Wayland, E. J. (জুলাই–ডিসেম্বর ১৯৩৪)। "Rifts, Rivers, Rains and Early Man in Uganda"। Journal of the Royal Anthropological Institute। Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland। 64: 333–352। জেস্টোর 2843813। ডিওআই:10.2307/2843813।
- ↑ "Rwenzori Mountains National Park"। Rwenzori Abruzzi। ২৭ মে ২০০৬। ২০০৮-০৩-০৫ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ৬ মে ২০০৮।
- ↑ Flowers of the Moon, Afroalpine vegetation of the Rwenzori Mountains ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে, Schutyser S., 2007, 5 Continents Editions, আইএসবিএন ৯৭৮-৮৮-৭৪৩৯-৪২৩-৪.
- ↑ H. Peter Linder and Berit Gehrke (২ মার্চ ২০০৬)। "Common plants of the Rwenzori, particularly the upper zones" (পিডিএফ)। Institute for Systematic Botany, জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়। ২০০৮-০৫-৩০ তারিখে মূল (PDF) থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০০৮-০৫-০৬।
বহিঃসংযোগ[সম্পাদনা]
- Rwenzori Mountains, a destination guide
- UWM.edu: 1937 aerial photographs of Rwenzori Mountains — University of Wisconsin-Milwaukee Libraries Digital Collections.
 Beach, Chandler B., সম্পাদক (১৯১৪)। "Ruwenzori"। The New Student's Reference Work। Chicago: F. E. Compton and Co।
Beach, Chandler B., সম্পাদক (১৯১৪)। "Ruwenzori"। The New Student's Reference Work। Chicago: F. E. Compton and Co।